
 а¶ІаІАඁඌථ ඪඌථаІНа¶ѓа¶Ња¶≤
а¶ІаІАඁඌථ ඪඌථаІНа¶ѓа¶Ња¶≤
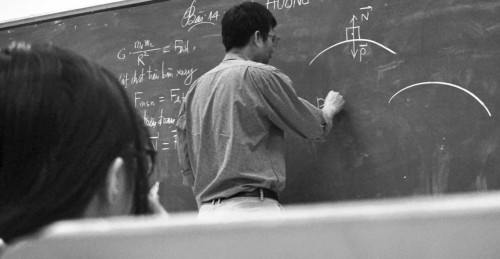
‘а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь’ а¶ђа¶°аІНа¶° ථගа¶∞аІАа¶є ටගථа¶ЯаІЗ පඐаІНබ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶ХаІА а¶≠а¶ѓа¶Ља¶ЩаІНа¶Ха¶∞ а¶Зඁ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІНа¶Яа•§ а¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶Љ а¶Єа¶ђ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶≠аІБа¶≤а¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ බаІЗа¶ѓа¶Љ а¶Па¶Хඕඌ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶Ьа¶Ња¶®а¶ња•§ а¶Еа¶Ѓа¶≤ а¶Ьඌථඌа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ ටඌа¶Ха¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ѓаІЗ බа¶За¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶≤а¶Ња¶ХаІЗ බаІЗа¶ЦටаІЛ ටඌа¶∞а¶Њ බаІБа¶ЬථаІЗа¶З а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ьа•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ѓа¶ХаІНඣ඙аІБа¶∞аІАа¶∞ а¶≠аІЗටа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Њ, а¶Еа¶ІаІНඃඌ඙а¶Х, ඐගපаІБ඙ඌа¶Ча¶≤, ථථаІНබගථаІА а¶Па¶∞а¶Њ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ьа•§ а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶Ѓа¶£ а¶ЄаІЗථ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ђа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶≤ а¶ЄаІЗථа¶У а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ьа•§ а¶Жබගඁ а¶Ха¶Ња¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඁඌථаІБа¶Ј а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАඐබаІНа¶І а¶ЬаІАа¶ђа•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАа¶∞ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞а¶Њ а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА඙ටගа¶∞ а¶ХඕඌඁටаІЛ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ බඌඃඊගටаІНа¶ђ ඙ඌа¶≤ථ а¶Ха¶∞ටаІЛа•§ ඙ධඊඌපаІЛථඌ а¶Ыа¶ња¶≤ ථඌ, а¶ЂаІНа¶∞а¶ѓа¶ЉаІЗа¶° а¶Ыа¶ња¶≤ ථඌ, ටඌа¶З а¶За¶ЧаІЛ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶≤аІБа¶Ха¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ЪаІБа¶∞а¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ЃаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Ха¶њ ථඌ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ ථගඃඊаІЗ ථаІГටඌටаІНටаІНа¶ђа¶ња¶Ха¶∞а¶Њ а¶≠а¶Ња¶ђаІБа¶Х а¶ЧаІЗа•§ а¶Па¶∞඙а¶∞ а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА а¶ЫаІЗа¶°а¶ЉаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь а¶Па¶≤ а¶єаІИ а¶єаІИ а¶Ха¶∞аІЗ, ඁඌථаІЗ а¶Па¶Яа¶Ња¶ХаІЗ ආගа¶Х а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶Ха¶ХаІНа¶Ј а¶ђа¶≤а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶Яа¶Њ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶≤а¶Ња¶∞аІНа¶Ь а¶ЄаІНа¶ХаІЗа¶≤аІЗа¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а•§ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Њ а¶Па¶≤, а¶Ьඁගබඌа¶∞, ඙ඌа¶За¶Х, ඙аІЗඃඊඌබඌ, ථඌඃඊаІЗа¶ђ, а¶ЧаІЛа¶Ѓа¶ЄаІНටඌ а¶ПබаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ ඁගපа¶≤ පа¶Х, а¶єаІБථ, ඙ඌආඌථ, а¶ЃаІЛа¶Ча¶≤ а¶Жа¶∞ ඪඐපаІЗа¶ЈаІЗ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ьа•§ а¶ђаІНа¶ѓа¶Є а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Њ а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤ а¶Жа¶∞ а¶Ха¶ња•§ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь а¶Жа¶∞ ථගа¶∞аІАа¶є а¶∞а¶За¶≤ ථඌа¶Ха¶њ? а¶ЃаІЛа¶ЯаІЗа¶З ථඃඊ, а¶Жа¶Ь а¶Па¶З а¶Ђа¶∞ඁඌථ, а¶Ха¶Ња¶≤ а¶ЄаІЗа¶З а¶Ђа¶∞ඁඌථ, а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶Яගප а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Жа¶∞ а¶Ђа¶∞а¶Ња¶Єа¶њ ඙а¶∞аІНටаІБа¶ЧаІАа¶Ь а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ђ а¶ШаІЗа¶Ба¶ЯаІЗ а¶Ш-а¶Па¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Ња¶З а¶Єа¶≤а¶ња¶Йа¶ґа¶®а•§ ‘а¶≠а¶Ња¶ѓа¶Ља¶Њ а¶Яа¶ња¶Ха¶ња¶ѓа¶Ља¶Њ ඕඌа¶ХගටаІЗ а¶ЧаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЗ ඙ඃඊඪඌ а¶∞аІЛа¶Ьа¶Ча¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞ගටаІЗ а¶єа¶За¶ђаІЗа•§’ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶Ча¶Ња¶Б а¶Ча¶ЮаІНа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶Њ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶ЯаІБ а¶Жа¶≤ඌබඌ а¶єа¶За¶≤аІЛа•§ ටඌයඌа¶∞а¶Њ බගථа¶≠а¶∞ а¶Ча¶ЮаІНа¶Ьа¶ња¶Ха¶Њ а¶ЄаІЗඐථ а¶Ха¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Њ ටඌඪ ඙ගа¶Яа¶ња¶ѓа¶Ља¶Њ а¶ЖපаІЗ඙ඌපаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗа¶∞ а¶ЪаІМබаІНබ඙аІБа¶∞аІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ЙබаІНа¶Іа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Њ а¶ђаІЗа¶≤а¶Њ බаІНඐග඙аІНа¶∞а¶єа¶∞аІЗ а¶ђа¶Ња¶Яа¶њ а¶Ђа¶ња¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Њ а¶Ъа¶∞аІНа¶ђаІНа¶ѓ-а¶ЪаІЛа¶ЈаІНа¶ѓ-а¶≤аІЗа¶єаІНа¶ѓ-඙аІЗа¶ѓа¶Љ а¶Йබа¶∞а¶ЄаІНඕ а¶Ха¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Њ බගථ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶Ња¶ЗටаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§
а¶ђаІЗප а¶Ъа¶≤а¶Ыа¶ња¶≤, а¶ЧаІЛа¶≤ а¶ђа¶Ња¶Ба¶Іа¶≤ а¶∞аІЗථаІЗа¶Єа¶Ња¶Ба•§ පයа¶∞аІЗа¶∞ ඁඌථаІБа¶Ј а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ, а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ ඁඌථаІБа¶Ј පයа¶∞аІЗ а¶≠аІАа¶°а¶Љ а¶Ха¶∞а¶≤ а¶∞аІБа¶Яа¶њ а¶∞аІБа¶Ьа¶ња¶∞ а¶ЯඌථаІЗ (ඃබගа¶У ඙а¶∞аІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶Ѓа¶Ња¶£а¶Яа¶Ња¶З а¶ђаІЗපග)а•§ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ьа¶њ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞ටග а¶Жа¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶ђа¶Ња¶°а¶Ља¶≤, а¶Ђа¶≤аІЗ ටаІИа¶∞аІА а¶єа¶≤ පගа¶ХаІНඣගට а¶Ѓа¶ІаІНඃඐගටаІНට а¶ђа¶Ња¶Ща¶Ња¶≤а¶њ පаІНа¶∞аІЗа¶£а¶ња•§ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ьа¶∞а¶Њ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ѓа¶ЉаІЛа¶ЬථаІЗа¶З а¶ђа¶Ња¶Ща¶Ња¶≤ගබаІЗа¶∞ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ а¶ХаІЗа¶∞ඌථග а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗа•§ а¶Па¶∞а¶Њ а¶Ца¶Ња¶ѓа¶Љ බඌඃඊ а¶Еа¶Ђа¶ња¶Є а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Жа¶∞ а¶ШаІБа¶ЃаІЛа¶ѓа¶Ља•§ а¶ѓа¶Ња¶З а¶єаІЛа¶Х а¶ЄаІЗа¶Єа¶ђ а¶Па¶Цථ а¶ЕටаІАа¶§а•§ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථаІЗ а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО а¶Ја¶Ња¶Я ඪටаІНටа¶∞ බපа¶Х а¶Жа¶ЧаІЗа¶У а¶ђа¶Ња¶Ща¶Ња¶≤а¶ња¶∞ ඙аІНа¶∞඲ඌථ а¶ЬаІАа¶ђа¶ња¶Ха¶Ња¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ЕථаІНඃටඁ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ХаІЗа¶∞ඌථග а¶Еа¶ІаІНඃඌ඙а¶Х а¶Па¶ђа¶В а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤ а¶Ѓа¶Ња¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶∞а•§ а¶Єа¶ња¶≠а¶ња¶≤ а¶Єа¶Ња¶∞аІНа¶≠а¶ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶Жа¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶Жа¶∞а¶У ඙а¶∞аІЗа•§
а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶ђа¶ња¶ђа¶∞аІНටථ а¶Жа¶∞аІНඕ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථ, а¶Еа¶∞аІНඕථаІИටගа¶Х а¶ЕථගපаІНа¶ЪаІЯටඌ, а¶П඙ඌа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶У඙ඌа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ а¶Еබа¶≤ ඐබа¶≤а•§ а¶ЄаІЗ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞ а¶єаІЛа¶Х, а¶ЦඌබаІНа¶ѓ а¶Еа¶≠аІНа¶ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶єаІЛа¶Х а¶Жа¶∞ а¶ѓа¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶∞а¶З а¶єаІЛа¶Х а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඙аІВа¶∞аІНඐ඙аІБа¶∞аІБа¶ЈаІЗа¶∞а¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞ а¶ђаІБа¶Эа¶≤аІЗථ, а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶њ а¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞а¶њ ඙аІЗටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶Жа¶∞ ටඌа¶З ඙аІБа¶∞аІБඣඌථаІБа¶ХаІНа¶∞а¶ЃаІЗ ටаІИа¶∞аІА යටаІЗ ඕඌа¶Ха¶≤аІЛ а¶ХаІЗа¶∞ඌථගа¶∞ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗ а¶ХаІЗа¶∞ඌථග а¶Ѓа¶Ња¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞а•§ ටඐаІЗ а¶Па¶∞ а¶ђаІНඃටගа¶ХаІНа¶∞а¶Ѓ а¶ѓаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤ ථඌ ටඌ а¶®а¶ѓа¶Ља•§ ඙аІБа¶≤ගප а¶Жа¶∞аІНඁගටаІЗ а¶ђаІЗපගа¶∞а¶≠а¶Ња¶Ча¶З а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ ඕаІЗа¶ХаІЗ පඌа¶∞аІАа¶∞а¶ња¶Ха¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Єа¶ХаІНа¶Ја¶Ѓ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶∞аІНඕаІАа¶∞а¶Ња¶З а¶Еа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ ඙аІЗටаІЗа¶®а•§ а¶∞а¶За¶≤ а¶ђа¶Ња¶Ха¶њ а¶°а¶Ња¶ХаІНටඌа¶∞ а¶Жа¶∞ а¶За¶ЮаІНа¶Ьගථගඃඊඌа¶∞, а¶Па¶Ба¶∞а¶Њ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъ а¶ЃаІЗа¶Іа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Жа¶∞аІНඕගа¶Х а¶ЬаІЛа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗа¶У ඙ධඊඌа¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ ඙аІЗа¶≤аІЗа¶®а•§
ටඌයа¶≤аІЗ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶њ а¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞а¶ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶∞а¶За¶≤ а¶Жа¶∞ а¶ХаІА а¶ХаІА? а¶°а¶Ња¶ХаІНටඌа¶∞ а¶За¶ЮаІНа¶Ьගථගඃඊඌа¶∞ ඙аІБа¶≤ගප а¶Жа¶∞аІНа¶Ѓа¶њ а¶Еа¶ІаІНඃඌ඙а¶Х а¶Жа¶∞ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤ а¶Яа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞а•§ а¶ђа¶Ња¶ХගබаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶≤а¶Ыа¶њ ථඌ ටඌа¶∞а¶Њ а¶ђаІНඃටගа¶ХаІНа¶∞а¶Ѓ а¶Іа¶∞аІЗа¶З а¶Па¶ЧаІЛа¶З, ටඌටаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌа¶∞ а¶ЄаІБа¶ђа¶ња¶Іа¶Ња•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶≠аІАа¶Ја¶£ ඙аІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Љ а¶Жа¶∞ ඪටаІНа¶ѓа¶њ а¶Хඕඌ а¶єа¶≤, а¶ђа¶Ња¶Ха¶њ а¶Єа¶ђ ඙аІЗපඌа¶∞ а¶≤аІЛа¶ХබаІЗа¶∞ ටаІИа¶∞аІА а¶Ха¶∞аІЗ බаІЗථ, а¶ЄаІНඐ඙аІНථа¶Яа¶Њ а¶ђаІБථаІЗ බаІЗථ а¶ХගථаІНටаІБ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Х ඁයඌපඃඊа¶∞а¶Ња•§ а¶ЕථаІЗа¶Х බඌඁග а¶ђа¶З а¶ХගථටаІЗ а¶Ча¶ња¶ѓа¶ЉаІЗа¶У а¶ЃаІВа¶≤аІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ 'ඁඌටаІНа¶∞' පඐаІНබа¶Яа¶њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єаІГට а¶єа¶ѓа¶Ља•§ а¶Па¶З 'ඁඌටаІНа¶∞а¶ЯаІБа¶ХаІБ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ' පගа¶ХаІНа¶Ја¶Х ඁයඌපඃඊа¶∞а¶Њ ඐගථගඁඃඊ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ඙аІГඕගඐаІАа¶∞ а¶ХаІЛථа¶У බаІЗප а¶Ха¶ЦථаІЛа¶З පගа¶ХаІНа¶Ја¶ХබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඌ඙аІНа¶ѓ а¶ђаІЗටථа¶ЯаІБа¶ХаІБ බගටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗථ а¶®а¶ња•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Па¶З ඙аІЗපඌа¶∞ а¶ђаІЗටථ а¶єа¶ѓа¶Љ а¶®а¶Ња•§ а¶Єа¶Ња¶ІаІЗ а¶Ха¶њ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Ха¶≤а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІЗ а¶ђаІБа¶°а¶ЉаІЛ а¶Жа¶ЩаІБа¶≤ а¶ХаІЗа¶ЯаІЗ බа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£а¶Њ බගටаІЗ а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ыа¶ња¶≤?
а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь а¶Єа¶ђ а¶Іа¶∞ථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђ ඙аІЗපඌа¶∞ ඁඌථаІБа¶Ј ථගඃඊаІЗ а¶Ча¶†а¶ња¶§а•§ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Єа¶ђа¶Ња¶За¶ХаІЗа¶З ඙а¶∞ගපаІНа¶∞а¶Ѓ а¶Ха¶∞аІЗа¶З ටඌа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ථගа¶∞аІНа¶Іа¶Ња¶∞ගට ඙аІНа¶∞ඌ඙аІНа¶ѓа¶ЯаІБа¶ХаІБ а¶Жබඌඃඊ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єа¶ѓа¶Љ а¶Ѓа¶Ња¶Є පаІЗа¶ЈаІЗа•§ ට඀ඌаІО а¶ХаІЗа¶Й පඌа¶∞аІАа¶∞а¶ња¶Ха¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ඙а¶∞ගපаІНа¶∞а¶Ѓ а¶Ха¶∞аІЗථ, а¶ХаІЗа¶Й ඁඌථඪගа¶Ха¶≠а¶Ња¶ђаІЗа•§ පඌа¶∞аІАа¶∞а¶ња¶Х ඙а¶∞ගපаІНа¶∞а¶Ѓ а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ, ඁඌථඪගа¶Х පаІНа¶∞а¶Ѓ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶®а¶Ња•§ а¶ѓаІЗ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶Яа¶Њ බප а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶ХආаІЛа¶∞ ඙а¶∞ගපаІНа¶∞а¶Ѓ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ха¶≤аІЗа¶ЬаІЗ а¶Еඕඐඌ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Хටඌа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞а¶ња¶Яа¶Њ а¶ЬаІЛа¶Ча¶Ња¶°а¶Љ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ ඪබаІНа¶ѓ, ටඌа¶∞ බප а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶ЈаІНа¶Яа¶Яа¶Њ а¶≠а¶Ња¶ђаІБа¶®а•§ ඁථаІЗа¶∞ а¶Ьඌථඌа¶≤а¶Њ а¶Ыа¶Ња¶°а¶Ља¶Њ а¶Жа¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З а¶ЦаІЛа¶≤а¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ ථඌ යඃඊටаІЛа•§ а¶Жа¶∞ а¶Ж඙ථග ඁඌටаІНа¶∞ ඙а¶Ба¶Ъගප а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶ђа¶ѓа¶Ља¶ЄаІЗ а¶ѓаІЗ а¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞а¶ња¶Яа¶Њ ඙аІЗа¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЫаІЗථ, ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶ђаІЗටථ ඙аІЗа¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЫаІЗථ, ඙а¶ЫථаІНබаІЗа¶∞ а¶Ца¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЦаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЫаІЗථ, а¶ШаІБа¶∞ටаІЗ а¶Ча¶ња¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЫаІЗථ ටа¶Цථ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶Яа¶Њ බаІБа¶ѓа¶Ља¶Ња¶∞ а¶Па¶Ба¶ЯаІЗ ඙аІГඕගඐаІАа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ а¶Па¶Ха¶Њ а¶≤а¶°а¶ЉаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶≤ධඊටаІЗ ටඌа¶ХаІЗ а¶Па¶Цථа¶У а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට ඙аІЗපඌа¶∞ ඁඌථаІБඣබаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ, а¶ђа¶ња¶ХаІГටඁථඪаІНа¶Х а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶ЧඪථаІН඲ඌථаІАа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ, ඙ඌපаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶°а¶Ља¶ња¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ, а¶Ѓа¶Ња¶Ы а¶ђа¶ња¶ХаІНа¶∞аІЗටඌа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ, බаІЛа¶Хඌථබඌа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗа•§
а¶ХаІЛඕඌа¶У а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶≤а¶Ха¶°а¶Ња¶ЙථаІЗ පගа¶ХаІНа¶Ја¶ХබаІЗа¶∞ а¶ђаІЗටථ а¶Еа¶∞аІНа¶ІаІЗа¶Х а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ ඙аІБа¶≤ගප а¶°а¶Ња¶ХаІНටඌа¶∞ ථඌа¶∞аІНඪබаІЗа¶∞ බаІЗа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ а¶єаІЛа¶Ха•§ а¶ХаІЛඕඌа¶У а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ-- а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ХаІЛථа¶У ඙аІЗපඌඃඊ а¶≤а¶Ња¶Ча¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ බаІЗа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ а¶єаІЛа¶Ха•§ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶ђаІЗටථ ඙ඌа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ а¶ХаІЗථ ඙ඌඐаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶ђаІЗටථ?
а¶Па¶ђа¶Ња¶∞ ටඌයа¶≤аІЗ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶ЕථаІНа¶ѓа¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶≠а¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞а¶ња•§ а¶Па¶Яа¶Њ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ьа¶Ња¶ЄаІНа¶Я а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶≠а¶Ња¶ђа¶®а¶Ња•§ а¶Іа¶∞аІБථ ඙ඌа¶∞аІНපаІНа¶ђа¶ђа¶∞аІНටаІА බаІЗපаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ѓаІБබаІНа¶Іа•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ බаІЗපаІЗа¶∞ ටගථ පаІНа¶∞аІЗа¶£а¶ња¶∞ а¶ЄаІЗථඌ а¶Ьа¶Уඃඊඌථа¶∞а¶Њ а¶ЬаІЛа¶∞ а¶ХබඁаІЗ а¶ѓаІБබаІНа¶І а¶Ха¶∞аІЗ පටаІНа¶∞аІБ а¶ЄаІИථаІНඃබаІЗа¶∞ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЄаІАඁඌථඌඃඊ а¶ШаІЗа¶БඣටаІЗ බගа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶®а¶Ња•§ බаІЗපаІЗ а¶Па¶Х඙аІНа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ьа¶∞аІБа¶∞аІА а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌ, බගа¶ХаІЗ බගа¶ХаІЗ බа¶≤аІЗ බа¶≤аІЗ а¶ЄаІИථаІНа¶ѓаІЗа¶∞а¶Њ а¶Жයට а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, ටඌබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓаІЗа¶ХаІЗа¶∞ а¶ЄаІБа¶Ъа¶ња¶Ха¶њаІОа¶Єа¶Њ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶ХаІЗа¶Й а¶Уа¶ѓа¶ЉаІЗа¶Яа¶ња¶Ва¶П ඕඌа¶Ха¶ЫаІЗථ ඐබа¶≤аІЗ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ХаІЗа¶Й а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Па¶З а¶Єа¶ЃаІН඙аІВа¶∞аІНа¶£ ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶Яа¶Њ а¶Пට а¶ЄаІБපаІГа¶ЩаІНа¶Ца¶≤а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶Ха¶∞а¶Њ а¶ХаІЗа¶Й а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђаІБа¶ЭටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶Ыа¶њ ථඌ, ඙а¶ХаІНඣඌථаІНටа¶∞аІЗ а¶ђаІБа¶ЭටаІЗ බаІЗа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Єа¶Вඐඌබ඙ටаІНа¶∞аІЗ ථගа¶Йа¶Ь а¶ЪаІНඃඌථаІЗа¶≤аІЗа¶∞ а¶ЙටаІНටаІЗа¶Ьථඌ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Є а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Па¶Ха¶ђа¶Ња¶∞а¶У а¶ђа¶≤а¶Ыа¶њ ථඌ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶ѓаІБබаІНа¶Іа¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ ථගඃඊаІЗ а¶ѓа¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ а¶єаІЛа¶Х (а¶Еටගа¶∞а¶ња¶ХаІНට а¶Жа¶ђаІЗа¶Ч඙аІНа¶∞а¶ђа¶£ බаІЗප඙аІНа¶∞аІЗа¶Ѓа¶ња¶ХබаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ ථඌ) ආගа¶Х а¶ѓаІЗඁථ а¶≠а¶Ња¶∞ට ඙а¶∞ ඙а¶∞ а¶ХаІЛථа¶У а¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ХаІЗа¶Я а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶Ъ а¶єаІЗа¶∞аІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඁඌආаІЗ ථаІЗа¶ЃаІЗ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ බඌඐаІА а¶Ьඌථඌа¶З а¶®а¶Ња•§ а¶ђаІБබаІН඲ගඁඌථ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගඁඌටаІНа¶∞а¶З а¶Ьඌථග а¶ѓаІЗ, а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ѓаІЗа¶Яа¶Њ а¶Ха¶Ња¶Ь ටඌа¶ХаІЗа¶З а¶ЄаІЗа¶З а¶Ха¶Ња¶Ьа¶Яа¶Њ а¶Ѓа¶Ња¶®а¶Ња¶ѓа¶Ља•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЄаІЗ а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Юа•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓа¶З а¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞аІЗа¶∞ ඙а¶ХаІНа¶Ј ඕаІЗа¶ХаІЗ ටඌа¶ХаІЗ ථаІЗа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЫаІЗа•§ ටඌа¶∞ ඙аІЗа¶ЫථаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЪаІБа¶∞ а¶Ца¶∞а¶Ъ а¶Ха¶∞аІЗ ටඌа¶ХаІЗ а¶ЯаІНа¶∞аІЗа¶ЗථаІНа¶° а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗ а¶Па¶ђа¶В а¶Єа¶∞аІНа¶ђаІЛ඙а¶∞а¶њ ටඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ьа¶Яа¶Њ а¶ЄаІБа¶ЈаІНආа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Єа¶ЃаІН඙ථаІНථ а¶Ха¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඃඕаІЗа¶ЈаІНа¶Я а¶∞а¶Ха¶Ѓа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Єа¶єа¶ѓаІЛа¶Чගටඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶ѓаІБබаІНа¶ІаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ а¶Еа¶ЄаІНටаІНа¶∞а¶Єа¶є ඃඌඐටаІАа¶ѓа¶Љ а¶Єа¶∞а¶ЮаІНа¶Ьа¶Ња¶Ѓа¶З а¶єаІЛа¶Х а¶Жа¶∞ а¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ХаІЗа¶ЯаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ а¶Єа¶єа¶ѓаІЛබаІНа¶Іа¶Њ а¶ђа¶Њ а¶ЙථаІНථට а¶ХаІЛа¶Ъа¶ња¶Ва¶Єа¶є ඃඌඐටаІАа¶ѓа¶Љ а¶ЄаІБа¶ђа¶ња¶Іа¶Ња•§ ටа¶Цථ а¶Ха¶њ а¶ђа¶Ња¶Ха¶њ а¶ЬаІАа¶ђа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶≤аІЛа¶ХаІЗа¶∞а¶Њ а¶ЦаІЛа¶≤ а¶Ха¶∞ටඌа¶≤ ථගඃඊаІЗ а¶ѓаІБබаІНа¶ІаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶ЗටаІЗථ? а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є а¶ђа¶ЄаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶ђаІЗටථа¶Яа¶Њ а¶ЕථаІНටට ථගටаІЗථ а¶®а¶Ња•§ ටඌа¶З ථඌ?
а¶≠ඌඐථඌа¶З а¶ѓа¶Цථ ටа¶Цථ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶ЯаІБ а¶Йа¶≤аІНа¶ЯаІЛ а¶Ха¶∞аІЗа¶З а¶≠аІЗа¶ђаІЗ බаІЗа¶Ца¶њ а¶Жа¶ЄаІБа¶®а•§ а¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶Љ а¶ѓа¶Цථ а¶Жа¶ЫаІЗа¶З а¶Ж඙ටаІНටග а¶Жа¶∞ а¶ХаІАа¶ЄаІЗа¶∞а•§ а¶Іа¶∞аІБථ, а¶єаІНа¶ѓа¶Ња¶Б а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Іа¶∞аІБථ, а¶ѓаІЗ а¶Па¶З ඙аІБа¶∞аІЛ ඙аІНඃඌථධаІЗа¶Ѓа¶ња¶Ха¶Яа¶Њ පаІБа¶∞аІБ ඕаІЗа¶ХаІЗ ටаІЛ а¶Жа¶∞ ඙аІНඃඌථධаІЗа¶Ѓа¶ња¶Х а¶Ыа¶ња¶≤аІЛ а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶ЄаІНටаІЗ а¶Жа¶ЄаІНටаІЗ а¶єа¶≤аІЛа•§ ඁඌථаІЗ а¶Жа¶ЄаІНටаІЗ а¶Жа¶ЄаІНටаІЗ යටаІЗ බаІЗа¶ђа¶Ња¶∞ ඙а¶∞ а¶єаІБ ථඌඁа¶Х а¶ђа¶≤පඌа¶≤аІА а¶Па¶ђа¶В а¶ЕඐපаІНа¶ѓа¶З ථගа¶∞඙аІЗа¶ХаІНа¶Ј а¶ЄаІЗа¶З а¶Єа¶Ва¶Чආථ а¶ШаІЛа¶Ја¶£а¶Њ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ а¶≤а¶Ха¶°а¶Ња¶Йථ ථඃඊ, а¶Па¶∞ а¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගඣаІЗа¶Іа¶Х а¶Яа¶ња¶Ха¶Ња•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට ඐගපаІНа¶ђа¶ђа¶Ња¶ЄаІАа¶ХаІЗ බаІЗа¶ђа¶Ња¶∞ ඁට а¶Яа¶ња¶Ха¶Њ а¶Ѓа¶ЬаІБට а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЄаІЗа¶З а¶Яа¶ња¶Хඌ඙аІНа¶∞බඌථ පаІБа¶∞аІБ а¶єа¶ђаІЗ ඙ඌа¶Ба¶Ъ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ХаІБа¶°а¶Ља¶њ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶ђа¶ѓа¶Ља¶ЄаІА а¶ђа¶Ња¶ЪаІНа¶ЪඌබаІЗа¶∞ බගඃඊаІЗа•§ а¶Па¶ђа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶ЪаІНа¶ЪඌබаІЗа¶∞ а¶ђаІЗපගа¶∞а¶≠а¶Ња¶Ч а¶Еа¶Вපа¶З а¶ѓаІЗа¶єаІЗටаІБ ඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Жа¶∞ а¶Ха¶≤аІЗа¶ЬаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ ටඌයа¶≤аІЗ а¶Ха¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ха¶Ьථ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІНа¶єаІНа¶ѓа¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІАа¶∞ а¶Єа¶Ња¶єа¶Ња¶ѓаІНа¶ѓаІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶Яа¶ња¶Ха¶Њ ඙аІНа¶∞බඌථаІЗа¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶њ ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶Ња¶≤ථඌ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗථ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Х ඁයඌපඃඊ а¶Па¶ђа¶В а¶Еа¶ІаІНඃඌ඙а¶Ха¶∞а¶Ња•§ а¶≤а¶Ха¶°а¶Ња¶Йථ ථаІЗа¶З ඙аІБа¶≤ගප ථаІЗа¶З а¶°а¶Ња¶ХаІНටඌа¶∞බаІЗа¶∞ ථඌа¶∞аІНඪබаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђаІГа¶єаІО а¶Еа¶Вප ටа¶Цථа¶У а¶Па¶З ඙аІНа¶∞а¶Ха¶≤аІН඙аІЗ а¶ѓаІБа¶ХаІНට යථ а¶®а¶ња•§ а¶Па¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ха¶њ а¶ЄаІЗа¶З පගа¶ХаІНа¶Ја¶Ха¶∞а¶Њ а¶ђаІЗටථаІЗа¶∞ а¶ђаІЗපග ඙ඌа¶∞ගපаІНа¶∞а¶Ѓа¶ња¶Х බඌඐග а¶Ха¶∞а¶ђаІЗථ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Ж඙ථඌа¶∞ ඁථаІЗ а¶єа¶ѓа¶Љ? а¶Ха¶ЦථаІЛа¶З а¶®а¶ѓа¶Ља•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ථගපаІНа¶Ъගට а¶ХаІЛථа¶У ඙аІБа¶≤ගපа¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІА а¶ХаІЛථа¶У а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІНа¶єаІНа¶ѓа¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІА а¶Пඁථа¶ХаІА а¶ЕථаІНඃඌථаІНа¶ѓ а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶Па¶З а¶Ѓа¶єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶∞а¶ња¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶Љ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЄаІЗа¶ђа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ъа¶≤аІЗа¶ЫаІЗථ ටඌа¶∞а¶Њ а¶ХаІЗа¶Йа¶З а¶Па¶З а¶Іа¶∞ථаІЗа¶∞ බඌඐаІА а¶Ха¶∞а¶ђаІЗථ а¶®а¶Ња•§
а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ђаІЗටථа¶≠аІБа¶ХаІНට а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶Ъа¶Ња¶∞аІА (а¶ЕඐපаІНа¶ѓа¶З а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶њ) ටඌබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Є පаІЗа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Цඌටඌ ඕඌа¶ХаІЗ а¶Жа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Є පаІБа¶∞аІБа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Цඌටඌ ඕඌа¶ХаІЗа•§ පаІЗа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Цඌටඌඃඊ а¶≤аІЛථаІЗа¶∞ а¶За¶Па¶Ѓа¶Жа¶З, а¶ЧаІНа¶∞а¶Єа¶Ња¶∞а¶њ, а¶ЂаІБа¶ѓа¶ЉаІЗа¶≤, බаІИථගа¶Х а¶Ца¶∞а¶Ъ, а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞, а¶Ѓа¶Ња¶Ы а¶Ѓа¶Ња¶Ва¶Є, ඐථаІНа¶ІаІБ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ьථ, а¶Па¶Х а¶Ж඲බගථ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ а¶Ца¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ а¶Жа¶За¶Єа¶ХаІНа¶∞а¶ња¶Ѓ а¶Па¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶∞ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђ, а¶Жа¶∞ පаІБа¶∞аІБа¶∞ а¶Цඌටඌඃඊ а¶ЄаІНඐ඙аІНථබаІЗа¶∞а•§ а¶ЂаІНа¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶Яа¶Яа¶Њ ඙ඌа¶≤аІНа¶ЯаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶°а¶ЉаІЛ а¶Єа¶°а¶ЉаІЛ ඕаІНа¶∞а¶њ а¶ђа¶њ-а¶Па¶За¶Ъа¶ХаІЗ, а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶єаІНа¶ѓа¶Ња¶Ъа¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Х, а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ а¶ЯаІНа¶ѓаІБа¶∞ ථගබаІЗථ඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Ва¶Ха¶Х а¶ЂаІБа¶ХаІЗа¶Яа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З а¶єа¶ѓа¶Љ ථඌ. а¶Ѓа¶Ња¶Є පаІЗа¶ЈаІЗ а¶Яඌථ ඙ධඊаІЗ а¶Жа¶∞ а¶Яග඙аІН඙ථග ටаІЛ а¶Й඙а¶∞а¶њ ඙ඌа¶Уа¶®а¶Ња•§
ටඐаІЗ පඌථаІНටගа¶У а¶Жа¶ЫаІЗ, а¶ѓаІЗ а¶ѓа¶Ња¶З а¶ђа¶≤аІБа¶Х а¶Уа¶Яа¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ђа¶≤аІЗа¶З а¶Па¶З බаІБа¶Га¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶ЉаІЗа¶У а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶ХаІНа¶Ја¶£аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶єа¶≤аІЗа¶У а¶ШаІБа¶Ѓа¶Яа¶Њ а¶єа¶ѓа¶Ља•§ а¶ХаІЛඕඌа¶У а¶Па¶Х а¶ђа¶ЄаІНටඌ а¶Ъа¶Ња¶≤, а¶ХаІЛඕඌа¶У а¶Па¶Х а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶∞аІЗපථ, а¶ХаІЛඕඌа¶У ථඌඁඁඌටаІНа¶∞ а¶Уа¶ЈаІБа¶І а¶Ца¶∞а¶Ъ, а¶ХаІЛඕඌа¶У а¶За¶≤аІЗа¶Ха¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶Х а¶ђа¶ња¶≤, а¶ХаІЛඕඌа¶У а¶Яа¶ња¶≠а¶њ а¶ђа¶Њ а¶ЃаІЛа¶ђа¶Ња¶За¶≤ а¶∞а¶ња¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶Ь а¶Еа¶ХаІНа¶Єа¶ња¶ЬаІЗථаІЗа¶∞ а¶ѓаІЛа¶Чඌථ බаІЗа¶ѓа¶Љ а¶ђаІБа¶ХаІЗа¶∞ а¶ХаІЛа¶£аІЗа•§ а¶ЖටаІНඁපаІНа¶≤а¶Ња¶Ша¶Њ ථඃඊ а¶Уа¶Ба¶∞а¶Њ а¶ѓаІЗа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Жа¶ђаІНබඌа¶∞а¶Яа¶Њ а¶Ьඌථඌඃඊ ටඌටаІЗ а¶ХаІЛථа¶У а¶Єа¶Ва¶ХаІЛа¶Ъ ඕඌа¶ХаІЗ ථඌ, а¶∞ඌටаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Жа¶≤аІБа¶≠ඌටаІЗ а¶ЪаІЛа¶Ц а¶Ъа¶ња¶Х а¶Ъа¶ња¶Х а¶Ха¶∞аІЗ ටаІЛа¶≤аІЗа•§
඙а¶∞ගපаІЗа¶ЈаІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ьа•§ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗ ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓаІЗа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь ථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Я а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶Єа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ьа¶Яа¶Ња¶ХаІЗ ආගа¶ХඁටаІЛ ඙ඌа¶≤ථ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗ ටа¶Цථа¶З а¶ѓа¶Цථ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආග඙ටග (ඁඌථаІЗ а¶Жа¶ІаІБථගа¶Х а¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞ ථаІЗටඌ а¶Жа¶∞ а¶ХаІА) ථගа¶∞඙аІЗа¶ХаІНа¶Ј а¶Па¶ђа¶В а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Х ඁටඌබа¶∞аІНපаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞аІЗ а¶ЙආаІЗ ථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Я а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶ХаІЗ බගඃඊаІЗ ථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Я а¶Ха¶Ња¶Ьа¶Яа¶њ а¶Ха¶∞ඌටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗа¶®а•§ а¶Па¶Цථ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶ЂаІНа¶∞а¶ѓа¶ЉаІЗа¶° а¶Жа¶ЫаІЗ а¶За¶ЧаІЛа¶У а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶Хටа¶Яа¶Њ а¶Єа¶Ђа¶≤ටඌ а¶Жа¶ЄаІЗ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Ња¶З බаІЗа¶Ца¶Ња¶∞а•§
Have an account?
Login with your personal info to keep reading premium contents
You don't have an account?
Enter your personal details and start your reading journey with us
Design & Developed by: WikiIND
Maintained by: Ekhon Dooars Team