



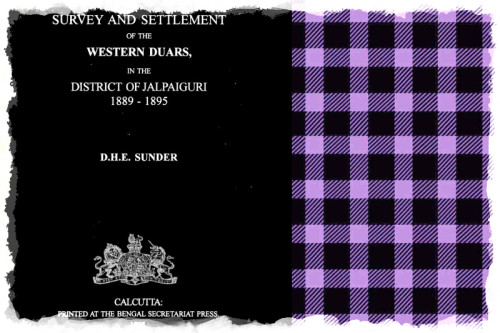
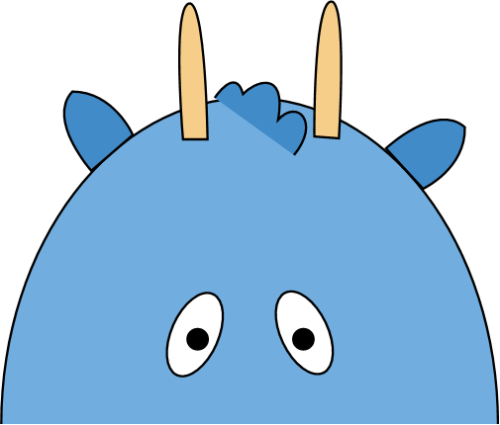





 শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
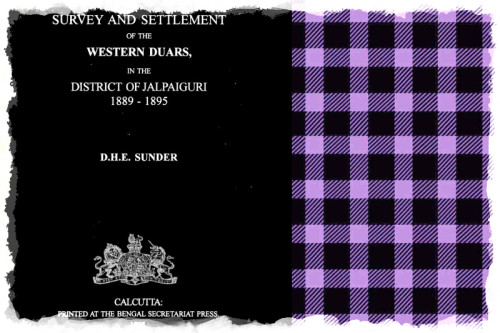
যে জেলার সদর শহর হিসেবে ‘টউন’ জলপাইগুড়ি আত্মপ্রকাশ করল সে চেহারাটা কেমন ছিল? এর চমৎকার একটি পরিচয় ধরা আছে সন্ডার্স সাহেবের বিবরণীতে। তার নাম ‘Survey and Settlement of the Western Duars in the District Of Jalpaiguri 1889-1895’. ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স হল বর্তমানের আলিপুরদুয়ার জেলার পুরোটা এবং জলপাইগুড়ি জেলার যে অংশটা তিস্তার পূর্ব পাড়ে অবস্থিত, সেটা। সন্ডার্স সাহেব অবশ্য তিস্তার পশ্চিমপাড়ে আমবাড়ি-ফালাকাটা মহকুমাটিও যুক্ত করেছিলেন, কিন্তু বৈকুন্ঠপুর পরগণা বাদ যায়।
আলিপুরদুয়ার কয়েক বছর আগেও জলপাইগুড়ি জেলারই অংশ ছিল। সন্ডার্স যখন তাঁর সার্ভে করেছিলেন তখন ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্সের পুরোটাই জলপাইগুড়ি জেলার অংশ, বলতে গেলে জেলার সিংহভাগ। সেই জেলার সদর শহর হিসেবে জলপাইগুড়ি টাউনের অবস্থান ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্সের ঠিক সীমানায়, কিন্তু তিস্তার পশ্চিম পাড়ে। এইজন্য বলা হয় যে জলপাইগুড়ি টাউন আসলে ডুয়ার্সে নয়।
তবে, ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স মাত্র তিন বছরের জন্য আলাদা একটা জেলা হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছিল। সেটা ছিল ১৮৬৫-এর নভেম্বর থেকে ১৮৬৮-এর ডিসেম্বর।
এই ওয়েস্টান ডুয়ার্স সম্পর্কে হান্টার সাহেব লিখেছিলেনঃ “The Bhutan Duars, the tract which was annexed at the close of the war of 1865, is a flat level strip of country, averaging about 22 miles width, running along the foot of the Bhutan hills, its chief characteristics are the numerous rivers and hill streams which intersect it in every direction, and the large tracts of sal forest and heavy grass and reed jungle, interspersed with wild cardamoms.”
নতুন টাউন হিসেবে জলপাইগুড়ি শহরের কথা হয়তো লোকে জানতে শুরু করেছিল। কিন্তু জেলা জলপাইগুড়ি ছিল বঙ্গবাসীর কাছে তখনো অস্পষ্ট। প্রায় অজানা। সেদিক থেকে বিচার করলে সন্ডার্স সাহেবের এই সার্ভে রিপোর্ট উৎসুক ব্যক্তিদের কাছে এই জেলার রহস্য প্রথম উন্মোচন করেছিল বললে ভুল বলা হয় না। এই রিপোর্টের একটি সংস্করণের ভূমিকায় তাই লেখা হয়েছেঃ The Sunder’s Survey and Settlement Report is a worthy reading book which not only helps in enhancing knowledge and information about the Duars region of Bengal to all common readers but it can be used as a valuable and first hand data source to the scholars, researchers, academicians, demographers, environmentalists, journalists, tourists, administrators, political leaders and policy makers.’ (Introduction by Dr. D.C. Roy)
উক্ত উদ্ধৃতির একটি শব্দও মিথ্যে নয়।
সন্ডার্স সাহেবের এই রিপোর্ট পড়লে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেটা হলো টাউন জলপাইগুড়ির সাথে জেলা জলপাইগুড়ির একটা বিরাট পার্থক্য ছিল। ইংরেজদের গড়ে তোলা টাউনটির সাথে জেলার যেন কোনও মিলই নেই। এই কারণেই টাউন জলপাইগুড়িতে জেলা জলপাইগুড়ির প্রতিফলন প্রায় নেই। সন্ডার্সের এই রিপোর্ট অজস্র কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য লুকিয়ে রয়েছে। এই রত্নভান্ডার থেকে কয়েকটি তুলে দিই।
ডুয়ার্সে সংখ্যাগুরু হল রাজবংশীরা। তাঁদের সংখ্যা ওই সময় ১২৩,৪৩৯। মুসলিমদের সংখ্যা ৫৩,৫৬২। মুসলিমরা সকালে পান্তাভাত খেতে ভালোবাসে এবং তাঁরা চিড়ে তৈরি করে না। বাচ্চার বয়স দু-বছর হলেই রাজবংশী এবং মুসলিম মায়েরা তাঁদের পিঠে বেঁধে নিয়ে কাজে যায় এবং দুই প্রকার মায়েরাই বাচ্চাদের প্রচুর প্রশ্রয় দিয়ে থাকে।
রাজবংশী জোতদারেরা কার্তিক মাসে লক্ষ্মীপুজো করে এবং তাতে হাঁস বলি দেওয়া হয়। পুজোর পর জোতদার মশাই তাঁর প্রজাদের চাল-ডাল-লংকা-লবণ-পেঁয়াজ সমেত হাঁসও বিতরণ করেন এবং মহাভোজ হয়।
একবার ভুটানের দেবরাজার সাথে কুচবিহারের গন্ডগোল বাঁধলে ভুটানের রাজা বেশ কিছু রাজবংশী পরিবার সমেত রাজাকেও ভুটানে ধরে নিয়ে যান। বিভিন্ন ঘটনার পর ভুটানে আটকে থাকা রাজবংশীরা জানান যে তাঁদের জাতিগত অস্তিত্ব নিয়ে সমস্য হচ্ছে। তখন রাজা তাঁদের মুক্তি দেন। কিন্তু সমতলে ফিরে এলে তাঁদের রাজবংশী বলে কেউ স্বীকার করল না। এই রকম বাষট্টিটি পরিবার পরে ‘দোবাসিয়া’ (দোভাষিয়া) নামে পরিচিতি লাভ করে। নিজেদের ভাষা এবং ভুটানি ভাষা জানা থাকার কারণেই এই নামকরণ।
মেচ-দের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সন্ডার্স সাহেব লক্ষ করেছিলেন যে তাঁরা মিথ্যে কথাকে কী পরিমাণ ঘৃণা করে। তাই তিনি মেচ-দের সত্যের শপথটি পুরো অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। সেটা হলোঃ I will speak the truth. If I speak not the truth may I and my wife and may destroyed by Mahakal. Let tiger and beer kill us. Let sickness seize us and all belonging to us. Let us all perish and die.
গারো সমাজে পরকীয়া করার ফাইন তেষট্টি টাকা। তবে পরকীয়া প্রমাণিত হওয়ার পরও যদি সংসার টিকিয়ে রাখতে চায় তবে ফাইন তিরিশ টাকা।
ভুটিয়াদের (তখনো ডুয়ার্সে তাঁদের বসবাস ছিল) প্রিয় পানীয় হলো চা যেটা আসে তিব্বত আর চীন থেকে। ঠান্ডা জলে শুকনো পাতা মিশিয়ে, কিঞ্চিৎ সোডা দিয়ে সেদ্ধ করে। তারপর লবণ-মাখন মিশিয়ে বাঁশের চোঙায় ঢেলে পান করা হয়। তবে চা তারা সব সময় পান করে কোনও না কোনও খাদ্য সহযোগে। অন্যদিকে, তারা চমৎকার হাঁড়িয়াও তৈরি করে যার দাম এক বোতল এক আনা।
টোটো-রা সন্ডার্স সাহেবকে বলতে পারেনি যে তারা কোথা থেকে এসেছে। ওই সময় মাত্র ছত্রিশ ঘর টোটো ছিল। তাদের জমিতে তখন থেকেই কোনও অজ্ঞাত কারণে আর কমলালেবু ফলত না। সবগুলি গাছ মরে গিয়েছিল। কিন্তু আমগাছ ছিল অনেকগুলি। আট কিলোমিটার দূরে ভুটানি এলাকা থেকে কমলালেবু এনে টোটোরা ব্রিটিশ এলাকায় বিক্রি করত। কিন্তু তাদের জমি ছিল উর্বর আর কোন জমিদার-মহাজন না থাকায় টোটোরা বেশ শান্তিতে ছিল বলে সন্ডার্স সাহেবের মনে হয়েছিল।
জলপাইগুড়ি টাউনের বাইরে বাকি জেলায় মিডিল ইংলিশ স্কুল ছিল তিনটে এবং ছাত্র ছিল ৬৮ জন। লোয়ার আর আপার প্রাইমারি স্কুল ছিল ৯৫টা। তার পড়ুয়া ছিল দু-হাজারের বেশি।
বোঝাই যাচ্ছে যে টাউনের বাইরে বাকি যে জেলা তা কত বৈচিত্র্যে ভরপুর ছিল। টাউন গড়ে ওঠার পর বেশ কয়েক দশক নবাগত পুরবাসী ব্যস্ত ছিল নিজেদের সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে। এর মধ্যেই অল্প অল্প করে ছড়িয়ে পড়ছিল ইস্টার্ন ডুয়ার্সে। গোটা জেলায় বৈকুন্ঠপুর ছাড়াও আরো এক ডজন মহকুমা। তার মধ্যে ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্সেই এগারটা। তিস্তার এ পাড়ে বারো নম্বর মহকুমাটা ছিল আমবাড়ি-ফালাকাটা। তখন টাউন থেকে শিলিগুড়ির রাস্তাটা যেত ঠিক আমবাড়ির মাঝখান দিয়ে আর রেল লাইনটা যেত কোনা দিয়ে।
এইসব মহকুমায় ইংরেজদের আপিস-টাপিস বসাতে হয়েছে। চাকরি করার জন্য লেখাপড়া জানা বাবুদের পাঠাতে হয়েছে। তারপর চায়ের বাগান। কাঠের ব্যবসা। তামাকের ব্যবসা এইসব আরো হরেক কাজে টাউন থেকে লোকজনকে যেতে আসতে হয়েছে। থাকতে হয়েছে। এইভাবে আস্তে আস্তে ভাটিয়াদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে জেলার পরিচয়।
সে এক আশ্চর্য জেলা। বাকি বাংলার সাথে তার মিল যত অমিল তার চেয়ে অনেক বেশি। এখানে বাংলা ফুরিয়ে গেছে। শুরু হচ্ছে নতুন একটা সংস্কৃতি যা নেমে এসেছে পাহাড় থেকে। চতুর্থ হিমযুগের শেষে যখন হিমালয় থেকে নেমে আসা বিপুল জলরাশির কারণে উত্তর ভারতের সমভূমি জলমগ্ন, বৃহত্তর বাংলার দক্ষিণ অংশে সেই জল তুলনায় বেশিদিন স্থায়ী হয়েছিল। সেই সময় সমুদ্র থেকে উঁচুতে থাকা ভূখন্ডেই বিকশিত হচ্ছিল আদি ভারতীয় সভ্যতাগুলি। দক্ষিণ ভারতের মালভূমিতে। উত্তরবঙ্গের উত্তরে। বেদ রচনা শুরুর আগেই এইসব অঞ্চলে সভ্যতার জন্ম। কামরূপ (জ্যোতিষপুর) এবং তার পূর্বে প্রাগজ্যোতিষপুরে প্রাকবৈদিক যুগেই সভ্যতা এই কারণেই গড়ে উঠেছিল।
পান্ডবরা এদিকে আসেন নি মানেই যে এদিকটা তুচ্ছ, এটা একটা বিশেষ ধারনামাত্র। বস্তুতঃ ‘আর্য সাহিত্যের’ রচয়িতারা পুন্ড্রবর্ধন সম্পর্কে খুব বেশি জানতেন না। অন্যদিকে, যে সত্য সম্পর্কে আর্য-রা প্রচুর শ্রদ্ধাশীল তা মেচ-দের প্রতিজ্ঞায় পাওয়া গেছে যাদের আসলে খুব একটা পাত্তাই দেওয়া হয় নি। যদিও বৈদিক রীতি-নীতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কামরূপ-প্রাগজ্যোতিষপুরে প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল। কোচরাজারা বিষ্ণুভক্ত হয়ে পড়েন এবং রাধাবিহীন কৃষ্ণকে গ্রহণ করেন। জলপাইগুড়িও ছিল ‘বৈকুন্ঠপুর’। যদিও দুর্গাপুজো ছিল মূলত শহুরে। রাজবংশীদের মধ্যে এর প্রভাব অনেকদিন পর্যন্ত প্রায় ছিলই না। কিন্তু একটা পুজো তাঁরা কুচবিহারের রাজবংশীদের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণেই করতেন। সেটা হলো কালীপুজো। এই পশ্চাদপটের জন্যই গত শতকের সাতের দশকের শেষের দিকে টাউনের কালীপুজো নানাবিধ রোমাঞ্চ আমদানি করতে শুরু করে। কিন্তু সে অন্য গপ্পো।
সন্ডার্স সাহেবের রিপোর্টে টাউন জলপাইগুড়ি সম্পর্কে কিছু নেই। কিন্তু ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্সের বিবরণ পড়লে বোঝা যাবে যে টাউন ছিল সেই রোমাঞ্চকর জেলার হেড আপিস। এটা বুঝলেই সেকালের টাউনের রোমাঞ্চটা একালে বসে কিঞ্চিৎ আঁচ করা যাবে। সন্ডার্স সব বিষয়ে নজর দিয়েছিলেন। তিনি ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্সের নেশা-ভাং বিষয়ক তথ্যও দিয়েছেন। কমন নেশার বস্তু ছিল আফিং। লিকারের প্রচলন মূলত ছিল চা শ্রমিকদের মধ্যে আর গাঁজা জনপ্রিয় ছিল বিহারের ওদিক থেকে মোষ চরাতে আসা গো-পালকদের মধ্যে। তামাকপাতাজাত ধূমপান তো ছিলই। এই অঞ্চলে এক ধরনের তামাকপাতার আকার হত হাতির কানের মত বড়।
টাউনে সন্ডার্স সাহেবের একটা মূর্তি থাকা উচিত ছিল।
(ক্রমশ)
Have an account?
Login with your personal info to keep reading premium contents
You don't have an account?
Enter your personal details and start your reading journey with us
Design & Developed by: WikiIND
Maintained by: Ekhon Dooars Team