



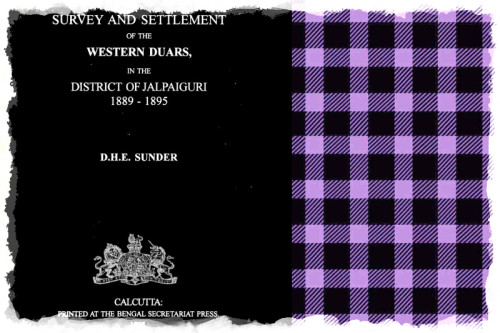
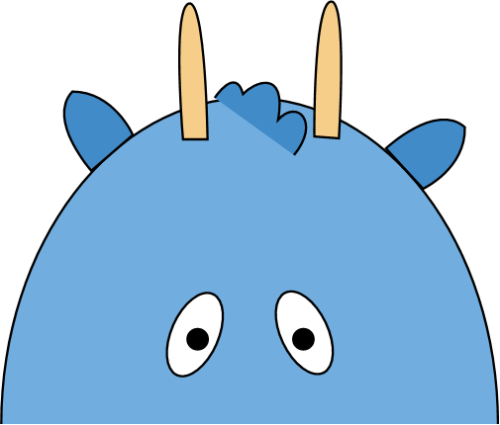





 নবনীতা সান্যাল
নবনীতা সান্যাল

আবার বিশুদার সঙ্গে দেখা। প্রথমে টাইপ রাইটার, তারপর ফটোকপির দোকান, শেষে কাগজ কলমের দোকান সব পার হয়ে বিশুদা এখন প্রায় বেকার। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সামনের রাস্তায় দেখা হল। উল্টোদিকে কালীপুজোর প্যাণ্ডেল, হৈ চৈ, এর মধ্যে তার খানিক এলোমেলো কথা শোনার পর আমি বললাম, এই যে এতো কথা বলছি আমরা, কী ছিল, কী আছে, কী গেছে। এসবের কী ভ্যালু! লিখিত ডকুমেন্ট কই?
বিশুদা একটা পান খেয়ে বলল, তা মার্কেট ভ্যালু যদি বল তো তেমন একটা নাই। কী থাকল আর কী গেল তাতে লাভ ক্ষতির দর আমি ঠিক বলতে পারিনা। আমি তো চিরকাল লস্ করেই কাটালাম। তবে মানে, এই যে আমি যা যা দেখছি, বা যা দেখছি তার কথার একটা ধরতাই দিতে পারি এই আরকি!
আমি বললাম, সে কথাই তো বলছি! সে তো আমিও বুঝতে পারলাম। বললাম, কিন্তু সবসময়ই আমি যা দেখি তুমি তা নাও দেখতে পারো, তাই না?
বিশুদা রেগে বলল, তা হতেই পারে, কিন্তু তাতে তো ইতিহাস বদলাচ্ছে না।
খুব বিনীত স্বরে এবার বলি, ইতিহাস মানেই তো পুরোনো কথা, তাই না! তা নিয়ে শেষকথা কী বলা চলে!
কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল বিশুদা---
আমি বললাম, এজন্যই লিখিত ইতিহাস দরকার।
বিশুদা এবার যুক্তি পেয়ে গেছে, মাস্টারসুলভ ভঙ্গিতে বলল, না না, সেইটাও ফাইনাল না। হর্ষবর্ধন খুব দানধ্যান করতেন, এইটা লিখল কে? হিউয়েন সাঙ। তাকে কে দেখেছে? কেউ না। তার কলমে, তার চোখে আমরা একটা সময়কে দেখলাম। সেটা সত্যি না অর্ধসত্যি কে জানে? সবটাই রিলেটিভ ব্যাপার!
আমি মনে মনে বললাম, পথে এসো। মুখে বললাম, তার মানে দেখা যাচ্ছে লিখিত ইতিহাস এবং মৌখিক ইতিহাস কোনোটাই শেষ কথা না। আবার এ দুটির মধ্যে বিরোধ থাকাও অস্বাভাবিক না। এখন যদি...
হাত তুলে আমাকে থামিয়ে বিশুদা বলল, থামো, ওই যদির কথা নদীতে! এখন দরকারি কথা কিছু থাকে তো বল। নাইলে বাদ দাও।

আমি বললাম, সেই নদীর কথাতেই তো আসতে চাইছি। চল হাঁটি।
কথা শুরু হল এরপর। শিলিগুড়ির প্রধান নদী বলতে তো তিনটি-- মহানন্দা, ফুলেশ্বরী, আর বালাসন?
বিশুদা হাত তুলে থামিয়ে দিল আবার, এই জ্ঞান নিয়ে লিখতে এসেছো! শিলিগুড়ি শহরেই রয়েছে পাঁচটি নদী – মহানন্দা, পঞ্চানই, ফুলেশ্বরী, জোড়াপানি, মহিষমারী। আর মহকুমা জুড়ে আরও অনেক নদী -- চামটা, বালাসন, মেচি, হূলিয়া, খেমচি, গিলাণ্ডি, মাগুরমারী আরও কতো।
আমি বললাম তবে সব নদীই আজ বিপন্ন, দূষিত। জনসংখ্যার বিপুল চাপ আর সচেতনতার অভাব এর অন্যতম কারণ।
গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বিশুদা বলল, কারণ তো বহু। কোনটা বা কই! আর আগে বরং শহরের নদী আর তার দুই তীরের কথা বল, শুনি । তারপরে বলবো তার এখনকার অবস্থা।
আমি বলে চললাম - শিলিগুড়ি শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে মহানন্দা নদী। কার্সিয়ং এর পূর্ব দিকে অবস্থিত মহালদিরাম অঞ্চলে এর উৎপত্তি। নদীটিকে মহানদী নামেও ডাকা হয়। সমতলে প্রবেশ করার পর এই নদী শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে শিলিগুড়ি শহরের নিকটবর্তী ফাঁসিদাওয়া হয়ে, মালদহ শহরের উপর দিয়ে বাহিত হয়ে বিহারের পূর্ণিয়া হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায় পদ্মার সঙ্গে মিশে গিয়েছে মহানন্দা। মহানন্দার কোনও উপনদী নেই। তবে, পাহাড়ে এ নদীর সঙ্গে মিশে গিয়েছে অনেক ছোটখাটো নদী। যেমন-- শিবখোলা, বাবুলখোলা, যোগীখোলা, সিংগীঝোরা ....আরও কতো—
একটু থেমে আমরা এবার একটা চা দোকানে বসলাম। চা অর্ডার দিয়ে বিশুদার দিকে তাকিয়ে বললাম, কী এইবার সব ঠিকঠাক বলছি তো? আমি বলছি না কিন্তু! তথ্য পড়ে, জেনে নিয়ে তবে বলছি।
চা হাতে নিয়ে বিশুদা বলল, হ্যাঁ হে-- সে বুঝে গেছি। তবে, এই মহানন্দার উল্লেখ কিন্তু বহূ প্রাচীনকালেও করা হয়েছে। তথ্যপ্রমাণ নেই বলে তোমাকে বলতে পারছি না বটে-- তবে, চিরকাল যে বর্ষাকালে নদীর জল বাড়ে আর শীতে কমে-- এ আমার নিজের চোখেই দেখা। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়েও এ নদীতে মাছ পাওয়া যেতো। আর এ নদীতে পলি, বালি দুই মাটিই আছে। অনেককাল আগে থেকেই মহানন্দার পাড়ের পলিমাটি বিক্রি হতো, বুঝলা?

ইতিমধ্যে আরেক রাউন্ড চা এসে গেল। আমি ঘাড় নেডে সম্মতি জানালাম। তারপর বললাম, আর বাকি নদীগুলির কথা শুনবে না? বিশুদা হাত দিয়ে ইংগিত করলে আমার কথাগাড়ি আবার গড়গড়িয়ে চলতে লাগল, আরেক নদী বালাসন। দার্জিলিং-এর কাছে ঘুম পাহাড়ের কাছে লেপচাজগৎ শিখর এর উৎসস্থল। সমতলে নেমে নদীটি দুটি ধারায় বিভক্ত হয়েছে-- বুড়ি বালাসন আর বালাসন। বুড়ি বালাসন বাগডোগরা অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। শিলিগুড়ির পশ্চিম দিক দিয়ে এগিয়ে নৌকাঘাট অঞ্চলে এই নদীর সংযুক্ত ধারা মহানন্দা নদীর সঙ্গে মিশেছে। বালাসন নদীতেও বিভিন্ন নদী এসে মিশেছে-- দুধিয়া ঝোরা, মাঞ্জা ঝোরা, রঙ রঙ খোলা, পুলুং ডুং খোলা, ভীম খোলা, রক্তি খোলা, রোহিণী খোলা প্রভৃতি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বালাসনের উল্লেখযোগ্য উপনদীগুলি হল-- রাং টাং নালা, পানচোলান নালা। এই দুটি উপনদীই তিনধারিয়া পাহাড়ের থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই দুই নদীর ওপর দিয়ে চলে যায় দার্জিলিং-এ যাওয়ার ট্রয় ট্রেন।
বিশুদা শুনছিল। মনোযোগ দিয়েই শুনছিল। ঠাণ্ডা চা টুকু কুলকুচো করে একঢোঁকে খেয়ে নিয়ে বলল-- ঠিকই আছে। তবে, কথা আরও আছে। বালাসন নদীতে বালির রঙ সোনার মতো- তাই এর নাম বালাসন। বর্ষাকালে এই নদীর জল পাহাড়ের বালি পাথর বহন করে আনে, যা সমতলের নদীগর্ভকে উঁচু করে তোলে। অথচ, এই নদী থেকেই বালি পাথর তুলে নেয় মানুষ। অদ্ভুত! নিজের ভাল তো পাগলেও বোঝে! যাগ্গে, এই বালিতে আবার মাটি নেই অভ্র আছে। শোনা কথা, বালাসন আগে তরাই সমতলে প্রবল বেগে প্রবাহিত হতো-- নদীতে খাল কাটা হলে বালাসনের মূল প্রবাহ সরু হয়ে বুড়ি বালাসনের রূপ নেয়। আর, বর্তমান বালাসন অপেক্ষাকৃত বড় নদীর রূপ নেয়। সে অবশ্য অনেক নদীই এমনভাবে খাত বদল করে-- সে যাক, বাকি নদীর কথা শুনি।
আমি বললাম, আর আছে মেচি, চামটা, মহিষমারী, পঞ্চনই, মাগুরমারী প্রভৃতি। নেপাল সীমান্তের সিঙ্গালিলা পর্বতশ্রেণি থেকে মেচি নদীর উৎপত্তি হয়েছে। সমতলে নেমে এই নদী নকশালবাড়ি অঞ্চলের উপর দিয়ে বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় প্রবেশ করেছে। মেচিতে এসে মিশেছে কিয়াং খোলা, আসলী ঝোরা, মানা ঝোরা। বর্ষাকালে অন্যান্য পাহাড়ি নদীর মতো মেচি নদীতে বান ডাকে। অন্য সময় জল থাকেনা। এ নদীর পশ্চিম পাড়ে নেপাল। শিলিগুড়ি মহকুমার চামটা নদীর উৎপত্তি হয়েছে সুকনার মহানন্দা অভয়ারণ্য থেকে। সুকনা, শালবাড়ি পেরিয়ে এই নদী পঞ্চনই নদীতে মিশেছে। পঞ্চনই নদীর উৎপত্তি সুকনার কিছুটা উপরি অংশ থেকে। অনেকের মতে, অনেকগুলি ঝোরার মিলিত জলের আধার যে সুকনা লেক-- তাই পঞ্চনই নদীর উৎসস্থল। মোহরগাঁও গুলমা চা বাগানকে পাশে রেখে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়েছে পঞ্চনই। ৩১নং জাতীয় সড়ক অতিক্রম করে শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন কলোনি অতিক্রম করে থুম্বা জোত অঞ্চলে গিয়ে পঞ্চনই মহানন্দায় মিলিত হয়েছে।
ফুলেশ্বরী, জোড়াপানি নদীগুলির উৎসস্থল পর্বত নয়। এই দুই নদী বনভূমি থেকে বেরিয়ে এসেছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে মাগুরমারী নদী। বাগডোগরার উত্তরাঞ্চল ঘেঁষে হূলিয়া নদী প্রবাহিত। ব্যাঙডুবি ও তার উত্তর অঞ্চলের বনভূমি ও ঝোরা থেকে হূলিয়া নদী বেরিয়ে এসেছে। খেমচি, গিলাণ্ডি, বাতারিয়া নদীগুলি এসেছে নকশালড়ির উত্তরের বনভূমি থেকে। নকশালবাড়ি পার হয়ে এই নদীগুলি দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে।
বিশুদা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর বলল, সে সব তো বুঝলাম। কিন্তু, এখনকার অবস্থা জানো কিছু? বন্যা হয়েছে কতো তা জানো? শোনো তাহলে-- ১৯৬৮ সালে বড় বন্যা হয় জলপাইগুড়ি শহরে। তিস্তার জল ছাপিয়ে যায়। শিলিগুড়ি শহরে তেমন বড় বন্যা হয় নি ঠিকই, তবে, প্রধানত মহানন্দা আর বালাসন নদীতে ছোটখাটো বন্যা হয়ে গেছে বেশ ক'বার। ২০০৯ সালে বালাসন নদীতে বাণ ডাকে। বন্যার জলের স্রোতে বালাসন নদীর উপর নির্মিত রেলব্রিজ ভেঙ্গে পড়েছিল। গত বছরেও একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ব্রিজ। মহানন্দা নদীতে বাড়াবাড়ি না হলেও জলপাই মোড় থেকে মেডিক্যাল মোড়, ফুলবাড়ি অঞ্চলে ঢুকে যায় মহানন্দার জল। এই যে বললে, মহানন্দার উপনদী নেই। থাকলেই জল বাড়তো। সম্ভবত সেজন্যেই বন্যার হাত থেকে বেঁচে গেছে শিলিগুড়ি।
তবে স্বাভাবিক বন্যা না হলেও, ভরসা করার মতো পরিস্থিতিও নাই। মহানন্দা নদীর অববাহিকা যদি প্লাবিত হয় তবে, জল বের হওয়ার সুযোগও কিন্তু নাই। তার পরেও আছে দূষণ। শিলিগুড়ি শহর এবং আশপাশের অঞ্চলের প্রায় সব নদীই দূষিত। নদীর নাব্যতা কমে গেছে। নদীর দুধারে এমনকি চরের মধ্যেও মানুষজন বসবাস করে। তারপর আছে নদী থেকে ইচ্ছেমতো বালি পাথর তুলে নেওয়া। যতো দিন যাচ্ছে নদীর স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছে, রুগ্ন হয়ে যাচ্ছে নদীগুলো। গাছপালা কাটার জন্য বৃষ্টি তো এমনিতেই কমে গেছে। নদীর ধারা শুকিয়ে গেছে।
আমি বললাম, হ্যাঁ, এখন মহানন্দারর দুধারে রয়েছে হাজার খানেক ঘরবাড়ি। শহরের জনসংখ্যার চাপ আর দূষণ নষ্ট করে ফেলেছে নদীর স্বাভাবিক গতি। মহানন্দার দুধারে খাটালও তো অনেক। প্রাকৃতিক বর্জ্য এবং রাসায়নিক বর্জ্যের দূষণও প্রবল। দূষিত পদার্থ সব সময়ই নদীর জলে মিশছে। নদীর জলে দেবদৃবীর মূর্তি বিসর্জন হয়। ফেলা হয় পচা ফুল বেলপাতা। পূজার প্রযোজনে মানুষের তৈরি করা ঘাট গড়ে ওঠে। শিলিগুড়ি শহরের হাইড্রেনগুলিও মুক্ত হয় নদীতে। ট্রাক বাস ধোওয়া হয় নদীর জলে। নদীর ধারেই বসে হাটবাজার। ফলে, আবর্জনা মেশে নদীতে। শহরের পূর্ব প্রান্তে ফুলেশ্বরী নদীর অস্তিত্ব আজ সম্পূর্ণ বিপন্ন। নদীর ধারেই রয়েছে বাজার। নদী ঘেঁষে গড়ে উঠেছে বহুতল। মহানন্দাসহ বিভিন্ন নদীর চর জবরদখল করে বসতি তৈরি হয়েছে। গুলমা অঞ্চলের মহিষমারী নদী তো একেবারে নর্দমায় পরিণত হয়েছে। পঞ্চনই নদীও দূষিত। বালাসন নদীখাত হয়ে উঠেছে বালি পাথর তুলে বিপজ্জনক। মহানন্দা বহন করছে কলিফার্ম ব্যাকটেরিয়া! যা প্রাণীর দেহের বর্জ্য থেকে এসেছে বলেই অনুমান করা হচ্ছে। মাগুরমারী নদী কচুরিপানায় ভরে গেছে। হূলিয়া নদীও শুকিয়ে গেছে। চামটাও শীর্ণকায়, দূষিত। ২০১৮ সালে চামটার ভয়াবহ বন্যা ভাসিয়ে দিয়েছিল সংলগ্ন শ্রমিক বস্তি। গিলাণ্ডি, খেমচিতেও বন্যা হয়েছে একাধিকবার। কমেছে নদীগুলির জলধারণ ক্ষমতা। চাষের জমির জন্য এই নদীগুলি থেকে পর্যাপ্ত জল আর পাওয়া যাচ্ছেনা। শিলিগুড়ি এবং সংলগ্ন নদীগুলির অবস্থা খুবই খারাপ। ছোট নদীগুলির কথা সমীক্ষায় আসেনি, তবে, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সমীক্ষায় দূষিত নদী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে মহানন্দা নদী। সম্প্রতি দেশের দূষিত নদীগুলির তালিকাতেও স্থান পেয়েছে মহানন্দা নদী।
বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিকল্পনা রয়েছে। কিছু ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হচ্ছে-- যেমন, নদীমুখী নালাগুলিকে বন্ধ করে অন্য পথে নোংরা জল পরিশোধন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরিশোধন কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি তরফে। সেমিনারে আলোচনার বিষয় হিসাবে উঠে আসছে শহরের নদী ও তার সুরক্ষা। নদীর তীরে গড়ে ওঠা শ্মশানঘাটগুলির বৈদ্যুতিককরণ করা হচ্ছে। তবে, সবার আগে দরকার নাগরিক সচেতনতা। নদীর ধারে খাটালগুলিকে সরিয়ে ফেলা দরকার অবিলম্বে। মহানন্দা অ্যাকশন প্ল্যান ঘোষিত হয়েছে। প্লাষ্টিক বন্ধ হয়েছে শহরে। আইন করে বন্ধ করা হয়েছে নদীতে কাপড় কাচা। বন্ধ করা হয়েছে স্নানের ঘাট। কিন্তু, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সবই চলছে। অচেতন, অবৈজ্ঞানিক , মনোভাব এবং আইন না মানার ধৃষ্টতা নদীগুলিকে দূষিত করেই চলেছে, যার ফলভোগ সকলকেই করতে হচ্ছে এবং আরও করতে হবে। চেতনা বৃদ্ধি না হলে পরিস্থিতি পাল্টাবে বলে মনে হয় না।
মাত্র পাঁচ দশকের মধ্যে নদীগুলিকে নর্দমা বানিয়ে ফেললাম আমরা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল বিশুদা। কী স্রোত! কী নাব্যতা ছিল নদীগুলোতে! এই মহানন্দা নদী থেকে আশির দশকেই হবে বোধহয়, গঙ্গার দিকে অভিযাত্রায় বেরিয়েছিলেন শিলিগুড়ি কয়েক জন মানুষ। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে গেল বিশুদা-- সব নষ্ট করে ফেলেছি আমরা। বেকুবের দল সব। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে গভীর গলায় বলল, নদী তো মা। তাকে আবর্জনা দিয়ে ভরিয়ে ফেলল। ছিঃ! এমন করে কেউ বড় হয়? হতে পারে কখনও?
হ্যাঁ, বাড়াবাড়ি তো বটেই। শহর বড় হয়ে উঠল না ছোটই থেকে গেল, তা আমি অবশ্যই জানি না বিশুদা। তবে, জুতোর মাপে পা কেটে বসানোর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি মনে পড়ে গেল।
বললাম, এর থেকে কী পরিত্রান নেই?
বিশুদা উঠে পড়ে জোরে হাঁটা লাগাল। বিড়বিড় করে মাথা নেড়ে বলতে বলতে হাাঁটা লাগাল, বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে... দাও ফিরে সে অরণ্য-- লও হে নগর!
কথা ঠিকই। তবে আর এখন উপায় কী? আর কি ফিরবে সেইসব স্বচ্ছতোয়া? ভাবতে ভাবতে আমিও এবার বাড়ি ফেরার পথ ধরলাম।
গ্রন্থ ঋণ:
১. শিলিগুড়ি তরাইয়ের ইতিবৃত্ত: সম্পাদনা, ড: রতন বিশ্বাস।
২. শিলিগুড়ি শহর ও মহকুমা পরিচয়-- অশোক গঙ্গোপাধ্যায়।
৩. পুরবার্তা (নবপর্যায় স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ২০২১) শিলিগুড়ি পুরনিগম।
বিশেষ কৃতজ্ঞতা : ড. রতন বিশ্বাস, অনিমেষ বসু।
Have an account?
Login with your personal info to keep reading premium contents
You don't have an account?
Enter your personal details and start your reading journey with us
Design & Developed by: WikiIND
Maintained by: Ekhon Dooars Team