




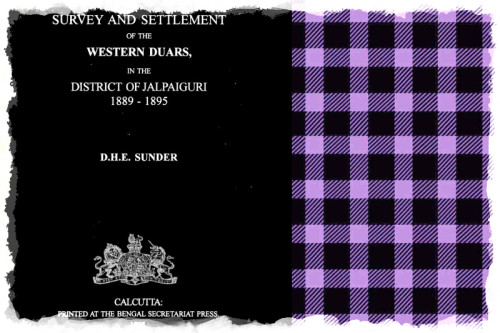
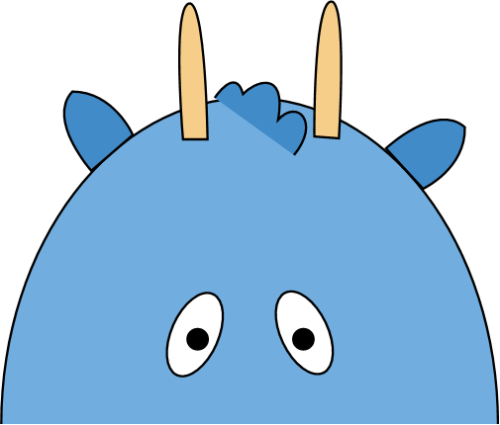





 а¶Єа¶ђаІНа¶ѓа¶Єа¶Ња¶ЪаІА බටаІНට
а¶Єа¶ђаІНа¶ѓа¶Єа¶Ња¶ЪаІА බටаІНට

බаІЗа¶ђаІА а¶Єа¶ња¶Ва¶є ඐථаІНබග а¶єа¶≤аІЗа¶У ඐගබаІНа¶∞аІЛа¶є а¶ХගථаІНටаІБ ඙аІНа¶∞පඁගට а¶є’а¶≤ а¶®а¶Ња•§ පаІБа¶∞аІБ а¶єа¶≤ а¶Ъа¶∞а¶Ѓ ඐගපаІГа¶ЩаІНа¶Ца¶≤а¶Ња•§ а¶ЕඐපаІЗа¶ЈаІЗ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ь а¶ЄаІИථаІНа¶ѓ а¶Па¶≤а•§ а¶Ыа¶≤ථඌа¶∞ а¶ЖපаІНа¶∞аІЯ ථගаІЯаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞а¶≤ ඐගබаІНа¶∞аІЛа¶єаІАබаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ а¶ѓаІБබаІНа¶Іа•§ а¶ђаІЛබඌ а¶У ඙ඌа¶Яа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶ЬබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Єа¶ЃаІБа¶Ца¶Єа¶Ѓа¶∞аІЗ ඐගබаІНа¶∞аІЛа¶єаІАа¶∞а¶Њ ඙ගа¶ЫаІБ а¶єа¶Яа¶≤а•§ බඁථ а¶є’а¶≤ а¶ХаІГа¶Ја¶Х ඐගබаІНа¶∞аІЛа¶єа•§ а¶Па¶З ඐගබаІНа¶∞аІЛа¶єа¶ХаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Зටගයඌඪඐගබ а¶ХаІЛа¶ЃаІН඙ඌථගа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ ඙аІНа¶∞ඕඁ ඙аІНа¶∞ටගඐඌබ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Ъа¶ња¶єаІНථගට а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ ඐගබаІНа¶∞аІЛа¶єаІАа¶∞а¶Њ ඙а¶∞а¶Ња¶ЄаІНට а¶єа¶≤аІЗа¶У а¶Па¶З а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථ а¶ђа¶ња¶Ђа¶≤аІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа¶®а¶ња•§ а¶Па¶З а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථаІЗа¶∞ а¶Ђа¶≤аІЗ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ЄаІНа¶ђаІЗа¶∞ а¶єа¶Ња¶∞ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Ха¶ЃаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ а¶ХаІЛа¶ЃаІН඙ඌථග ථගа¶ЬаІЗа¶З а¶Ьа¶Ѓа¶њ ථගа¶∞аІНа¶Іа¶Ња¶∞а¶£, а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ЄаІНа¶ђаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ѓа¶Ња¶£ ථගа¶∞аІНа¶£аІЯ, а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ЄаІНа¶ђ а¶ЖබඌаІЯаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞а¶≤а•§ а¶Ьඁගබඌа¶∞බаІЗа¶∞ බаІЗаІЯ а¶Ьа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶Ѓа¶Ња¶£ а¶Ха¶Ѓа¶њаІЯаІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶є’а¶≤а•§ а¶Жа¶ЗථපаІГа¶ЩаІНа¶Ца¶≤а¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ а¶ХаІЛа¶ЃаІН඙ඌථග а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ђаІЗපග බඌаІЯගටаІНа¶ђ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞а¶≤а•§ а¶За¶ЈаІНа¶Я а¶ЗථаІНа¶°а¶њаІЯа¶Њ а¶ХаІЛа¶ЃаІН඙ඌථග а¶За¶Ьа¶Ња¶∞ඌබඌа¶∞аІА а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌа¶∞ а¶Еඐඪඌථ а¶Па¶ђа¶В බаІЗа¶ђаІА а¶Єа¶ња¶Ва¶є а¶У ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЕථаІБа¶Ъа¶∞බаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Хඁගපථ а¶Чආථ а¶Ха¶∞аІЗа•§
а¶Па¶∞ ඙ඌපඌ඙ඌපග а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ђаІЬ а¶Ша¶Яථඌ а¶Ша¶ЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶ња¶∞ а¶ЗටගයඌඪаІЗа•§ а¶ХаІНඃඌ඙аІНа¶ЯаІЗථ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶ЯаІЗа¶∞ ථаІЗටаІГටаІНа¶ђаІЗ ඐගබаІНа¶∞аІЛа¶є බඁථаІЗа¶∞ ඙ඌපඌ඙ඌපග аІІаІ≠аІ≠аІ© а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶ђаІИа¶ХаІБථаІНආ඙аІБа¶∞ ඙аІБа¶∞аІЛ඙аІБа¶∞а¶њ а¶ХаІЛа¶ЃаІН඙ඌථගа¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞аІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Па¶∞ а¶Ђа¶≤аІЗ а¶∞а¶ЊаІЯа¶Хට а¶ђа¶Вප බаІНа¶ђа¶Ња¶∞а¶Њ පඌඪගට а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ а¶Ьඁගබඌа¶∞ගටаІЗ ඙а¶∞аІНඃඐඪගට а¶єаІЯа•§ а¶Па¶∞඙а¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶∞а¶ЊаІЯа¶Хට а¶ђа¶Вප ඙ඌа¶Хඌ඙ඌа¶Ха¶ња¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ а¶ђа¶Єа¶ђа¶Ња¶Є පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Па¶ђа¶В а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶ЄаІНටаІАа¶∞аІНа¶£ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶ња¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Њ а¶ђа¶≤аІЗа¶З ඙а¶∞а¶ња¶Ъගට а¶є’ටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа¶®а•§ аІІаІЃаІђаІѓ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶њ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЄаІНඐටථаІНටаІНа¶∞ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Њ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ ඙аІНа¶∞පඌඪථගа¶Х а¶Ха¶Ња¶Ь පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа•§
а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶ња¶∞ а¶≤аІЛа¶Ха¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග
а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶Ъа¶∞аІНа¶Ъа¶ЊаІЯ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶њ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථа¶Ха¶Ња¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶Єа¶ЃаІГබаІНа¶Іа•§ а¶Пටබа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ЬаІАඐථ а¶Іа¶Ња¶∞а¶ЊаІЯ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ ඙аІВа¶Ьа¶Њ-඙බаІН඲ටග а¶Єа¶є а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞-а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථ а¶ЬаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ХаІГටගа¶Х, а¶Еටග඙аІНа¶∞а¶Ња¶ХаІГටගа¶Х, а¶Ха¶≤аІН඙ථඌ а¶У ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞ а¶∞аІВ඙ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටගට а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа•§ а¶Па¶Цඌථа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Еа¶∞а¶£аІНа¶ѓ, ඙ඌයඌаІЬ, ථබаІА а¶ЄаІЗ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є а¶У а¶Ха¶≤аІН඙ථඌа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞පаІНа¶∞аІЯ බගаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§
а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶Ч а¶Єа¶є а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶ња¶∞ а¶Жа¶∞а¶У а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඐගපаІЗඣටаІНа¶ђ а¶є’а¶≤ а¶Па¶З а¶ђа¶ња¶ЄаІНටаІАа¶∞аІНа¶£ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ а¶Жа¶ђа¶єа¶Ња¶УаІЯа¶Ња•§ а¶Па¶Цඌථа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЛටаІБ-а¶ђаІИа¶ЪගටаІНа¶∞ а¶У ටඌа¶∞ а¶Й඙а¶≤а¶ђаІНа¶Іа¶њ ඁථа¶ХаІЗ а¶Йа¶∞аІНа¶ђа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶ЄаІГа¶ЬථපаІАа¶≤ а¶≠ඌඐථඌ а¶ЛබаІНа¶І а¶Ха¶∞аІЗа•§ ටඐаІЗ а¶Зබඌථගа¶Ва¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථ а¶Ша¶ЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЫаІЯа¶Яа¶њ а¶ЛටаІБа¶З ඙а¶∞а¶ња¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ђаІЛа¶Эа¶Њ а¶ѓаІЗа¶§а•§ а¶Па¶Цථ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ ටගථа¶Яа¶њ а¶ЛටаІБа¶∞ а¶Ж඲ග඙ටаІНа¶ѓа•§ а¶ЧаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Ѓ-а¶ђа¶∞аІНа¶Ја¶Њ-පаІАа¶§а•§ а¶ђа¶Ња¶ХаІА а¶ЛටаІБа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Еа¶≤аІН඙ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЫаІБа¶БаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ЕටаІАට ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З ඙аІНа¶∞ටගа¶Яа¶њ а¶ЛටаІБа¶ХаІЗ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ а¶Х’а¶∞аІЗ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞-а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථ ඙ඌа¶≤ගට а¶єаІЯаІЗ а¶Жа¶Єа¶ЫаІЗ а¶Па¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа•§ а¶Па¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶У а¶Еа¶ђа¶Єа¶∞ ඐගථаІЛබථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶П а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ ඁඌථаІБа¶Ј а¶ЄаІГа¶Ьථ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗථ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАට, ථаІГටаІНа¶ѓ а¶У ථඌа¶ЯаІНа¶ѓа•§ ටගඪаІНටඌ-а¶Ха¶Ња¶≤а¶ЬඌථаІА-а¶°а¶ња¶Ѓа¶Њ-а¶ЃаІВа¶∞аІНටаІНටග-а¶∞а¶ЊаІЯа¶°а¶Ња¶Х-а¶Ьа¶≤ඥඌа¶Ха¶Њ а¶Єа¶є а¶Еа¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓ а¶ЫаІЛа¶Я-а¶ђаІЬ ථබаІА а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬගටаІЗ а¶ђаІЯаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗа¶ЫаІЗа•§ ථබаІАа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶ђаІБа¶ХаІЗ а¶Х’а¶∞аІЗ а¶ђаІЯаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗ ඙а¶≤а¶ња•§ ටඌа¶З а¶ЄаІЗ ඙а¶≤ගටаІЗ а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶Ьа¶Ѓа¶њ а¶Йа¶∞аІНа¶ђа¶∞ а¶єаІЯаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶У а¶єаІЯ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶ЬථаІАаІЯ ඙а¶∞ගඁඌථаІЗа•§ ටඌа¶З а¶Єа¶єа¶Ь а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶Ха¶Ња¶Ь а¶Еа¶ђа¶Єа¶∞ බаІЗаІЯ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Па¶Цඌථа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶ЬаІАа¶ђа¶њ ඁඌථаІБа¶Ја¶ХаІЗа•§ ටඌа¶З а¶ЧаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Ѓ-а¶ђа¶∞аІНа¶Ја¶Њ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Є а¶Ъа¶Ња¶∞аІЗа¶ХаІЗа¶∞ а¶єа¶ЊаІЬа¶≠а¶Ња¶Ща¶Њ а¶Ца¶Ња¶ЯаІБථගа¶∞ ඙а¶∞ а¶ЃаІЗа¶≤аІЗ а¶Еа¶ђа¶Єа¶∞а•§ ටаІИа¶∞а¶њ а¶єаІЯ а¶Чඌථ, ථඌа¶ЯаІНа¶ѓа•§ а¶П а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶ЬаІАа¶ђа¶њ ඁඌථаІБа¶Ј පගа¶≤аІН඙ а¶ЄаІГа¶ЬථаІЗа¶У බа¶∞а•§ ටаІИа¶∞а¶њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЙථаІНථට а¶У а¶Жа¶Ха¶∞аІНа¶Ја¶£аІАаІЯ ථඌа¶ЯаІНඃපаІИа¶≤аІАа•§ ථඌа¶ЯаІНа¶ѓ а¶ЃаІВа¶≤ට බаІБ’а¶Іа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞а•§ а¶ЖථаІБа¶ЈаІНආඌථගа¶Х а¶У а¶Еа¶ђа¶Єа¶∞ ඐගථаІЛබථඁаІВа¶≤а¶Ха•§
а¶ЖථаІБа¶ЈаІНආඌථගа¶Х ඙ඌа¶≤а¶Њ а¶ЧаІЬаІЗ а¶ЙආаІЗа¶ЫаІЗ а¶≠аІЯ-а¶≠а¶ХаІНටග-ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є ඕаІЗа¶ХаІЗа•§ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටග-а¶Єа¶ЮаІНа¶Ьඌට а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ බаІЗඐටඌа¶∞ ඙аІНа¶∞ටග ථගඐаІЗබථаІЗа¶∞ а¶ЙබаІНබаІЗපаІЗ а¶∞а¶Ъගට а¶єаІЯ а¶ЧаІАට-ථаІГටаІНа¶ѓ-ථඌа¶ЯаІНа¶ѓа•§ ටඌටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ බаІЗඐටඌа¶∞ ඁඌයඌටаІНа¶ЃаІНа¶ѓ а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶®а¶Њ а¶У බаІЗඐටඌа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶Ња¶∞а•§ а¶Па¶Єа¶ђ а¶ЙаІОа¶Єа¶Ња¶∞ගට а¶єаІЯ පගа¶≤аІН඙аІАа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£ ඕаІЗа¶ХаІЗа•§ а¶ПටаІЗ а¶ХаІГටаІНа¶∞ගඁටඌ ථаІЗа¶За•§ а¶Ѓа¶єаІО а¶єа¶≤аІЗа¶У а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІАа¶£ а¶≤аІЛа¶Ха¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗ а¶Па¶За¶Єа¶ђ බаІЗඐබаІЗа¶ђаІА а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа¶∞ а¶У а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶Ха•§ ටඌа¶З ටඌබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටග а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞а¶У а¶Єа¶Ва¶Єа¶Ња¶∞аІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶ЖටаІНа¶ЃаІАаІЯ-а¶ЄаІНа¶ђа¶ЬථаІЗа¶∞ ඁටа¶За•§ ථගඐаІЗබථаІЗа¶∞ а¶ђа¶ХаІНටඐаІНа¶ѓа¶У а¶Па¶ХаІЗа¶ђа¶Ња¶∞аІЗ а¶Ша¶∞аІЛаІЯа¶Ња•§ а¶Ха¶Цථа¶У а¶Пඁථ පඐаІНබа¶У а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єаІГට а¶єаІЯ а¶ѓа¶Њ ටඕඌа¶Хඕගට а¶≠බаІНа¶∞а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗ а¶ђаІНа¶∞ඌටаІНа¶ѓа•§
а¶Пටබа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ а¶≤аІЛа¶Ха¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶ЃаІВа¶≤ට а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶Єа¶ЃаІН඙аІНа¶∞බඌаІЯа•§ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ЬаІАඐථ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶ЃаІВа¶≤ а¶Й඙ඌаІЯ а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶Ха¶Ња¶Ьа•§ а¶Жа¶ЧаІЗа¶З а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ЬаІЗථаІЗа¶Ыа¶њ а¶Па¶Цඌථа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЧаІАට-ථаІГටаІНа¶ѓ-ථඌа¶ЯаІНа¶ѓ බаІБ’а¶Іа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞а•§ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞ а¶≠ගටаІНටගа¶Х а¶ђа¶Њ а¶ЖථаІБа¶ЈаІНආඌථගа¶Х а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓ а¶є’а¶≤ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶Њ, а¶ЪаІЛа¶∞-а¶ЪаІБа¶∞ථаІАа•§ ථаІГටаІНа¶ѓ а¶У а¶ЧаІАට а¶є’а¶≤ а¶ЃаІЗа¶ЪаІЗථаІА, а¶Ча¶ЃаІАа¶∞а¶Њ а¶ЗටаІНа¶ѓа¶Ња¶¶а¶ња•§ а¶Еа¶ђа¶Єа¶∞ ඐගථаІЛබථඁаІВа¶≤а¶Х а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Єа¶∞аІНа¶ђа¶Ња¶Іа¶ња¶Х ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶є’а¶≤ ඙ඌа¶≤а¶Ња¶Яа¶њаІЯа¶Ња•§ а¶Па¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶У а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Іа¶Ња¶Ѓа¶Ча¶Ња¶®а•§
а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ
а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ ඙ඌа¶≤а¶Њ а¶ЃаІВа¶≤ට а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞, а¶Жа¶≤ග඙аІБа¶∞බаІБаІЯа¶Ња¶∞, а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶њ, а¶ЙටаІНටа¶∞ а¶У බа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£ බගථඌа¶Ь඙аІБа¶∞ а¶ЬаІЗа¶≤а¶ЊаІЯ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤а¶ња¶§а•§ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶Њ, а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ, а¶Хඌථග-а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ а¶ЗටаІНඃඌබග а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ ථඌඁаІЗ ඙аІВа¶Ьа¶Њ ඙ඌථ බаІЗа¶ђаІА а¶Ѓа¶®а¶Єа¶Ња•§ බගථඌа¶Ь඙аІБа¶∞аІЗ а¶Па¶З а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථ а¶Й඙а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІЗ ‘а¶ђ-а¶ЦаІЗа¶≤а¶Њ’ а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶Ьථ඙аІНа¶∞а¶њаІЯа•§ а¶Па¶∞ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶ЬථаІАаІЯටඌ ඐගපаІЗа¶Ј а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНа¶ђ ඐයථ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶Њ а¶є’а¶≤ ඙බаІНඁ඙аІБа¶∞а¶Ња¶£ ඙аІНа¶∞а¶≠ඌඐගට ඁථඪඌа¶∞ а¶Ча¶Ња¶®а•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ඁථඪඌඁа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ а¶ђа¶ЩаІНа¶Ча¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗ а¶ђа¶єаІБа¶≤ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶Ња¶∞ගට а¶У а¶Ьථ඙аІНа¶∞а¶њаІЯа•§ බаІЗа¶ђаІА ඁථඪඌа¶∞ ඁඌයඌටаІНа¶ЃаІНа¶ѓ а¶У ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ а¶Ча¶Ња¶УаІЯа¶Њ-а¶Еа¶≠ගථаІЯ а¶єаІЯ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ а¶Ча¶Ња¶®а•§ а¶ЖථаІБඁඌථගа¶Х а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶ЯаІАаІЯ ටаІНа¶∞аІЯаІЛබප පටа¶Х ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Еа¶ЈаІНа¶Яඌබප පටа¶ХаІЗа¶∞ а¶ХаІЛථа¶У а¶Па¶Х а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Єа¶Ва¶Ха¶≤а¶ња¶§а•§ а¶Єа¶∞аІН඙බаІЗа¶ђаІА ඁථඪඌа¶∞ а¶Па¶З а¶Чඌථа¶ХаІЗ ඙බаІНඁ඙аІБа¶∞а¶Ња¶£ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єаІЯ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ ඁථඪඌа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ථඌඁ ඙බаІНа¶Ѓа¶Ња•§ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ ඁටа¶≠аІЗබ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗ ඙බаІНа¶Ѓа¶Њ а¶ЖබටаІЗ ඁථඪඌа¶∞ а¶¶а¶ња¶¶а¶ња•§
ඁථඪඌ ථඌඁаІЗа¶∞ а¶ХаІЛථа¶У බаІЗа¶ђаІАа¶∞ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ц а¶ђаІЗබ, ඙аІБа¶∞а¶Ња¶£, а¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ЊаІЯа¶£, а¶Ѓа¶єа¶Ња¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶ѓаІЗ ඙බаІНඁ඙аІБа¶∞а¶Ња¶£аІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ц а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶њ ටඌ ටаІЛ а¶Й඙඙аІБа¶∞а¶Ња¶£а•§ ඙аІБа¶∞а¶Ња¶£ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶∞а¶Ъථඌ а¶Х’а¶∞аІЗ а¶ЃаІВа¶≤ ඙аІБа¶∞а¶Ња¶£аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЬаІБаІЬаІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ පඌඪаІНටаІНа¶∞ а¶ЕථаІБаІНа¶ѓа¶ЊаІЯаІА а¶Єа¶∞аІН඙аІЗа¶∞ බаІЗඐටඌ ථඌа¶Ча•§ ඁථඪඌ а¶≤аІЛа¶ХබаІЗа¶ђаІАа•§ ඁථඪඌඁа¶ЩаІНа¶Ча¶≤аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ща¶Ња¶≤аІА а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗ ඁථඪඌබаІЗа¶ђаІАа¶∞ ඙аІБа¶ЬаІЛ පаІБа¶∞аІБ а¶єаІЯа•§ ඁථඪඌ බаІЗа¶ђаІАа¶З а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞, а¶Жа¶≤ග඙аІБа¶∞බаІБаІЯа¶Ња¶∞, а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶њ а¶Єа¶є а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ђаІЗප а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ а¶ђа¶Њ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶Њ ථඌඁаІЗ ඙аІБа¶Ьගට а¶єа¶®а•§ ටගථග а¶Хඌථග а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ ථඌඁаІЗа¶У ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶ња¶§а•§
а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ ඙ඌа¶≤а¶ЊаІЯ а¶Ѓа¶∞аІНටаІЗ බаІЗа¶ђаІА඙аІВа¶Ьа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Хඌයගථග ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯ а¶Чඌථ а¶У а¶Еа¶≠ගථаІЯаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗа•§ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶ња¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗ а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНඕаІЗа¶∞ а¶ХаІЛථа¶У а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶∞а¶ЃаІНа¶≠аІЗ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ ඙аІВа¶Ьа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶Па¶З ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ЖඐපаІНа¶ѓа¶ња¶Х а¶ђа¶ња¶ЈаІЯ а¶Ча¶Ња¶®а•§ а¶ђа¶ња¶ђа¶Ња¶є, а¶ЕථаІНථ඙аІНа¶∞ඌපථ, а¶ЧаІГය඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶ЗටаІНඃඌබග а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗа¶∞ පаІБа¶≠ а¶ЄаІВа¶ЪථඌаІЯ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНа¶•а•§ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђаІЗа¶З а¶Жа¶≤аІЛа¶ЪථඌаІЯ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶њ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ЃаІВа¶≤ а¶Й඙а¶Ъа¶Ња¶∞ ටඌа¶∞ а¶Ча¶Ња¶®а•§ а¶Жа¶∞ ඃබග а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНඕаІЗа¶∞ ඁඌථඪගа¶Х ඕඌа¶ХаІЗ ටඐаІЗ ඙ඌа¶≤а¶Ња¶∞ (ථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶∞аІВ඙) а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶ѓаІЗ а¶Чඌථ ටඌ а¶Ѓа¶Ња¶≤බයаІЗа¶∞ а¶Ха¶ђа¶њ а¶Ьа¶Ча¶ЬаІНа¶ЬаІАඐථ а¶ШаІЛа¶Ја¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶∞а¶Ъථඌ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Єа¶Ва¶ЧаІГа¶єа¶ња¶§а•§ ටඐаІЗ а¶ЕඐපаІНа¶ѓа¶З а¶ЄаІНඕඌථ а¶ђаІНඃටගа¶∞аІЗа¶ХаІЗ ටඌа¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Єа¶Ва¶ѓаІЛа¶Ьථ а¶Ша¶ЯаІЗа•§ ටඌ а¶ЄаІНඕඌථаІАаІЯ ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђаІЗа•§ ඐථаІНබථඌ, බаІЗа¶ђаІА ඁථඪඌа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ, ඁඌයඌටаІНа¶ЃаІНа¶ѓ, а¶Ѓа¶∞аІНටаІЗ ඙аІВа¶Ьа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ථ а¶У а¶≠ඌඪඌථ—а¶Па¶За¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶З ඐගථаІНа¶ѓа¶ЄаІНට а¶Чඌථ а¶У ඙ඌа¶≤а¶Ња•§ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗ බаІБ’඙аІНа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ථ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ ‘а¶Хඌථග а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ’ а¶ЕථаІНа¶ѓа¶Ьථ ‘а¶ЧаІАටඌа¶≤а¶њ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ’а•§ а¶Хඌථග а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶ња¶З а¶ђа¶єаІБа¶≤ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤а¶ња¶§а•§ а¶П ඙аІНа¶∞а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ පаІНа¶∞බаІНа¶ІаІЗаІЯ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶Х පаІНа¶∞аІА а¶Ъа¶Ња¶∞аІБа¶ЪථаІНබаІНа¶∞ а¶ЄаІНඃඌථаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ђа¶ња¶ЦаІНඃඌට а¶ђа¶З ‘а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА’а¶Є а¶Еа¶Ђ ථа¶∞аІНඕඐаІЗа¶ЩаІНа¶Ча¶≤’—а¶П а¶≤а¶ња¶ЦаІЗа¶ЫаІЗථ-- In all ceremonies related to Marriage, Sradh, Pregnancy and Child Birth worship is offered to Bishohori Thakurani in the outer yard of the house with curd, flattened rice and ripe plantain as offering. There are two types of Bishohori. One is Kani-Bishohori which is more commonly worshiped. The other is Gitali Bishohori. She is worshiped during the Marriage ceremony. The image consists of Beulani (Behula), Bala (Lacckhindar), Goda, Godani, Washer Woman, Siva, Fish, Snakes etc.
а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНඕаІЗа¶∞ ඁඌථඪගа¶Х а¶ЕථаІБа¶Єа¶Ња¶∞аІЗ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶ѓаІЗа¶ХаІЛථа¶У а¶Єа¶ЃаІЯ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ ඙ඌа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ ටඐаІЗ පаІНа¶∞а¶Ња¶ђа¶£ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗ а¶Па¶З ඙ඌа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථ ටаІБа¶≤ථඌаІЯ а¶ђаІЗපග а¶єаІЯаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ ඙ඌа¶≤а¶Њ ටගථබගථ, ඪඌටබගථ, а¶Па¶Ча¶Ња¶∞аІЛබගථ а¶Іа¶∞аІЗ а¶Ъа¶≤аІЗа•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ පаІНа¶∞ඌඐථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Ѓа¶Ња¶Є а¶ЬаІБаІЬаІЗ а¶Па¶З а¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Па¶З а¶Йබඌයа¶∞а¶£а¶У а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ ඙аІНа¶∞ටගබගථ а¶∞ඌට а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶Ча¶≠аІАа¶∞ а¶є’а¶≤аІЗ а¶Па¶З ඙ඌа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Жа¶∞а¶ЃаІНа¶≠ а¶єаІЯ а¶Ъа¶≤аІЗ ඙а¶∞аІЗа¶∞බගථ а¶ЄаІВа¶∞аІНа¶ѓаІЛබаІЯ ඙а¶∞аІНඃථаІНа¶§а•§ ඐථаІНබථඌ බගаІЯаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Х’а¶∞аІЗ а¶≠ඌඪඌථ ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Па¶З ඙ඌа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Чඌථ а¶У а¶Еа¶≠ගථаІЯа•§ බගථඌа¶Ь඙аІБа¶∞аІЗ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ ඁඌථඪගа¶Х ථඌ ඕඌа¶Ха¶≤аІЗ а¶Па¶З а¶Чඌථ а¶Ча¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶єаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶ХаІЗа¶ђа¶≤ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථ а¶єаІЯа•§ ටඌа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ‘а¶ђ-а¶ЦаІЗа¶≤а¶Њ’а•§
а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Жа¶Єа¶∞аІЗ а¶Чඌථ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНඕаІЗа¶∞ ඁඌථඪගа¶Х ඕඌа¶Ха¶≤аІЗ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ а¶Чඌථ ඙ඌа¶≤а¶Њ а¶ђа¶Њ ථඌа¶ЯаІНа¶ѓаІЗа¶∞ ඁට а¶Х’а¶∞аІЗ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ ඙ඌа¶≤а¶ЊаІЯ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶ЃаІВа¶≤ ‘а¶ЧаІАබඌа¶≤’ (а¶Ча¶ЊаІЯа¶Х) ඕඌа¶ХаІЗа¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ѓ-а¶єа¶ЄаІНටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ а¶Ъа¶Ња¶Ѓа¶∞а•§ а¶Ъа¶Ња¶Ѓа¶∞ ටаІИа¶∞а¶њ а¶єаІЯ а¶Ъа¶Ѓа¶∞а¶њ а¶Ча¶Ња¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ЪаІБа¶≤ බගаІЯаІЗа•§ ටඐаІЗ а¶Жа¶Ьа¶ХаІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶°а¶ња¶Ьа¶ња¶Яа¶Ња¶≤ а¶ѓаІБа¶ЧаІЗ а¶Па¶З а¶Ъа¶Ња¶Ѓа¶∞ ටаІИа¶∞а¶њ а¶єаІЯ а¶ХаІГටаІНа¶∞а¶ња¶Ѓ а¶≤а¶Ња¶За¶≤ථаІЗа¶∞ а¶ЄаІБටаІЛ බගаІЯаІЗа•§ බаІЗа¶ЦටаІЗ а¶ЃаІВа¶≤ а¶Ъа¶Ња¶Ѓа¶∞аІЗа¶∞ ඁටа¶З, යඌටаІЗ ථගа¶≤аІЗ а¶ђаІЛа¶Эа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ ඙ඌа¶∞аІНඕа¶ХаІНа¶ѓа•§ а¶≤аІЗа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ЪаІБа¶≤ а¶ђа¶Ња¶Ба¶Іа¶Њ ඕඌа¶ХаІЗ а¶ХඌආаІЗа¶∞ බථаІНа¶° а¶ђа¶Њ а¶∞аІБ඙аІЛа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ЯаІЗа•§ а¶Па¶З а¶Ъа¶Ња¶Ѓа¶∞аІЗа¶∞ ඐඌටඌඪ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Ха¶≤аІНඃඌථа¶Ха¶∞ а¶ђа¶≤аІЗ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶ЃаІВа¶≤ а¶ЧаІАබඌа¶≤аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАа¶∞аІВ඙аІЗ ඕඌа¶ХаІЗථ а¶Па¶Ха¶Ьථ බаІЛаІЯа¶Ња¶∞аІАа•§ а¶Зථග а¶ЃаІВа¶≤ а¶ЧаІАබඌа¶≤а¶ХаІЗ а¶Єа¶Ња¶єа¶Ња¶ѓаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞аІЗථ ඙ඌа¶≤а¶Ња¶ХаІЗ а¶Па¶Ча¶њаІЯаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗа•§ а¶Па¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶У ඕඌа¶ХаІЗථ а¶Жа¶∞а¶У ඪටаІЗа¶∞ а¶Жආඌа¶∞аІЛа¶Ьථ පගа¶≤аІН඙аІАа•§ а¶ѓа¶Ња¶Ба¶∞а¶Њ а¶Еа¶≠ගථаІЯ а¶Ха¶∞аІЗථ, ඐඌබаІНඃඃථаІНටаІНа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ьඌථ а¶У а¶Чඌථ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶∞а¶Ња¶З а¶ЃаІЗаІЯаІЗබаІЗа¶∞ а¶Ъа¶∞ගටаІНа¶∞аІЗ а¶Еа¶≠ගථаІЯ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єаІЯ ‘а¶ЫаІЛа¶Ха¶∞а¶Њ’ а¶ђа¶Њ ‘а¶ЫаІБа¶Ха¶∞аІА’а•§ а¶Па¶Цථ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Њ පගа¶≤аІН඙аІА а¶Еа¶Вපа¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§
පаІБа¶∞аІБටаІЗа¶З ඕඌа¶ХаІЗ ‘а¶Ѓа¶ња¶Йа¶Ьа¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ а¶Хථඪඌа¶∞аІНа¶Я’а•§ ටඌа¶∞඙а¶∞ а¶ЫаІЛа¶Ха¶∞а¶Њ а¶ђа¶Њ а¶ЫаІБа¶Ха¶∞аІАබаІЗа¶∞ ථаІГටаІНа¶ѓ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯ ඐඌබаІНඃඃථаІНටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Жа¶ђа¶єаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ බаІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶њ ඙ඌа¶≤а¶ЊаІЯ а¶ѓаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶∞а¶ЃаІНа¶≠а¶ња¶Х а¶ЫаІБа¶Ха¶∞аІА-ථаІГටаІНа¶ѓ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯ ටඌ а¶ѓаІМථ а¶Жа¶ђаІЗබථ ඙аІВа¶∞аІНа¶£а•§ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶Вප а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓаІЗа¶З а¶Жබගа¶∞а¶ЄаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶ЦаІБа¶ђ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶Жа¶∞ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗබаІЗа¶∞ බаІНа¶ђа¶Ња¶∞а¶Њ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපගට ථаІГටаІНа¶ѓа¶У а¶ѓаІЗ а¶Хටа¶Яа¶Њ а¶ѓаІМථ а¶Жа¶ђаІЗබථ ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶є’ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ ටඌ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ъа¶ХаІНа¶ЈаІЗ ථඌ ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓа¶ХаІНа¶Ј а¶Ха¶∞а¶≤аІЗ а¶ђаІЛа¶Эа¶Ња¶З а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ ඙ඌа¶≤ඌටаІЗа¶У а¶Па¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЩаІНа¶Ча¶ња¶Х а¶Еа¶≠ගථаІЯаІЗ ඃඕаІЗа¶ЈаІНа¶Яа•§ ඪඌ඙а¶ХаІЗ а¶ѓаІМථටඌа¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІАа¶Х а¶∞аІВ඙аІЗ ථගඣаІНආඌ а¶Єа¶єа¶Ха¶Ња¶∞аІЗ ඙аІВа¶Ьа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯ ඙аІГඕගඐаІАа¶∞ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа•§ а¶ѓаІМථ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠аІЛа¶Ча¶∞ට බаІБа¶Яа¶њ ඪඌ඙аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶≤а¶Ња¶≤ පඌа¶≤аІБа¶Хඌ඙аІЬ ඙аІЗටаІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ђаІЗප ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАа¶®а•§
а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶њ а¶Єа¶є а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Па¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ХаІГටගа¶Х ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗа¶ґа•§ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶ЄаІНටаІАа¶∞аІНа¶£ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ ථබаІА а¶ђа¶ња¶ІаІМට, а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶БටඪаІНа¶ѓа¶Ња¶БටаІЗ а¶Ьа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶Ња¶ХаІАа¶∞аІНа¶£а•§ а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО а¶Єа¶∞аІН඙-а¶ђа¶Єа¶ђа¶Ња¶Є-а¶Й඙ඃаІЛа¶ЧаІАа•§ ටඌа¶З а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ ඙аІНа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ ඪඌ඙аІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Є а¶Па¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа•§ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ටаІЛ а¶ХаІЗа¶Й а¶ХаІЗа¶Й а¶ЦаІБа¶ђ а¶ђа¶ња¶Ја¶Ња¶ХаІНа¶§а•§ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІБа¶∞аІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶Єа¶∞аІН඙-බа¶ВපථаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х ඁඌථаІБа¶Ј а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶®а•§ а¶Ъа¶ња¶Ха¶њаІОа¶Єа¶Њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌа¶∞ а¶ЙථаІНථටගа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБа¶∞ а¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶ЃаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Ха•§ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђаІЗ а¶Уа¶Эа¶Ња¶∞ යඌටаІЗ а¶≠аІБа¶≤ а¶Ъа¶ња¶Ха¶њаІОа¶Єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶Хට а¶ѓаІЗ ඁඌථаІБа¶Ј ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£ а¶єа¶Ња¶∞а¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ ටඌа¶∞ а¶ЗаІЯටаІНටඌ ථаІЗа¶За•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඁථаІЗ ඪඌ඙ а¶ЕබаІНа¶≠аІБට а¶Па¶Х ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£аІАа•§ ටඌа¶∞ ඙ඌ ථаІЗа¶За•§ а¶Ьа¶ња¶≠ а¶ЪаІЗа¶∞а¶Ња•§ ඥаІЗа¶≤аІЗ බаІЗаІЯ а¶ђа¶ња¶Ја•§ ටඌа¶З ඪඌ඙ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶≠аІЯа•§ а¶≠аІЯ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶≠а¶ХаІНа¶§а¶ња•§ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ ඙аІВа¶Ьа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£а•§
а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ ඙ඌа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Хඌයගථග а¶Єа¶Ва¶ХаІНа¶ЈаІЗ඙аІЗ а¶Па¶За¶∞аІВ඙– ඁථඪඌ а¶ЪаІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Ѓа¶∞аІНටаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ ඙аІВа¶Ьа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤а¶®а•§ а¶Жа¶∞ ටඌа¶З ටගථග а¶ђаІЗа¶ЫаІЗ ථගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Еа¶≠а¶ња¶Ьඌට а¶ђа¶£а¶ња¶Х а¶Ъа¶Ња¶Бබ ඪබඌа¶Ча¶∞а¶ХаІЗа•§ а¶Ъа¶Ња¶Бබ ඪබඌа¶Ча¶∞ පගඐаІЗа¶∞ а¶≠а¶ХаІНа¶§а•§ ටඌа¶З ටගථග а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Њ බаІЗඐටඌ ඁථඪඌа¶ХаІЗ а¶ШаІГа¶£а¶Ња¶≠а¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓа¶ЦаІНඃඌථ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Жа¶∞ ටඌටаІЗ а¶ХаІЛ඙аІЗ ඙аІЬа¶≤аІЗථ а¶Па¶Ха¶Ъа¶ХаІНа¶ЈаІБ ඁථඪඌа¶∞а•§ а¶ђа¶Ња¶£а¶ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ ඪ඙аІНටධගа¶Ща¶Њ а¶Єа¶Ња¶Ча¶∞аІЗ а¶°аІБа¶ђаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ЧаІЗа¶Х а¶ЫаІЯ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа•§ а¶Єа¶∞аІНа¶ђа¶ХථගඣаІНආ ඙аІБටаІНа¶∞ а¶≤а¶ЦගථаІНබа¶∞ ඁථඪඌа¶∞ а¶Ыа¶≤ථඌаІЯ а¶ђа¶Ња¶Єа¶∞а¶Ша¶∞аІЗ а¶Єа¶∞аІН඙ බа¶ВපථаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ ඪබаІНа¶ѓа¶ЃаІГට а¶≤а¶ЦගථаІНබа¶∞аІЗа¶∞ ඪබаІНа¶ѓ а¶ђа¶ња¶Іа¶ђа¶Њ а¶ЄаІНටаІНа¶∞аІА а¶ЃаІГට а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЃаІАа¶∞ පඐබаІЗа¶є ථගаІЯаІЗ а¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІНа¶ЧаІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ ඃඌටаІНа¶∞а¶Њ а¶Ха¶∞а¶≤а•§ а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЃаІАа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£ а¶Ђа¶ња¶∞а¶њаІЯаІЗ ථаІЗа¶УаІЯа¶Ња•§ ඃඌටаІНа¶∞ඌ඙ඕаІЗ ථඌථඌ ඙аІНа¶∞ටගа¶ХаІВа¶≤ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌа¶∞ а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶єа¶≤аІЗа¶У а¶ЕඐපаІЗа¶ЈаІЗ а¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІНа¶ЧаІЗа¶∞ බаІЗඐටඌබаІЗа¶∞ ඪථаІНටаІБа¶ЈаІНа¶Я а¶Ха¶∞аІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ ඪටаІАටаІНа¶ђаІЗа¶∞ а¶ЬаІЛа¶∞аІЗ а¶≤а¶ЦගථаІНබа¶∞а¶ХаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ба¶Ъа¶њаІЯаІЗ ටаІЛа¶≤аІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ ටඌа¶ХаІЗ а¶Хඕඌ බගටаІЗ а¶є’а¶≤ а¶Ѓа¶∞аІНටаІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶Ъа¶Ња¶Бබ ඪබඌа¶Ча¶∞а¶ХаІЗ බගаІЯаІЗ ඁථඪඌа¶∞ ඙аІВа¶Ьа¶Њ а¶Ха¶∞а¶њаІЯаІЗ ථаІЗа¶ђаІЗа•§
а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ъа¶Ња¶Бබ ඪබඌа¶Ча¶∞ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶Ха¶≤аІН඙аІЗ а¶Еа¶Яа¶≤а•§ ටගථග а¶ѓаІЗ යඌට බගаІЯаІЗ පගඐаІЗа¶∞ ඙аІВа¶Ьа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶ЄаІЗ යඌටаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБටаІЗа¶З ඁථඪඌа¶∞ ඙аІВа¶Ьа¶Њ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗථ а¶®а¶Ња•§ а¶Йа¶≤а¶ЯаІЗ ඁථඪඌа¶ХаІЗ а¶Ча¶Ња¶≤а¶Ња¶Ча¶Ња¶≤ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗථ а¶ХаІБа¶∞аІВ඙ඌ а¶ђа¶≤аІЗа•§ а¶ђа¶≤аІЗа¶ЫаІЗථ ‘а¶ЪаІНа¶ѓа¶Ња¶Ва¶ЃаІБаІЬа¶њ а¶Хඌථග’а•§ а¶ХаІЗථථඌ ඐගඁඌටඌ а¶ЪථаІНа¶°аІА-а¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඐගඐඌබаІЗ ඁථඪඌ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЪаІЛа¶Ц а¶єа¶Ња¶∞а¶Ња¶®а•§ а¶Жа¶∞ ටඌа¶Ба¶∞ ඁඌඕඌа¶Яа¶њ а¶ЪаІНа¶ѓа¶Ња¶Ща¶Ѓа¶Ња¶ЫаІЗа¶∞ ඁට а¶ђаІЬа•§
а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶ђа¶Ња¶ЄаІАа¶Ча¶£ а¶ЪаІНа¶ѓа¶Ња¶Ща¶Ѓа¶Ња¶Ы а¶ЪаІЗථаІЗа¶®а•§ а¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶Яа¶Њ а¶Ѓа¶Ња¶ЫаІЗа¶∞ ඁට බаІЗа¶ЦටаІЗ а¶Па¶∞ а¶≤аІЗа¶ЬаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඌථаІНට а¶≤а¶Ња¶≤а¶ЪаІЗ а¶єаІЯа•§ ඁඌඕඌа¶Яа¶њ පа¶∞аІАа¶∞аІЗа¶∞ ටаІБа¶≤ථඌаІЯ а¶ђаІЬ а¶єаІЯ а¶Жа¶∞ а¶ЦаІБа¶ђ а¶≤аІЛа¶≠аІА а¶єаІЯ а¶Па¶З а¶Ѓа¶Ња¶Ыа•§ а¶ЄаІБටа¶∞а¶Ња¶В а¶ЪаІНа¶ѓа¶Ња¶Ща¶ЃаІБаІЬа¶њ а¶Хඌථග а¶ђа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶ЦаІЗ඙аІЗ ඃඌථ а¶Ѓа¶®а¶Єа¶Ња•§ а¶ХаІНа¶∞аІЛа¶Іа¶ђа¶єаІНа¶£а¶ња¶§аІЗ ඙аІБаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤ටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶®а•§ а¶ХටබаІВа¶∞ а¶ѓаІЗ а¶Па¶З а¶Ша¶Яථඌ а¶ЧаІЬඌට а¶ХаІЗа¶Й а¶ЬඌථаІЗ ථඌ ඃබග ථඌ а¶ђаІЗа¶єаІБа¶≤а¶Њ а¶ЄаІЗ а¶ХаІНа¶∞аІЛа¶Іа¶ђа¶єаІНа¶£а¶ња¶§аІЗ පඌථаІНටගа¶∞ а¶ђа¶Ња¶∞а¶њ ථගа¶ХаІНа¶ЈаІЗ඙ а¶Ха¶∞а¶§а•§ а¶ђаІЗа¶єаІБа¶≤а¶Њ පаІНඐපаІБа¶∞а¶ХаІЗ а¶ђаІЛа¶Эа¶Ња¶≤аІЛа•§ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ХඌථаІНа¶°аІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶Ъа¶Ња¶Бබ ඪබඌа¶Ча¶∞ ඙аІЗа¶Ыථ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶ђа¶Ња¶Ѓа¶єа¶ЄаІНටаІЗ ඁථඪඌа¶∞ ඙аІВа¶Ьа¶Њ а¶Єа¶Ња¶∞а¶≤аІЗථ а¶ЂаІБа¶≤ බගаІЯаІЗа•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ බа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£ а¶єа¶ЄаІНටаІЗ а¶ЄаІЗ පගඐа¶ХаІЗ ඙аІВа¶Ьа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа•§ ඁථඪඌ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ ටඌටаІЗа¶З а¶ЦаІБа¶ґа¶ња•§ (а¶ХаІНа¶∞ඁප)
а¶Ыа¶ђа¶њ – а¶∞аІБа¶Ѓа¶Њ බටаІНට
Have an account?
Login with your personal info to keep reading premium contents
You don't have an account?
Enter your personal details and start your reading journey with us
Design & Developed by: WikiIND
Maintained by: Ekhon Dooars Team