











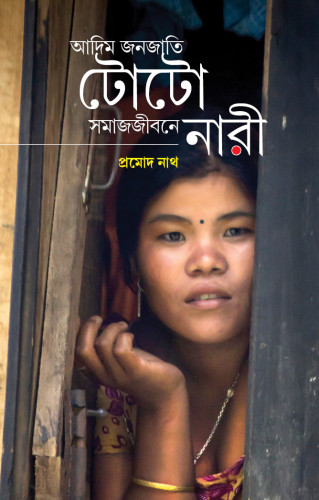



 а¶ЬඃඊබаІА඙ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞
а¶ЬඃඊබаІА඙ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞

а¶ђа¶ња¶Чට පටа¶ХаІЗа¶∞ පаІЗа¶Ј බපа¶Х ඕаІЗа¶ХаІЗ ඐගපаІНඐඌඃඊථ а¶ѓа¶Цථ а¶ЧаІБа¶Яа¶ња¶ЧаІБа¶Яа¶њ ඙ඌඃඊаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ බаІЗපаІЗ ඥаІБа¶ХටаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞а¶≤, а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤ а¶Ха¶≤аІЗа¶Ь ඙ධඊаІБа¶ѓа¶Ља¶Њ а¶ЄаІЗබගථаІЗа¶∞ а¶ХගපаІЛа¶∞, а¶ѓаІБа¶ђа¶∞а¶Њ ටඌа¶∞ а¶ЙටаІНටඌ඙ а¶ЯаІЗа¶∞ ඙ඌа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Ца¶ђа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ча¶ЬаІЗа¶∞ а¶єаІЗа¶°а¶≤а¶Ња¶ЗථаІЗа•§ а¶ЃаІЗа¶ЯаІНа¶∞аІЛ а¶ХаІНඃඌප а¶ПථаІНа¶° а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶њ ථගඃඊаІЗ ඐගටа¶∞аІНа¶Х а¶Ъа¶∞а¶ЃаІЗ а¶ЙආаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђа¶Ња¶Ѓ පඌඪа¶ХаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНබа¶∞ а¶Ѓа¶єа¶≤аІЗа¶Уа•§ а¶ЄаІЗа¶З ඐගටа¶∞аІНа¶Ха¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Яа¶Ња¶Яа¶Ха¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ ථඌ а¶ХаІЛථаІЛබගථа¶З, а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ ටа¶Цථ а¶ЯаІНа¶∞аІЗථ а¶ѓаІЛа¶Ча¶Ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶Пට а¶Е඙аІНа¶∞ටаІБа¶≤ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ѓаІЗ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Хඌපගට а¶Ца¶ђа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ча¶Ь а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ ඙аІМа¶Ба¶Ыට а¶Па¶Хබගථ ඙а¶∞аІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ЄаІЛа¶Ѓа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ха¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶Ца¶ђа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ча¶Ь ඙аІЬටаІЗ ඙аІЗටඌඁ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗа•§ ටඌа¶∞඙а¶∞ а¶Ча¶ЩаІНа¶Ча¶Њ බගඃඊаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Ьа¶≤ а¶ђа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ, а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ ඙ඌධඊඌඃඊ ඙ඌධඊඌඃඊ а¶Па¶Цථ а¶ђа¶єаІБа¶Ьඌටගа¶Х а¶Єа¶Ва¶ЄаІНඕඌа¶∞ а¶∞а¶ња¶ЯаІЗа¶≤ а¶Ха¶Ња¶ЙථаІНа¶Яа¶Ња¶∞ ඐගථඌ а¶ђа¶Ња¶Іа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ, а¶Па¶ђа¶В а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞ඌථаІНට බаІЗපаІЗа¶У а¶Ьа¶ња¶Уа¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶Я-а¶ЯаІНа¶∞аІЗථаІНа¶°а¶Є а¶Па¶Цථ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ ‘а¶ЯаІНа¶∞аІЗථаІНа¶°’ а¶єаІЯаІЗ බඌа¶БаІЬа¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§
а¶ЄаІЗа¶З ටа¶Цථ-а¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ђа¶Га¶ЄаІНа¶ђа¶≤ පයа¶∞аІЗ පයа¶∞аІЗ а¶ѓаІЗ බаІБа¶∞аІНа¶Чඌ඙аІВа¶Ьа¶Њ යට ටඌටаІЗ а¶≠аІАа¶Ја¶£ а¶Па¶Х а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІНඃටඌ а¶Жа¶∞ а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Ха¶ња¶Жථඌ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ХඌආаІЗа¶∞ а¶ЂаІНа¶∞аІЗа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶≤а¶Ња¶≠а¶≤а¶њ а¶Хඌ඙ධඊ а¶Жа¶≤඙ගථаІЗ а¶Па¶Ба¶ЯаІЗ а¶ЧаІЛа¶Яа¶Њ පයа¶∞аІЗ බаІБа¶Ъа¶Ња¶∞а¶Яа¶Њ а¶ђа¶°а¶Љ ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶£аІНධ඙ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞ට а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞ඪගබаІНа¶І а¶°аІЗа¶Ха¶∞аІЗа¶Яа¶∞а¶∞а¶Њ, а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ බගථයඌа¶Яа¶Њ පයа¶∞аІЗ а¶ѓаІЗඁථ ඙аІНа¶∞ඪගබаІНа¶І а¶Ыа¶ња¶≤ ‘а¶Ха¶Ња¶≤а¶Њ-а¶єаІБа¶ЯаІБ'а¶∞ а¶°аІЗа¶Ха¶∞аІЗа¶Яа¶∞’а•§ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Њ а¶Па¶ђа¶В а¶єаІБа¶ЯаІБ ථඌඁа¶Х а¶ЄаІЗа¶З බаІБа¶З ඐථаІНа¶ІаІБа¶∞ а¶ЬаІБа¶Яа¶њ, ඃඌබаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ ථඌඁ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ බඌබඌа¶∞а¶Њ а¶ХаІБа¶За¶ЬаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞පаІНථаІЗа¶∞ ඁට а¶Ьа¶ња¶ЬаІНа¶ЮаІЗа¶Є а¶Ха¶∞ට а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞, а¶ђа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶≤аІЗ බаІБа¶∞аІНа¶Чඌ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Ѓа¶£аІНධ඙аІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Ха¶Ња¶Ьа¶У а¶ЬаІБа¶ЯаІЗ а¶ѓаІЗа¶§а•§ а¶єаІНа¶ѓа¶Ња¶Б, ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶ЄаІЗа¶≤а¶ња¶Ѓ-а¶Ьа¶Ња¶≠аІЗබаІЗа¶∞ ඁටа¶З а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІБа¶∞аІНа¶£ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ЪගටаІНа¶∞ථඌа¶ЯаІНа¶ѓаІЗа•§ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶ЫаІЛа¶Я а¶ЫаІЛа¶Я а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ђаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶£аІНධ඙ ථගа¶∞аІНඁගට යට ඙ඌධඊඌа¶∞ පගа¶≤аІН඙аІАබаІЗа¶∞ ථගа¶∞аІНබаІЗа¶ґа¶®а¶Ња¶ѓа¶Ља•§ ඙ඌа¶Яа¶Хඌආග, ඙ඌа¶ЯаІЗа¶∞ а¶Жа¶Бප, а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь, а¶ђа¶Ња¶Бප а¶Па¶Єа¶ђ බගඃඊаІЗа¶З а¶ЄаІЗа¶ЬаІЗ а¶Йආට а¶Хට ථඌ а¶Ѓа¶£аІНа¶°а¶™а•§ ඕඌа¶Хට а¶ЄаІБථаІНබа¶∞ а¶ЄаІБථаІНබа¶∞ а¶Жа¶≤඙ථඌ, а¶Жа¶∞ а¶ђаІЗපගа¶∞а¶≠а¶Ња¶Ч ඙аІБа¶ЬаІЛа¶∞ а¶Ѓа¶£аІНධ඙аІЗа¶∞ ඀ගථගපගа¶В а¶Яа¶Ња¶Ъ а¶Еа¶ЈаІНа¶Яа¶ЃаІАа¶∞ а¶Єа¶Ха¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ පаІЗа¶Ј а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Йආට а¶®а¶Ња•§ а¶Еа¶ЈаІНа¶Яа¶ЃаІАа¶∞ බаІБ඙аІБа¶∞ а¶≠а¶∞аІЗ а¶Йආට а¶ЧаІЛඐගථаІНබ а¶≠аІЛа¶Ч а¶Ъа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶Ца¶ња¶ЪаІБа¶°а¶Ља¶ња¶∞ а¶ЄаІБа¶ЧථаІНа¶ІаІЗ, а¶Жа¶∞ а¶∞ඌට ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌඃඊ а¶≠а¶ња¶°а¶Љ ඐඌධඊට а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶Ња¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞а•§ а¶ЄаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Па¶Х ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£а¶ЦаІЛа¶≤а¶Њ а¶ЖථථаІНබ а¶ѓа¶Ња¶™а¶®а•§
ටа¶Цථ а¶°а¶ња¶°а¶њ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ а¶Яа¶ња¶≠а¶њ а¶ЪаІНඃඌථаІЗа¶≤, ඃඌටаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ ඙аІВа¶Ьа¶Њ ඙а¶∞а¶ња¶ХаІНа¶∞а¶Ѓа¶Њ බаІЗа¶Ца¶§а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ђа¶°а¶Љ а¶ђа¶°а¶Љ ඙аІНඃඌථаІНа¶°аІЗа¶≤аІЗа¶∞ පගа¶≤аІН඙а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓ а¶ЄаІЗ а¶Па¶Х а¶Еа¶ђа¶Ња¶Х а¶ђа¶ња¶ЄаІНа¶Ѓа¶ѓа¶Љ а¶Ьа¶Ња¶Чඌට а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗа•§ а¶Чට බаІБа¶ЯаІЛ බපа¶ХаІЗ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ ඐබа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Єа¶ђа¶Яа¶Ња¶За•§ а¶Па¶Цථ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ පයа¶∞аІЗа¶У а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ а¶ЄаІЗа¶З а¶Єа¶ђ ඙аІНඃඌථаІНа¶°аІЗа¶≤ ථගа¶∞аІНඁගට а¶єа¶ѓа¶Љ ථග඙аІБа¶£ බа¶ХаІНඣටඌඃඊ, а¶Па¶Цථ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ පයа¶∞аІЗа¶У බаІНඐගටаІАа¶ѓа¶Ља¶Њ, ටаІГටаІАа¶ѓа¶Ља¶Њ, а¶ЪටаІБа¶∞аІНඕаІАටаІЗ а¶Єа¶ђ ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ЙබаІНа¶ђаІЛ඲ථ а¶єа¶ѓа¶Љ, а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ ඁට ඀ගටаІЗ а¶ХаІЗа¶ЯаІЗа¶За•§ а¶Па¶З ටаІЛ а¶Чට а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌ පයа¶∞аІЗа¶∞ ඁයඌථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶ХаІЗа¶∞ ඙аІВа¶Ьа¶Њ а¶ђа¶≤аІЗ а¶ЦаІНඃඌට, а¶ЪаІЗටа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶ЦаІНඃඌට а¶Ѓа¶£аІНධ඙ ‘а¶ЈаІЛа¶≤аІЛа¶Ха¶≤а¶Њ ඙аІВа¶∞аІНа¶£’ а¶Па¶ђа¶Ња¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶°а¶Ља¶ња¶∞ ඙ඌපаІЗа¶За•§ ථඌ, а¶Па¶Цථ а¶Ја¶ЈаІНආаІАа¶∞ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ ඙ඌධඊඌа¶∞ а¶ХаІЛථаІЛ а¶ЙබаІНа¶ѓа¶ЃаІА බඌබඌ ථඌа¶УаІЯа¶Ња¶Ца¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ ඁඌඕඌаІЯ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ ඙аІНඃඌථаІНа¶°аІЗа¶≤аІЗ а¶∞а¶В а¶ШඣටаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ЄаІНට, а¶Пඁථа¶Яа¶Њ а¶Жа¶∞ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶Цථ ඪ඙аІНටඁаІАа¶∞ а¶Єа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ ‘а¶Жа¶≤඙ථඌа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶∞а¶В а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ХඌආаІЗа¶∞ а¶ЧаІБа¶Ба¶°а¶ЉаІЛ а¶Па¶ЦථаІЛ පаІБа¶ХаІЛа¶ѓа¶Љ ථග’ а¶ђа¶≤аІЗ ඙ඌධඊඌа¶∞ බගබගබаІЗа¶∞ а¶Ъа¶њаІОа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶Ба¶Ъа¶Ња¶ЃаІЗа¶Ъа¶њ а¶Жа¶∞ පаІЛථඌ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶Цථ а¶ЃаІЗබගථаІА඙аІБа¶∞ ථබаІАа¶ѓа¶Ља¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞පගа¶ХаІНඣගට ඙аІЗපඌබඌа¶∞ а¶≤аІЛа¶Ха¶Ьථ а¶Жа¶ЄаІЗ а¶Па¶ЦඌථаІЗа¶У, а¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶Љ а¶ЃаІЗ඙аІЗ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ѓа¶єа¶Ња¶≤а¶ѓа¶Ља¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶З ඙аІНඃඌථаІНа¶°аІЗа¶≤ ‘а¶°аІЗа¶≤а¶ња¶≠а¶Ња¶∞а¶њ’ බගඃඊаІЗ බаІЗа¶ѓа¶Ља•§ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶Ъඌ඙ ඕඌа¶ХаІЗ ටඌබаІЗа¶∞а¶У, а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌඃඊ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶≠а¶Ња¶∞аІНа¶ЪаІБа¶ѓа¶Ља¶Ња¶≤а¶њ а¶ЄаІЗа¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶ЙබаІНа¶ђаІЛ඲ථ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶ЄаІНа¶ђаІЯа¶В а¶ЃаІБа¶ЦаІНඃඁථаІНටаІНа¶∞аІАа•§ а¶ЄаІНඕඌථаІАа¶ѓа¶Љ ථаІЗටඌ, ඁථаІНටаІНа¶∞аІА, ඐගපගඣаІНа¶Яа¶Ьථ බගඃඊаІЗ а¶ЙබаІНа¶ђаІЛ඲ථ ටаІЛ ඙а¶∞аІЗа¶∞ ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Ља•§ ටаІГටаІАа¶ѓа¶Ља¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌඃඊ а¶≠а¶ња¶°а¶Љ а¶єа¶ѓа¶Љ а¶Па¶Цථ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ђа¶Га¶ЄаІНа¶ђа¶≤аІЗа¶Уа•§ а¶∞а¶ХаІНа¶ЈаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Ња¶З, а¶Па¶З පයа¶∞а¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ ඁට а¶ђа¶°а¶Љ а¶ЖඃඊටථаІЗа¶∞ ථඃඊ а¶ђа¶≤аІЗ, а¶ЯаІНа¶∞аІЗථ-а¶ђа¶Ња¶Є-а¶Еа¶ЯаІЛ а¶Ха¶∞аІЗ පයа¶∞аІЗа¶∞ а¶Па¶Х඙аІНа¶∞ඌථаІНට ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЕථаІНඃ඙аІНа¶∞ඌථаІНට ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶ЫаІБа¶ЯටаІЗ а¶єа¶ѓа¶Љ ථඌ, а¶Па¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ а¶єа¶Ња¶Ба¶Яа¶≤аІЗ а¶Па¶Х ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Єа¶ђ ඙аІВа¶Ьа¶Њ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Ља•§ а¶Па¶Ха¶ђа¶Ња¶∞, බаІБа¶ђа¶Ња¶∞, ටඌа¶∞඙а¶∞ а¶Па¶Ха¶ШаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗа¶У а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඁට а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶∞а¶За•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЄаІЗа¶Єа¶ђ ථගඃඊаІЗ ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌබаІЗа¶∞ а¶ХаІЛථаІЛ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Жа¶ЄаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ ථඌ, а¶Ьа¶Ѓа¶ХаІЗа¶∞ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Ха¶Њ බаІЗа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ а¶ХаІЛථаІЛ බа¶∞аІНපථ ටаІЛ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗа¶З ථаІЗа¶За•§

а¶Па¶З а¶Ьа¶Ѓа¶ХаІЗа¶∞ а¶ЙаІОа¶Є ඪථаІН඲ඌථ а¶Жа¶Ь а¶ђа¶°а¶Љ а¶Ьа¶∞аІБа¶∞а¶ња•§ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ђа¶°а¶Љ පයа¶∞ පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБа¶°а¶Ља¶њ а¶ѓаІЗඁථ ටඌа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ха¶Єа¶ЃаІЛ඙а¶≤а¶ња¶Яඌථ а¶ЪаІЗа¶єа¶Ња¶∞а¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌථа¶Чට а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗа•§ а¶Ѓа¶Ња¶≤බඌ а¶ђа¶Њ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඁට а¶ЬаІЗа¶≤а¶Њ ඪබа¶∞аІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Ьථඪа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Жа¶Іа¶ња¶ХаІНа¶ѓа•§ а¶ЄаІНа¶ђа¶≠ඌඐටа¶З а¶Па¶За¶Єа¶ђ පයа¶∞аІЗ ප඙ගа¶В а¶Ѓа¶≤, а¶Ѓа¶Ња¶≤аІНа¶Яග඙аІНа¶≤аІЗа¶ХаІНа¶Є а¶ЗටаІНඃඌබගа¶∞ а¶Жа¶ђа¶ња¶∞аІНа¶≠а¶Ња¶ђ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ථаІНа¶ѓа¶Ња¶Ъа¶Ња¶∞а¶Ња¶≤ а¶ЧаІНа¶∞аІЛа¶•а•§ а¶ХගථаІНටаІБ ඁඌඕඌа¶≠а¶Ња¶ЩаІНа¶Ча¶Њ, බගථයඌа¶Яа¶Њ, а¶ІаІБ඙а¶ЧаІБа¶°а¶Ља¶њ, а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶Ња¶ЦаІНа¶ѓа¶Ња¶ЧаІБа¶°а¶Ља¶њ а¶Па¶За¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶ЫаІЛа¶Я පයа¶∞аІЗа¶У а¶Па¶Цථ а¶Па¶Ха¶Ња¶Іа¶ња¶Х ප඙ගа¶В а¶Ѓа¶≤аІЗа¶∞ а¶Й඙ඪаІНඕගටග а¶ХаІЗථ? а¶Па¶∞ ඙аІЗа¶ЫථаІЗ а¶Жа¶∞аІНඕගа¶Х а¶ѓаІЛа¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶ХаІЛථаІЛ а¶ЄаІБථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Я ඙а¶∞а¶ња¶ХඌආඌඁаІЛ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ථа¶Ьа¶∞аІЗ ඙ධඊаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Па¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤а¶ЧаІБа¶≤аІЛටаІЗ а¶ХаІЛථаІЛ පගа¶≤аІН඙ඌඃඊථ ටаІЛ а¶Ша¶ЯаІЗа¶®а¶ња•§ а¶Жа¶∞ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶њ а¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞а¶ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ ටаІЛ а¶ХаІНа¶∞а¶Ѓа¶Ња¶Чට а¶Єа¶Ва¶ХаІБа¶Ъගට а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Еටа¶Па¶ђ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶Еа¶Ва¶ХаІЗа¶∞ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶Па¶З а¶ЫаІЛа¶Я а¶Ѓа¶Ђа¶Га¶ЄаІНа¶ђа¶≤ පයа¶∞а¶ЧаІБа¶≤аІЛටаІЗ ථа¶Ча¶∞ඌඃඊථаІЗа¶∞ а¶Чටග පаІНа¶≤ඕа¶З а¶єа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ а¶Йа¶Ъа¶ња¶§а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ ආගа¶Х а¶Йа¶≤а¶ЯаІЛа¶Яа¶Ња•§ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ථගа¶∞аІНа¶Ѓа¶Ѓ а¶ђа¶Ња¶ЄаІНටඐ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶Па¶З а¶ѓаІЗ, а¶Ха¶ња¶ЫаІБබගථ а¶Жа¶ЧаІЗ ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶ѓаІЗ පаІНа¶∞аІЗа¶£аІАа¶ХаІЗ ‘а¶≤аІБа¶ЃаІН඙аІЗථ ඙аІНа¶∞а¶≤аІЗටඌа¶∞а¶ња¶ѓа¶ЉаІЗට’ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Ъа¶ња¶єаІНථගට а¶Ха¶∞ටඌඁ, ටඌа¶∞а¶Њ а¶Жа¶Ь ‘а¶≤аІБа¶ЃаІН඙аІЗථ а¶ђаІБа¶∞аІНа¶ЬаІБа¶ѓа¶Ља¶Њ’ටаІЗ а¶∞аІВ඙ඌථаІНටа¶∞ගට а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ ටඌа¶∞а¶Ња¶З а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ ථඌථඌථ а¶ЄаІНටа¶∞аІЗ а¶Йа¶ЮаІНа¶Ыа¶ђаІГටаІНටග а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЦаІЛа¶≤а¶Ња¶Ѓа¶ХаІБа¶Ъа¶ња¶∞ ඁට а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ а¶Й඙ඌа¶∞аІНа¶Ьථ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа•§ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Ха¶њ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ-а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග-а¶ЃаІВа¶≤аІНа¶ѓа¶ђаІЛа¶І ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶ња¶ЪаІНа¶ѓаІБට ඃඌ඙ථ ටඌබаІЗа¶∞, а¶≠аІЛа¶ЧඐඌබаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ а¶ХаІЛථаІЛ බа¶∞аІНපථ ථаІЗа¶За•§ ටඌа¶∞а¶Ња¶З а¶Па¶Цථ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶За¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶Еථගа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ ථගаІЯථаІНටаІНа¶∞а¶£ а¶Ха¶∞аІЗа•§ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Ъඌයගබඌ а¶ЃаІЗа¶ЯඌටаІЗа¶З ඙аІНа¶∞ඌබаІБа¶∞аІНа¶≠а¶Ња¶ђ а¶Па¶За¶Єа¶ђ а¶Ѓа¶≤-а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞а•§ ටඌබаІЗа¶∞ ඐබඌථаІНඃටඌаІЯ යගථаІНබග ඥаІБа¶ХаІЗ ඙аІЬа¶ЫаІЗ а¶Ѓа¶Ђа¶ЄаІНа¶ђа¶≤ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ ඁථථаІЗ а¶ЬаІАඐථаІЗа•§ ටඌබаІЗа¶∞ බаІМа¶∞ඌටаІНа¶ЃаІНа¶ѓаІЗа¶З а¶єа¶Ња¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Ха¶њ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња•§
а¶Жа¶∞ ඙аІНа¶∞පаІНථа¶Яа¶Њ а¶Па¶ЦඌථаІЗа¶З, බඌඃඊа¶Яа¶Њ а¶Ха¶Ња¶∞? а¶ЙටаІНටа¶∞ ඃබග а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬටаІЗ а¶єа¶ѓа¶Љ, а¶ђа¶Ња¶Ща¶Ња¶≤а¶њ а¶ђаІБබаІНа¶Іа¶ња¶ЬаІАа¶ђаІА а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ХаІЗа¶З ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶Жඃඊථඌඃඊ බඌа¶БධඊඌටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶Па¶Яа¶Њ а¶ђаІБа¶ЭටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ, а¶Ча¶£а¶§а¶Ња¶®аІНටаІНа¶∞а¶ња¶Х а¶≤аІЗа¶Ца¶Х පගа¶≤аІН඙аІА а¶Єа¶Ва¶ШаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඐගථගඃඊаІЛа¶Ч а¶Ха¶∞ගථග, ටඌа¶∞ а¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ђаІЗපග а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶њ පаІНа¶∞а¶Ѓа¶ња¶Х а¶Єа¶Ва¶ЧආථаІЗ, а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ ටඌа¶∞а¶Ња¶З а¶Ѓа¶ња¶Ыа¶ња¶≤аІЗ а¶≠а¶ња¶°а¶Љ а¶ђа¶Ња¶°а¶Ља¶ња¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶∞ඐගආඌа¶ХаІБа¶∞а¶ХаІЗ а¶°аІНа¶∞а¶ѓа¶Ља¶ња¶Ва¶∞аІБа¶Ѓ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞ගථග, ටඌа¶Ба¶∞ а¶ђа¶ња¶ђа¶ња¶І а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶≠ඌඐථඌа¶ХаІЗ а¶Ьථа¶Ча¶£аІЗа¶∞ а¶Єа¶єа¶Ь඙ඌа¶ЪаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ බඌඃඊගටаІНа¶ђ а¶ХаІЗа¶Й ථගа¶За¶®а¶ња•§ а¶Йа¶≤аІНа¶ЯаІЗ ඪටаІНටа¶∞ බපа¶Х ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ ඪඌයගටаІНа¶ѓ, පගа¶≤аІН඙, ඪගථаІЗа¶Ѓа¶Њ а¶ЗටаІНඃඌබග а¶Ча¶£а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶Ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶ХаІЗ ඃඕඌඪඁаІНа¶≠а¶ђ බаІБа¶∞аІНа¶ђаІЛа¶ІаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞аІЗ ටаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Њ, 'а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞а¶њ' පගа¶≤аІН඙-ඪඌයගටаІНа¶ѓ ථඌඁаІЗ පаІНа¶∞аІЗа¶£аІА ඙аІГඕа¶ХаІАа¶Ха¶∞а¶£, а¶ЄаІЗа¶За¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІАа¶ѓа¶Љ а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Ха¶њ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Єа¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶ХаІЗ а¶Еа¶ђа¶ЬаІНа¶Юа¶Њ а¶ђа¶Њ බаІНа¶∞аІБට а¶≠аІЗа¶ЩаІЗа¶ЪаІБа¶∞аІЗ බаІЗа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶Яа¶ња¶Є а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶Па¶Єа¶ђаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶£а¶Ња¶Ѓа¶З а¶єа¶≤аІЛ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගටаІЗ а¶Е඙аІЗа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶ХаІГට ‘а¶Ъа¶ЯаІБа¶≤’ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶єаІБа¶єаІБ а¶ЕථаІБ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗа¶ґа•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶Ша¶Ња¶°а¶Љ ඕаІЗа¶ХаІЗ බඌඃඊ а¶ЭаІЗа¶°а¶ЉаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤ටаІЗ а¶Па¶З а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶ХаІЗ පаІБа¶ІаІБඁඌටаІНа¶∞ а¶ЧаІЛа¶ђа¶≤а¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬථаІАටගа¶∞ а¶ЕථаІБ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶ђа¶≤аІЗ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ ඃටа¶З ඪඌථаІНටаІНඐථඌ බගа¶З ථඌ а¶ХаІЗථ, а¶ЧаІЛа¶ђа¶≤а¶ѓа¶Ља¶ХаІЗ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶З а¶≠аІВа¶Ца¶£аІНа¶°аІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ж඲ග඙ටаІНа¶ѓ а¶ђа¶ња¶ЄаІНටඌа¶∞ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶ХаІЛථаІЛ а¶Ъа¶ХаІНа¶∞ඌථаІНට а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єа¶ѓа¶Љ ථග, а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ ඙аІНа¶∞а¶ѓа¶ЉаІЛа¶Ьථ ඙ධඊаІЗа¶®а¶ња•§ а¶ЄаІЗа¶З බаІВа¶∞аІНа¶ЃаІБа¶Ц а¶ЪаІМа¶ІаІБа¶∞аІА а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ а¶Ха¶ђаІЗа¶З а¶ђа¶≤аІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ, а¶Ьඌටග а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ЖටаІНа¶Ѓа¶ШඌටаІАа•§
Have an account?
Login with your personal info to keep reading premium contents
You don't have an account?
Enter your personal details and start your reading journey with us
Design & Developed by: WikiIND
Maintained by: Ekhon Dooars Team