




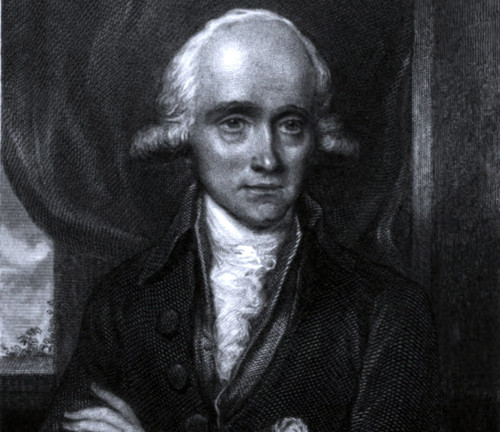
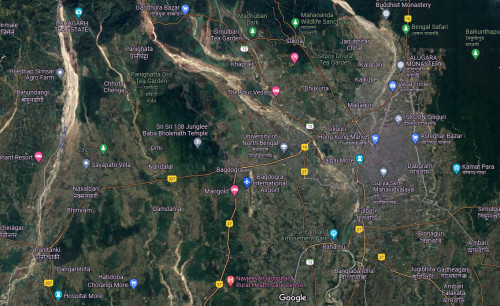
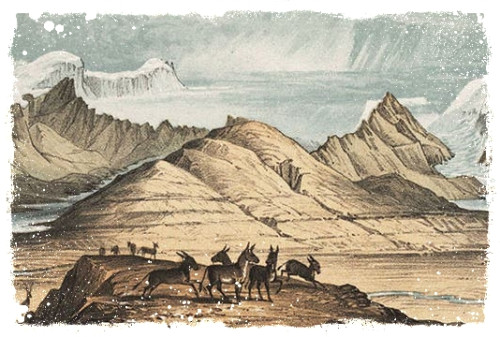





 а¶Єа¶ђаІНа¶ѓа¶Єа¶Ња¶ЪаІА බටаІНට
а¶Єа¶ђаІНа¶ѓа¶Єа¶Ња¶ЪаІА බටаІНට

බаІЛටඌа¶∞а¶Ња¶°а¶Ња¶Ща¶Њ ඙ඌа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЕථаІНඃටඁ а¶Ьථ඙аІНа¶∞а¶њаІЯ ඙ඌа¶≤а¶Њ ‘а¶Ха¶∞а¶ња¶Ѓ ඐඌබපඌ’а•§ а¶Ха¶∞а¶ња¶Ѓ ඐඌබපඌ ඙ඌа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Хඌයගථග а¶Єа¶Ва¶ХаІНа¶ЈаІЗ඙аІЗ а¶Па¶За¶∞аІВ඙, බаІАа¶∞аІНа¶Ша¶Ха¶Ња¶≤ а¶Е඙аІБටаІНа¶∞а¶Х ඕඌа¶Ха¶Ња¶∞ ඙а¶∞ ඪබаІНа¶ѓаІЛа¶Ьඌට ඙аІБටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶Ц බаІЗа¶ЦаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£ а¶ЬаІБаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤ ‘а¶Ха¶∞а¶ња¶Ѓ ඐඌබපඌ’а¶∞а•§ а¶ЦаІБපගටаІЗ а¶≠а¶∞аІЗ а¶Йආа¶≤ а¶Ѓа¶®а•§ а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗа¶∞ а¶ЖථථаІНබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ බඌථ-а¶ІаІНඃඌථаІЗ а¶ЃаІЗටаІЗ а¶Йආа¶≤аІЗථ а¶§а¶ња¶®а¶ња•§ ඐඌබපඌ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ යඌටаІЗ ඪඌටබගථ ඪඌටа¶∞ඌට а¶Па¶Ха¶Яඌථඌ බඌථ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ ඙а¶∞ а¶ХаІНа¶≤ඌථаІНට а¶єаІЯаІЗ ඪග඙ඌයаІАබаІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶ЄаІЗ а¶≠а¶Ња¶∞ а¶ЫаІЗаІЬаІЗ ඐගපаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Па¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶ХаІНа¶Ја¶£ ඙а¶∞ а¶Па¶≤аІЗථ а¶ЃаІВа¶∞аІНපගබ а¶Ча¶Ња¶Ьа¶ња•§ බඌථ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶∞аІНඕථඌ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЭаІЛа¶≤а¶Њ а¶ЦаІБа¶≤аІЗ а¶Іа¶∞а¶≤аІЗа¶®а•§ ඐඌබපඌа¶∞ а¶≤аІЛа¶Х а¶ЖපаІНа¶Ъа¶∞аІНа¶ѓ а¶єаІЯаІЗ а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ а¶ЃаІВа¶∞аІНපගබаІЗа¶∞ а¶ЭаІЛа¶≤а¶ЊаІЯ а¶ѓа¶Ња¶За¶З බඌථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯ ථගඁаІЗа¶ЈаІЗ а¶ЕබаІГපаІНа¶ѓ а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Єа¶ђа•§ а¶Ца¶ђа¶∞ а¶ЧаІЗа¶≤ ඐඌබපඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа•§ а¶ЖපаІНа¶Ъа¶∞аІНа¶ѓ а¶Па¶З а¶Хඕඌ පаІБථаІЗ а¶Ха¶∞а¶ња¶Ѓ ඐඌබපඌ а¶єа¶Ња¶Ьа¶ња¶∞ а¶єа¶≤аІЗථ а¶Ча¶Ња¶Ьа¶ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа•§ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ ටගථග а¶ХаІА а¶Ъඌථ! а¶ѓа¶Њ а¶Ъа¶Ња¶За¶ђаІЗථ ටඌа¶З ටаІБа¶≤аІЗ බаІЗа¶ђаІЗථ ටඌа¶Ба¶∞ යඌටаІЗа•§ а¶ЄаІНඁගට а¶єаІЗа¶ЄаІЗ а¶ЃаІВа¶∞аІНපගබ а¶Ьඌථඌа¶≤аІЗථ, ටගථ а¶Жа¶ЩаІБа¶≤аІЗа¶∞ ඁඌඕඌаІЯ ඃටа¶ЯаІБа¶ХаІБ а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶њ а¶Іа¶∞аІЗ ටටа¶ЯаІБа¶ХаІБа¶З а¶Ъа¶Ња¶За•§ а¶Па¶З а¶ХඕඌаІЯ ඙аІНа¶∞а¶ђа¶≤ а¶ЖටаІНඁඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІЗ ඐඌබපඌ а¶ЃаІВа¶∞аІНපගබа¶ХаІЗ ථගаІЯаІЗ ථගටаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Ча¶Ња¶Ьа¶њ ටගථ а¶Жа¶ЩаІБа¶≤аІЗа¶∞ ඁඌඕඌаІЯ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට ඙аІГඕගඐаІА ටаІБа¶≤аІЗ а¶Іа¶∞а¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Ђа¶≤аІЗ ඐඌබපඌа¶∞ а¶Жа¶∞ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З а¶∞а¶За¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Еඕа¶Ъ а¶ЃаІВа¶∞аІНපගබ а¶Ъа¶Ња¶За¶≤аІЗථ බඌථаІЗа¶∞ බа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£а¶Ња•§ ඐඌබපඌ ටа¶Цථ ථගа¶ЬаІЗа¶ХаІЗа¶З ටаІБа¶≤аІЗ බගа¶≤аІЗථ ටඌа¶Ба¶∞ යඌටаІЗа•§ а¶ПටаІЗ а¶ЦаІБа¶ђ а¶ЦаІБපග а¶єа¶≤аІЗථ а¶ЃаІВа¶∞аІНපගබ а¶Ча¶Ња¶Ьа¶ња•§ а¶Жа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶∞ а¶∞аІВ඙ а¶Іа¶∞аІЗ а¶ЖපаІАа¶∞аІНඐඌබ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ ඐඌබපඌа¶ХаІЗ а¶Па¶ђа¶В а¶Ђа¶ња¶∞а¶њаІЯаІЗ බගа¶≤аІЗථ а¶Єа¶ђа¶Ха¶ња¶ЫаІБа•§ а¶Ха¶∞а¶ња¶Ѓ ඐඌබපඌ а¶ЄаІБа¶ЦаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЬටаІНа¶ђ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶≤а¶Ња¶Ча¶≤аІЗа¶®а•§
а¶Па¶З а¶ХඌයගථගටаІЗ බපඌඐටඌа¶∞аІЗа¶∞ а¶Хඌයගථගа¶Чට а¶Ѓа¶ња¶≤ а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓа¶£аІАаІЯа•§ බපඌඐටඌа¶∞аІЗа¶∞ ඙а¶ЮаІНа¶Ъа¶Ѓ а¶Еඐටඌа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ѓа¶®а•§ බаІИටаІНа¶ѓа¶∞а¶Ња¶Ь а¶ђа¶≤а¶ња¶∞ а¶ХаІНඣඁටඌ а¶Ца¶∞аІНа¶ђ а¶Ха¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶≠а¶Чඐඌථ а¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶£аІБ ඐඌඁථ а¶∞аІВ඙аІЗ а¶Жа¶ђа¶ња¶∞аІНа¶≠аІВට а¶єа¶®а•§ බඌථඐаІАа¶∞ а¶ђа¶≤аІЗ а¶ЦаІНඃඌට а¶ђа¶≤а¶њ බඌථ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶За¶≤аІЗ ඐඌඁථа¶∞аІВ඙аІА а¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶£аІБ ටගථ ඙ඌаІЯаІЗа¶∞ ඪඁඌථ а¶Ьа¶Ѓа¶њ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶∞аІНඕථඌ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ЖටаІНඁඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІЗ а¶≠а¶∞඙аІБа¶∞ а¶ђа¶≤а¶њ а¶ЦаІБපගඁථаІЗ ටඌ බගටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶За¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Па¶За¶ХඕඌаІЯ ඐඌඁථаІЗа¶∞ පа¶∞аІАа¶∞ а¶ХаІНа¶∞ඁපа¶Г а¶ђаІЬ а¶є’ටаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа•§ ඁඌඕඌ а¶Жа¶Хඌප а¶ЂаІБа¶БаІЬаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ ඐඌඁථ ටඌа¶Ба¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ ඙ඌ а¶∞а¶Ња¶Ца¶≤аІЗථ а¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІНа¶ЧаІЗ, බаІНඐගටаІАаІЯ ඙ඌ а¶∞а¶Ња¶Ца¶≤аІЗථ ඙аІГඕගඐаІАටаІЗа•§ ටаІГටаІАаІЯ ඙ඌ а¶ХаІЛඕඌаІЯ а¶∞а¶Ња¶Ца¶ђаІЗථ а¶ЄаІЗ а¶Хඕඌ а¶Ьа¶ња¶ЬаІНа¶Юа¶Ња¶Єа¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶З බаІИටаІНа¶ѓа¶∞а¶Ња¶Ь а¶ђа¶≤а¶њ а¶єа¶Ња¶Ба¶ЯаІБа¶ЃаІБаІЬаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ ඁඌඕඌаІЯ ටаІГටаІАаІЯ ඙බ а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Па¶З а¶Хඌයගථග а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗа¶∞а¶З а¶Ьа¶Ња¶®а¶Ња•§ а¶Ха¶∞а¶ња¶Ѓ ඐඌබපඌ ඙ඌа¶≤а¶ЊаІЯ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ බаІЗа¶Ца¶њ ටඌ а¶ЕථаІНа¶ѓа¶∞аІВ඙аІЗа•§ ඙аІБа¶∞а¶Ња¶£аІЗа¶∞ а¶ХඌයගථගටаІЗ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ а¶Ъа¶∞ගටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Й඙ඪаІНඕගටග а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ බаІЗа¶Ца¶њ ඪටаІНඃ඙аІАа¶∞ ඙ඌа¶≤ඌටаІЗа¶Уа•§ බаІБа¶З а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІЗа¶∞ ථගа¶∞аІНа¶ђа¶ња¶ШаІНථ а¶Єа¶єа¶Ња¶ђа¶ЄаІНඕඌථ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ а¶РටගයаІНа¶ѓа•§ а¶Ђа¶≤аІНа¶ЧаІБа¶Іа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞ ථаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ђаІЯаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗа¶ЫаІЗ а¶Жа¶Ьа¶Уа•§ а¶ђа¶єа¶ња¶∞а¶Ња¶Чට а¶ХаІНඣඁටඌ а¶Па¶ЄаІЗ а¶Па¶З а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Х ථඣаІНа¶Я а¶Ха¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Єа¶Ђа¶≤ а¶єаІЯථග, а¶єа¶ђаІЗ ථඌ—а¶Па¶З ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Жа¶ЫаІЗа•§
බаІЛටඌа¶∞а¶Ња¶°а¶Ња¶Ща¶Њ ඙ඌа¶≤а¶ЊаІЯ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶єаІЯа•§ а¶ЃаІВа¶≤ а¶Ча¶ЊаІЯа¶Х а¶ђа¶Њ а¶ЧаІАබඌа¶≤аІЗа¶∞ යඌටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ ටඌа¶∞аІЗа¶∞ ඐඌබаІНඃඃථаІНටаІНа¶∞ බаІЛටඌа¶∞а•§ а¶Па¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶У а¶Єа¶Ња¶∞а¶ња¶ЮаІНа¶Ьа¶Њ, а¶ђаІЗа¶єа¶Ња¶≤а¶Њ, а¶ђа¶Ња¶БපаІА, ඪඌථඌа¶З, ඥаІЛа¶≤, а¶єа¶Ња¶∞а¶ЃаІЛථගаІЯа¶Ња¶Ѓ ඙аІНа¶∞а¶≠аІГටග ඐඌබаІНඃඃථаІНටаІНа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єаІГට а¶єаІЯа•§ а¶Ьථ඙аІНа¶∞а¶њаІЯ а¶Хඌයගථගа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ ඁථඁаІБа¶ЧаІНа¶Іа¶Ха¶∞ а¶Еа¶≠ගථаІЯ а¶У а¶ЄаІБථаІНබа¶∞ а¶Ча¶Ња¶®а•§ а¶єа¶ЊаІЬа¶єаІАа¶Ѓ а¶Ха¶∞а¶Њ පаІАටаІЗа¶∞ а¶∞ඌටаІЗа¶У а¶ЦаІЛа¶≤а¶Њ а¶Жа¶ХඌපаІЗа¶∞ ථගа¶ЪаІЗ а¶ЦаІЬаІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶Ъа¶Я а¶ђа¶Њ ටаІНа¶∞ග඙а¶≤ а¶ђа¶ња¶Ыа¶њаІЯаІЗ ඙ඌа¶≤а¶Њ а¶Й඙а¶≠аІЛа¶Ч а¶Ха¶∞аІЗථ බа¶∞аІНපа¶Ха•§ ඙ඌа¶Ба¶ЪපаІЛ, а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Њ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶Єа¶ЃаІЯ ටඌа¶∞а¶У а¶ђаІЗපග ඁඌථаІБа¶Ј ඕඌа¶ХаІЗථ а¶Па¶Х а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Жа¶Єа¶∞аІЗа•§ а¶П а¶Па¶Х а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Жа¶Ха¶∞аІНа¶Ја¶£, ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£аІЗа¶∞ а¶ЫаІЛа¶БаІЯа¶Њ, а¶∞а¶ХаІНටаІЗа¶∞ а¶Яа¶Ња¶®а•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶Ба¶∞а¶Њ ‘а¶ЄаІБපаІАа¶≤ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗ’ ඙аІНа¶∞аІЗа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶ЧаІГа¶є а¶≠а¶ЊаІЬа¶Њ а¶Х’а¶∞аІЗ ඁථаІЛа¶∞а¶Ѓ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌа¶∞ ඙а¶∞ ථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶ЊаІЯаІЛа¶ЬථаІЗ බа¶∞аІНපа¶Х ඙ඌа¶З යඌටаІЗ а¶ЧаІЛථඌ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶ђа¶Њ а¶Йа¶Ъа¶њаІОа•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ча¶≤බа¶Яа¶Њ ආගа¶Х а¶ХаІЛථ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯа•§
а¶єаІБබаІБа¶Ѓ-බаІЗа¶У
а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶Ча¶≠аІАа¶∞ටඌ ටඌа¶∞ а¶ЧඌථаІЗа•§ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІАථ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь а¶ЬаІАඐථаІЗ а¶ђа¶Ња¶∞аІЛ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗ ටаІЗටаІНа¶∞ගප ඙ඌа¶∞аІНа¶ђа¶£а•§ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටගа¶∞ а¶ХаІЛа¶≤аІЗ ඙ගආаІЗ ඁඌථаІБа¶Ј а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња•§ ටඌа¶З а¶ЬаІАඐථ а¶Ъа¶∞аІНа¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ЃаІВа¶≤ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටගа¶ХаІЗ а¶Ша¶ња¶∞аІЗа•§ а¶ЂаІБа¶≤-඙ඌටඌа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ХаІГටගа¶Х а¶Й඙а¶Ъа¶Ња¶∞ а¶ѓаІЗඁථ а¶Єа¶Ња¶Ьа¶њаІЯаІЗ ථаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶єаІЯ ටаІЗඁථа¶З පа¶∞аІАа¶∞, ඁථ, а¶Чඌථа¶У а¶Й඙а¶Ъа¶Ња¶∞ а¶∞аІВ඙аІЗ ථගඐаІЗබථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටග ඙аІВа¶Ьа¶ЊаІЯа•§ ඙аІБа¶ЬаІЛ ඙ඌа¶∞аІНඐථ а¶Й඙а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІЗ а¶ЃаІЗа¶≤а¶Ња¶У а¶ђа¶ЄаІЗа•§ а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІА ඙ඌа¶∞аІНа¶ђа¶£ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Єа¶ЃаІЯа¶З а¶ЙаІОа¶Єа¶ђаІЗа¶∞ а¶∞аІВ඙ ථаІЗаІЯа•§ а¶ЕථаІЗа¶Х ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ЃаІЗа¶≤а¶Ња¶ЃаІЗපඌ, а¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶∞ а¶Жබඌථ ඙аІНа¶∞බඌථ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Ха¶ХаІЗ а¶Ча¶≠аІАа¶∞ а¶Х’а¶∞аІЗ ටаІЛа¶≤аІЗа•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІА ඙ඌа¶∞аІНа¶ђа¶£ а¶Ша¶ња¶∞аІЗ а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ а¶єаІЯ ථඌ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගа¶Яа¶њ ඁඌථаІБа¶Ј ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓа¶ХаІНа¶Ј а¶ђа¶Њ ඙а¶∞аІЛа¶ХаІНа¶Ј а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЬаІЬа¶њаІЯаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ ටඌටаІЗа•§ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ‘а¶єаІБබаІБа¶Ѓ-බаІЗа¶У’ а¶Па¶Х а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІА а¶ђаІНඃටගа¶ХаІНа¶∞а¶ЃаІА ඙аІВа¶ЬඌථаІБа¶ЈаІНа¶†а¶Ња¶®а•§ а¶ЃаІВа¶≤ට а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤ඌබаІЗа¶∞ බаІНа¶ђа¶Ња¶∞а¶Њ ථගаІЯථаІНටаІНа¶∞ගට а¶Па¶З а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗ ඙аІБа¶∞аІБа¶ЈаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප ථගඣගබаІНа¶Іа•§ а¶ЄаІЗ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථ බаІВа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶У බа¶∞аІНපථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ђа¶Ња¶∞а¶£ ටඌබаІЗа¶∞а•§ ථගа¶∞аІНබаІЗප а¶ЕඁඌථаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗ ඙аІЗටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ а¶Хආගථ පඌඪаІНа¶§а¶ња•§ а¶ЄаІЗ පඌඪаІНටගа¶∞ а¶Ђа¶≤ ඙аІЗටаІЗ а¶є’ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђа¶Ња¶За¶ХаІЗа•§
‘а¶єаІБබаІБа¶Ѓ-බаІЗа¶У’ ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЬаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Жа¶Ха¶∞аІНа¶Ја¶£аІАаІЯ ‘඙ඌа¶∞а¶Ђа¶∞а¶ЃаІНඃඌථаІНа¶Є’а•§ ඙аІВа¶Ьа¶Њ а¶Еа¶∞аІНа¶Ъථඌа¶∞ а¶Ьа¶∞аІБа¶∞аІА а¶Еа¶ЩаІНа¶Ч а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ѓаІБа¶ХаІНට а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Ња¶∞а¶Њ а¶Чඌථ а¶У ථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІА а¶Еа¶≠ගථаІЯ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Па¶З а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථ а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථ а¶єаІЯ а¶Жа¶Ја¶ЊаІЭ-පаІНа¶∞ඌඐථ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗа•§ а¶ЧаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶ЃаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ђа¶≤ බඌඐබඌයаІЗа¶∞ ඙а¶∞ ථаІЗа¶ЃаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗ а¶ђа¶∞аІНа¶Ја¶Ња•§ а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶ЬаІАа¶ђа¶њ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Жа¶Ја¶ЊаІЭ-පаІНа¶∞ඌඐථ а¶Па¶З බаІБ’а¶Ѓа¶Ња¶Є а¶У а¶Жа¶ЧаІЗ-඙а¶∞аІЗ а¶Жа¶∞а¶У ඙ථаІЗа¶∞ බගථ ඙аІНа¶∞а¶ђа¶≤ а¶ђа¶∞аІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯа•§ а¶Шථ а¶Ха¶Ња¶≤аІЛ а¶ЃаІЗа¶Ш ඕаІЗа¶ХаІЗ ථඌඁаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђа¶≤ а¶Іа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞ а¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња•§ а¶Ъа¶Ња¶∞ගබගа¶Х а¶Єа¶ђаІБа¶Ь а¶єаІЯ а¶Жа¶∞а¶Уа•§ а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ а¶ХаІГа¶Ја¶Х ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ЄаІНට а¶єаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗ а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа•§ а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶∞ а¶ђаІБа¶Х а¶Ъа¶Ја¶Њ а¶єаІЯа•§ ථа¶∞а¶Ѓ а¶Хඌබඌ-а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶∞ а¶ЄаІЛа¶Бබඌ а¶ЧථаІНа¶ІаІЗ а¶≠а¶∞аІЗ а¶УආаІЗ а¶Ъа¶Ња¶∞а¶™а¶Ња¶ґа•§ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Ђа¶Єа¶≤ а¶ђаІЛථඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ьа•§ а¶Ха¶Ња¶∞аІБа¶∞ ඐගපаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ ථаІЗа¶За•§ ඁථаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ЖථථаІНа¶¶а•§ ථටаІБථ а¶Ђа¶Єа¶≤ а¶ЙаІО඙ඌබථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶њаІЯа¶ЊаІЯ а¶ЬаІЬа¶њаІЯаІЗ ඕඌа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЖථථаІНа¶¶а•§
а¶Па¶З а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ња¶Х ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපаІЗа¶∞ а¶ђаІНඃටаІНа¶ѓаІЯ а¶єаІЯ а¶Ха¶Цථа¶Уа•§ а¶Жа¶ХඌපаІЗ а¶ЃаІЗа¶ШаІЗа¶∞ а¶Ха¶£а¶Ња¶Ѓа¶Ња¶§аІНа¶∞ බаІЗа¶Ца¶Њ ථаІЗа¶За•§ а¶ЕටаІНа¶ѓа¶Іа¶ња¶Х а¶Йа¶ЬаІНа¶ЬаІНа¶ђа¶≤ а¶ЄаІВа¶∞аІНа¶ѓаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ца¶∞ а¶ЙටаІНටඌ඙ ඙аІБаІЬа¶њаІЯаІЗ බаІЗаІЯ а¶ѓаІЗа¶®а•§ පаІБа¶Ха¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗ а¶Ца¶Ња¶≤-а¶ђа¶ња¶≤-඙аІБа¶ХаІБа¶∞-ථබаІА-ථඌа¶≤а¶Њ-а¶Эа¶ња¶≤-බගа¶Ша¶ња•§ а¶ХаІНа¶∞ඁපа¶Г а¶Єа¶ђаІБа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶∞аІЛа¶є а¶Ха¶ЃаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗа•§ а¶ІаІВа¶Єа¶∞ а¶єаІЯ а¶Ъа¶Ња¶∞а¶™а¶Ња¶ґа•§ а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶∞ а¶ђаІБа¶Х а¶ЂаІЗа¶ЯаІЗ а¶ЪаІМа¶Ъа¶ња¶∞а•§ а¶Жа¶ХඌපаІЗ а¶ЃаІЗа¶ШаІЗа¶∞ බаІЗа¶Ца¶Њ ථаІЗа¶З, а¶ђа¶∞а¶Ја¶Ња¶∞ а¶Ьа¶≤ ථаІЗа¶За•§ а¶ХаІГа¶Ја¶ХаІЗа¶∞ а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗ а¶Ьа¶≤а•§ ඙а¶≤аІНа¶≤аІАа¶Ха¶ђа¶њ а¶Ьа¶Єа¶ња¶Ѓа¶ЙබаІНබගථаІЗа¶∞ а¶ђаІБа¶ХаІЗ ටඌа¶З а¶ЄаІЗа¶З а¶ђаІЗබථඌа¶∞ а¶Ца¶ђа¶∞а•§ а¶≠а¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶ЗаІЯа¶Њ а¶Єа¶ЃаІНа¶∞а¶Ња¶Я а¶Жа¶ђаІНа¶ђа¶Ња¶Єа¶ЙබаІНබගථаІЗа¶∞ බа¶∞බаІА а¶ХථаІНආаІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶ђаІНඃඕඌа¶∞ ඙а¶∞ප ඙ඌа¶З а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња•§
а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ња¶Х ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ХаІГටගа¶Х а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶єаІЯ ථඌ а¶ѓа¶Цථ, а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶ЬаІАа¶ђа¶њ ඁඌථаІБа¶Ј-а¶Ьථ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටග ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථ ථаІЗаІЯа•§ ටаІЗඁථа¶З а¶Па¶Х а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞ ‘а¶єаІБබаІБа¶Ѓ-බаІЗа¶У’а•§ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ ඐගඐඌයගටඌ, а¶ХаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞аІА а¶ЃаІЗаІЯаІЗа¶∞а¶Њ ‘а¶Ьа¶≤ а¶Ѓа¶Ња¶ЩටаІЗ’ а¶ђаІЗа¶∞аІЛаІЯа•§ а¶Па¶Х а¶ХаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞аІА а¶ЃаІЗаІЯаІЗа¶∞ ඁඌඕඌаІЯ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ша¶ЯаІЗ а¶Ьа¶≤ ඕඌа¶ХаІЗа•§ ටඌටаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЩаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ЪаІНа¶Ъа¶Њ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶єаІЯ ඙ඌථ, а¶ЄаІБ඙ඌа¶∞а¶њ а¶У а¶Ха¶ња¶ЫаІБ බаІБа¶∞аІНа¶ђа¶Ња•§ а¶Ша¶ЯаІЗа¶∞ а¶Ча¶ЊаІЯаІЗ а¶Єа¶ња¶БබаІБа¶∞аІЗа¶∞ ඙ඌа¶Ба¶Ъа¶Яа¶њ а¶ЂаІЛа¶Яа¶Њ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶Па¶З а¶ХаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞аІА а¶ХථаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ђаІЯа¶Є а¶є’ටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ ඪඌට ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Па¶Ча¶Ња¶∞аІЛ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа•§ ටඌа¶∞ ඁඌඕඌаІЯ а¶Ыඌටඌ а¶Іа¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶Па¶З а¶ЃаІЗаІЯаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єаІЯ ‘а¶Ша¶Яа¶Іа¶∞аІА а¶ХаІБа¶Зථඌ’а•§ а¶ХаІБа¶Зථඌа¶∞ ධඌථයඌට ඕඌа¶ХаІЗ а¶ђа¶∞а¶Ња¶≠аІЯ а¶ЃаІБබаІНа¶∞а¶ЊаІЯа•§ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ බප-а¶ђа¶Ња¶∞аІЛ а¶ЬථаІЗ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ බа¶≤а•§ а¶Па¶∞а¶Њ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶ШаІЛа¶∞аІЗ а¶Чඌථ а¶Ча¶Ња¶ЗටаІЗ а¶Ча¶Ња¶ЗටаІЗа•§ ටඌа¶∞а¶Њ а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНඕаІЗа¶∞ а¶ЙආаІЛථаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞а¶≤аІЗ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ а¶Ѓа¶єа¶≤а¶Ња¶∞а¶Њ а¶єаІБа¶≤аІБа¶ІаІНඐථග බගаІЯаІЗ ටඌබаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶Чට а¶ЬඌථඌаІЯа•§ а¶Ша¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђаІЗа¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶Ша¶Яа¶Іа¶Ња¶∞аІА а¶ХаІБа¶Зථඌа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞а¶£а¶Ња¶Ѓ а¶Х’а¶∞аІЗ а¶ЕථаІБа¶∞аІЛа¶І а¶Ха¶∞а¶ђаІЗ а¶Ша¶Я а¶ЙආаІЛථаІЗ ථඌඁගаІЯаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗа•§ а¶Па¶∞඙а¶∞ а¶Ша¶ЯаІЗ а¶У а¶ЫඌටඌаІЯ බаІЗа¶ђаІЗ а¶Ьа¶≤а•§
а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Ња¶∞а¶Њ а¶Па¶ХаІЗ а¶Е඙а¶∞а¶ХаІЗ а¶Єа¶ња¶БබаІБа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Ца¶њаІЯаІЗ බаІЗа¶ђаІЗа•§ а¶Па¶∞඙а¶∞ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЙආаІЛථаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶єа¶ђаІЗ а¶Ъа¶Ња¶ЈаІЗа¶∞ а¶Еа¶≠ගථаІЯа•§ а¶ШаІЬа¶Њ а¶ШаІЬа¶Њ а¶Ьа¶≤ а¶ЙආаІЛථаІЗ ඥаІЗа¶≤аІЗ а¶Хඌබඌ-а¶Хඌබඌ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶ђаІЗ а¶ЙආаІЛථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶ња•§ ටඌа¶∞඙а¶∞ බаІБа¶Ьථ а¶Еа¶≠ගථаІЯ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗ а¶Ъа¶Ња¶ЈаІЗа¶∞ а¶ђа¶≤බ а¶∞аІВ඙аІЗ, а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶ХаІГа¶Ја¶ХаІЗа¶∞ а¶Ъа¶∞ගටаІНа¶∞аІЗ а¶Еа¶≠ගථаІЯ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗа•§ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶∞а¶ЩаІНа¶Ч а¶∞а¶Єа¶ња¶Хටඌ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶Чඌථ а¶Ча¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶єаІЯа•§ ටඌа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ථаІГටаІНа¶ѓа•§
඙аІНа¶∞а¶Ња¶∞аІНඕථඌ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯ а¶ЗථаІНබаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ, а¶Ьа¶≤аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓа•§ ටඌа¶ХаІЗ ටаІБа¶ЈаІНа¶Я а¶Ха¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ѓаІМථ а¶ЙටаІНටаІЗа¶Ьа¶Х а¶Еа¶ЩаІНа¶Ча¶≠а¶ЩаІНа¶Ча¶њ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶ђаІЯа¶ЄаІНа¶Х ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ පаІБථаІЗа¶Ыа¶њ а¶ЕටаІАටаІЗ а¶Па¶З а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶∞ටа¶Ъа¶Ња¶∞ගථаІАа¶Ча¶£ а¶ђа¶ња¶ђа¶ЄаІНටаІНа¶∞ ඕඌа¶ХටаІЗа¶®а•§ а¶≤аІЛа¶Ха¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶Х පගපගа¶∞ а¶Ѓа¶ЬаІБඁබඌа¶∞ ටඌа¶Ба¶∞ ‘а¶ЙටаІНටа¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶Ъа¶∞ගට’ а¶ЧаІНа¶∞ථаІНඕаІЗа¶У ටаІЗඁථа¶Яа¶њ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Ња¶∞а¶Њ а¶ђа¶ЄаІНටаІНа¶∞а¶єаІАථඌ ඕа¶ХටаІЗථ а¶ђа¶≤аІЗа¶З а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗа¶∞ а¶∞ඌටаІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶ХаІЛථа¶У ඙аІБа¶∞аІБа¶Ј а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ а¶ђаІЗа¶∞аІБටаІЗ ඙ඌа¶∞ටаІЗථ а¶®а¶Ња•§ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь ඐග඲ඌථаІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶∞аІАටග а¶ХආаІЛа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ඙ඌа¶≤ථаІАаІЯ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Ча¶Ња¶БаІЯаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶ШаІБа¶∞аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Чථ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶Х’а¶∞аІЗ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Ња¶∞а¶Њ а¶ЕථаІНа¶Іа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Па¶Х а¶∞ඌටаІЗ а¶Й඙ඪаІНඕගට а¶єаІЯ ඁඌආаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗа•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЫаІЛа¶ЯаІНа¶Я а¶Ха¶≤а¶Ња¶Ча¶Ња¶Ы ඙аІЛа¶Бටඌ а¶єаІЯа•§ а¶ЄаІНථඌථ а¶Ха¶∞ඌථаІЛ а¶єаІЯ ටඌа¶ХаІЗа•§ а¶Па¶∞඙а¶∞ а¶ђа¶Ња¶∞аІЛа¶∞а¶Ха¶Ѓ පඪаІНа¶ѓ а¶Єа¶є а¶Ша¶Я а¶ЄаІНඕඌ඙ථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ ටඌа¶∞඙а¶∞ පаІБа¶∞аІБ а¶єаІЯ а¶ЧаІАට а¶У ථаІГටаІНа¶ѓа•§ යඌටටඌа¶≤а¶њ බගаІЯаІЗ а¶У а¶ХаІНඃඌථаІЗа¶ЄаІНටඌа¶∞а¶Њ а¶ђа¶Ња¶Ьа¶њаІЯаІЗ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Ња¶∞а¶Њ а¶Ха¶≤а¶Ња¶Ча¶Ња¶ЫаІЗа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶∞ගබගа¶ХаІЗ а¶Ша¶ња¶∞аІЗ а¶Па¶З ථаІГටаІНа¶ѓ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපථ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶∞ බаІЗඐටඌа¶∞ а¶ЙබаІНබаІЗපаІЗа•§ а¶Па¶З а¶ЧඌථаІЗ බаІЗඐටඌа¶ХаІЗ ටаІБа¶ЈаІНа¶Я а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶ѓаІЗඁථ ඕඌа¶ХаІЗ ටаІЗඁථа¶З ඕඌа¶ХаІЗ а¶ЕපаІНа¶≤аІАа¶≤ පඐаІНබаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶У а¶≠බаІНа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъа¶Ња¶∞а¶£ а¶Еа¶ѓаІЛа¶ЧаІНа¶ѓ а¶Ча¶Ња¶≤а¶Ња¶Ча¶Ња¶≤а•§ බаІЗඐටඌа¶ХаІЗ а¶Ца¶Ња¶∞ඌ඙ а¶Ца¶Ња¶∞ඌ඙ පඐаІНබаІЗ а¶ІаІАа¶ХаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЬඌථඌථаІЛ а¶єаІЯ а¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ ථඌ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ බඌаІЯаІА а¶Х’а¶∞аІЗа•§ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට පа¶∞аІАа¶∞ ඁථ බගаІЯаІЗ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Ња¶∞а¶Њ а¶Жඐඌයථ а¶Ьඌථඌථ ටඌа¶ХаІЗа•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶Жа¶ђаІЗබථаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶ХаІЗ а¶Єа¶ЃаІН඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Єа¶Б඙аІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Жа¶ХаІБа¶§а¶ња•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Ња¶∞а¶Њ а¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶∞ බаІЗඐටඌ а¶єаІБබаІБа¶Ѓ බаІЗа¶У-а¶ХаІЗ а¶ђа¶≤аІЗථ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ђа¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗ ඐගථගඁаІЯаІЗ а¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ බඌа¶Уа•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶ѓаІМථ а¶Жа¶ђаІЗබථ а¶Ж඙ඌටа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ බаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶Ха¶ЯаІБ а¶≤а¶Ња¶ЧටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ъа¶Ња¶ЈаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ, а¶ђаІЗа¶Ба¶ЪаІЗ ඕඌа¶Ха¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞ඌඕඁගа¶Х а¶∞ඪබаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Па¶З а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьа¶®а•§ а¶ПටаІЗ а¶ХаІЛථа¶У а¶≠ථගටඌ ථаІЗа¶За•§ а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЬаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Еа¶ЄаІНටගටаІНа¶ђаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞පаІНа¶®а•§ а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶≠ගටаІНටගа¶Х а¶Па¶З а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶ЊаІЯ а¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶∞ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьථ ඙аІНа¶∞පаІНථඌටаІАа¶§а•§ а¶ЄаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£аІЗа¶∞ ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞а¶§а¶Ња•§ ටඌа¶З а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Ња¶∞а¶Њ පа¶∞аІАа¶∞ ඁථ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට බගаІЯаІЗа¶З а¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶∞ බаІЗඐටඌа¶ХаІЗ а¶Жа¶єаІНඐඌථ а¶ЬඌථඌටаІЗа¶®а•§ ථගа¶∞аІНа¶ђа¶ња¶ШаІНථаІЗ පඣаІНа¶ѓ а¶ЙаІО඙ඌබථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Ъа¶Ња¶ЈаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІЗ ථа¶∞-ථඌа¶∞аІАа¶∞ а¶∞ටගа¶ХаІНа¶∞аІАаІЬа¶Њ а¶ЕථаІНඃටඁ а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞ а¶∞аІВ඙аІЗ а¶Ча¶£аІНа¶ѓ а¶єаІЯ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Ьථа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАටаІЗа¶За•§ а¶П а¶є’а¶≤ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Єа•§ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£аІЗа¶∞ а¶Ча¶≠аІАа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЙаІОа¶Єа¶Ња¶∞ගට а¶≠а¶ХаІНටග පаІНа¶∞බаІНа¶Іа¶Ња¶∞ ථගඐаІЗа¶¶а¶®а•§ ථඌа¶∞аІА ටаІЛ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටගа¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІАа¶Ха•§ а¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶∞ බаІЗඐටඌ ටаІБа¶ЈаІНа¶Я а¶є’а¶≤аІЗа¶З а¶≠аІВа¶Ѓа¶њ а¶Йа¶∞аІНа¶ђа¶∞ а¶єа¶ђаІЗа•§
‘а¶єаІБබаІБа¶Ѓ බаІЗа¶У’ а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІА а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථа¶Яа¶њ а¶Па¶Цථ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Ха¶Ѓ а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටගට а¶∞аІВ඙аІЗ а¶Па¶З а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞ ඙ඌа¶≤ථаІЗа¶∞ බаІГа¶ЈаІНа¶ЯඌථаІНට а¶Ха¶Цථа¶У а¶Ха¶Цථа¶У බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Ња¶∞а¶Њ а¶Па¶Цථ а¶Жа¶∞ ථа¶ЧаІНථ а¶єаІЯаІЗ а¶ѓаІЛа¶Ч බаІЗථ а¶®а¶Ња•§ ටඐаІЗ а¶єаІБබаІБа¶Ѓ බаІЗа¶У-а¶ХаІЗ ටаІБа¶ЈаІНа¶Я а¶Ха¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ѓаІМථ а¶ЙටаІНටаІЗа¶Ьа¶Х а¶Жа¶ЩаІНа¶Ча¶ња¶Ха¶Ња¶≠ගථаІЯ а¶Па¶З а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞аІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ХаІЛථа¶У а¶ХаІЛථа¶У а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ යආඌаІО а¶Ха¶Цථа¶У а¶ђа¶Њ а¶Па¶З а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ва¶ХаІНඣග඙аІНට а¶∞аІВ඙аІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ХаІБපඌථ ඙ඌа¶≤а¶Њ а¶ђа¶Њ බаІЛටඌа¶∞а¶Њ а¶°а¶Ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞ а¶Чඌථ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපගට а¶єаІЯ а¶Еа¶ђа¶Єа¶∞ ඐගථаІЛබථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓа•§ а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІА а¶ЖථаІБа¶ЈаІНආඌථගа¶Х ඙ඌа¶≤а¶Њ а¶ѓаІЗඁථ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ, а¶Єа¶Ња¶За¶Яа¶≤, а¶єаІБබаІБа¶Ѓ බаІЗа¶У а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНඕаІЗа¶∞ ඁඌථඪගа¶Х а¶∞аІВ඙аІЗ а¶ђа¶Њ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶ЬථаІЗа•§ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗ а¶Па¶З а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞а¶Єа¶ЃаІВа¶є ඙ඌа¶≤ථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ ටඌටаІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓаІЗа¶ХаІЗа¶∞ а¶Еа¶Вපа¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶Па¶З а¶ѓаІЛа¶Чබඌථ ඪටа¶Га¶ЈаІНа¶ЂаІВа¶∞аІНа¶§а•§
а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ ඙ඌа¶≤ථаІАаІЯ а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІВа¶є а¶ЕථаІЗа¶Ха¶Ња¶ВපаІЗа¶З ථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАа•§ а¶ЧаІАට-ඐඌබаІНа¶ѓ а¶Єа¶єа¶ѓаІЛа¶ЧаІЗ ථаІГටаІНа¶ѓа¶У а¶Па¶∞ а¶Еа¶Ва¶ґа•§ ටඌа¶З а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Єа¶ЃаІЯа¶З බа¶∞аІНපа¶ХаІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗ а¶ХаІЗа¶ђа¶≤ а¶Ѓа¶ЮаІНа¶ЪаІЗ а¶Й඙ඪаІНඕඌ඙ථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶Жа¶∞а¶У а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ђа¶єаІБа¶≤ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞ ‘а¶ђаІИа¶∞ඌටග ථඌа¶Ъ’а•§ а¶ЖබටаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶ђа¶њаІЯаІЗ а¶Й඙а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІЗ а¶ЧаІАට а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАа¶§а•§ а¶ђаІЗප а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶є’а¶≤ а¶ђаІИа¶∞ඌටග ථаІГටаІНа¶ѓ ථඌа¶ЯаІНа¶ѓ а¶Жа¶ЩаІНа¶Ча¶ња¶ХаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපගට а¶єаІЯа•§
а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶ђа¶њаІЯаІЗа¶∞ ථගа¶Ьа¶ЄаІНа¶ђ а¶Іа¶∞а¶£ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶Ѓа¶ЮаІНа¶ЪаІЗ ටаІЗඁථа¶З а¶ђа¶њаІЯаІЗа¶∞ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථ а¶Еа¶≠ගථаІЯаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ а¶Й඙ඪаІНඕඌ඙ගට а¶єаІЯа•§ а¶ЕටаІНඃථаІНට ථаІЯථඌа¶≠а¶ња¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶Па¶З ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗа¶ґа¶®а¶Ња•§ ටඌටаІЗ ථаІГටаІНа¶ѓ а¶У ථඌа¶ЯаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶Єа¶ЃаІГබаІНа¶Іа•§ а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶Ъа¶∞аІНа¶Ъа¶Ња¶∞ ථඐ ථඐ а¶∞аІВ඙ ථටаІБථ а¶ЙබаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Іа¶Ња¶∞а¶ЊаІЯ ඙аІНа¶∞ඐඌයගට а¶єаІЯа•§ ටඌ а¶ђа¶∞а¶Ђа¶Ча¶≤а¶Њ ථබаІАа¶∞ ඁටа¶З ඙аІНа¶∞ඐයඁඌථ а¶У ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථපаІАа¶≤а•§ ටඌа¶З ටඌටаІЗ а¶ХаІЛථа¶У පаІИа¶ђа¶Ња¶≤ а¶Чටගа¶∞аІЛа¶І а¶Ха¶∞аІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶≤аІЛа¶Ха¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞ а¶Єа¶Ња¶∞аІНඕа¶Хටඌ, පа¶ХаІНටග ටඌа¶З а¶Ъа¶ња¶∞а¶Ха¶Ња¶≤аІАа¶®а•§ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗඁගපаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ а¶ЄаІЗа•§
(а¶ХаІНа¶∞ඁප)
а¶Ыа¶ђа¶њ- බаІЛටඌа¶∞а¶Њ ඙ඌа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Жа¶Єа¶∞а•§ а¶Еа¶ЩаІНа¶Хථ- а¶∞аІБа¶Ѓа¶Њ බටаІНට
Have an account?
Login with your personal info to keep reading premium contents
You don't have an account?
Enter your personal details and start your reading journey with us
Design & Developed by: WikiIND
Maintained by: Ekhon Dooars Team