











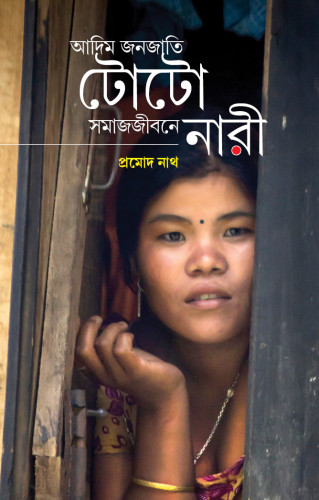



 පаІБа¶≠аІНа¶∞ а¶Ъа¶ЯаІНа¶ЯаІЛ඙ඌ඲аІНа¶ѓа¶ЊаІЯ
පаІБа¶≠аІНа¶∞ а¶Ъа¶ЯаІНа¶ЯаІЛ඙ඌ඲аІНа¶ѓа¶ЊаІЯ

а¶ХаІА යට ඃබග а¶ђаІИа¶ХаІБථаІНආ඙аІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞а¶Њ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶ЬබаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ ඁගටаІНа¶∞ටඌ а¶ЪаІБа¶ХаІНටගටаІЗ а¶ЖඐබаІНа¶І а¶єаІЯаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶£а¶§ යටаІЗථ බаІЗපаІАаІЯ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗ? а¶ѓаІЗඁථа¶Яа¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ХаІБа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞а•§ а¶ЕඐපаІНа¶ѓа¶њ а¶Іа¶Ња¶∞аІЗ а¶Па¶ђа¶В а¶≠а¶Ња¶∞аІЗ а¶ХаІБа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶ѓаІЗ а¶ђаІИа¶ХаІБථаІНආ඙аІБа¶∞аІЗа¶∞ ටаІБа¶≤ථඌаІЯ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Па¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤ ටඌ а¶ЕථඪаІНа¶ђаІАа¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ѓ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථටඌ а¶ШаІЛа¶Ја¶£а¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶Єа¶ЊаІЬаІЗ ඙ඌа¶Ба¶ЪපаІЛа¶∞а¶У а¶ђаІЗපග බаІЗපаІАаІЯ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђа¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶З а¶ѓаІЗ а¶Жа¶Ха¶Ња¶∞аІЗ а¶ђаІЬ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Пඁථ ථаІЯа•§ а¶ХаІНа¶ЈаІБබаІНа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓа¶У а¶Ха¶Ѓ а¶Ыа¶ња¶≤ ථඌ ථаІЗа¶єа¶ЊаІОа•§ а¶ЄаІБටа¶∞а¶Ња¶В а¶ЖаІЯටථаІЗ а¶ЫаІЛа¶Я а¶єа¶≤аІЗа¶У а¶ђаІИа¶ХаІБථаІНආ඙аІБа¶∞ යටаІЗа¶З ඙ඌа¶∞ට а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ බаІЗපаІАаІЯ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓа•§
а¶ХගථаІНටаІБ ටඌ а¶єаІЯ а¶®а¶ња•§
а¶Па¶З ථඌ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶Яа¶Ња¶З а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Яа¶Ња¶Йථ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶ња¶∞ ඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗ а¶Еටග а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ша¶Яа¶®а¶Ња•§ а¶ПඁථගටаІЗ බаІЗපаІАаІЯ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ ථගа¶∞ඌ඙ටаІНටඌа¶∞ බඌаІЯගටаІНа¶ђ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ьа¶∞а¶Њ ථගаІЯаІЗ ථаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ђа¶≤аІЗ බаІЗපаІАаІЯ а¶∞а¶Ња¶ЬඌබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ьа¶Ха¶∞аІНа¶Ѓ ඐගපаІЗа¶Ј а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶ПබаІЗа¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶Вපа¶З а¶Жа¶ЃаІЛබ-඙аІНа¶∞а¶ЃаІЛබ-පගа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Па¶ђа¶В а¶≤ථаІНධථаІЗ ඐඌථаІНа¶Іа¶ђаІАබаІЗа¶∞ ථගаІЯаІЗ а¶ЂаІВа¶∞аІНටග а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ЄаІНට ඕඌа¶ХටаІЗа¶®а•§ а¶ХаІЗа¶Й а¶ХаІЗа¶Й а¶ЕඐපаІНа¶ѓ ඪඌයගටаІНа¶ѓ-а¶Єа¶Ва¶ЧаІАට а¶Ъа¶∞аІНа¶Ъа¶ЊаІЯ ඁථаІЛථගඐаІЗප а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ටඐаІЗ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗа¶З а¶Ха¶Ѓа¶ђаІЗපග ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗ а¶Жа¶ІаІБථගа¶Х ඙ඌපаІНа¶ЪඌටаІНа¶ѓ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶ђа¶ња¶ЄаІНටඌа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌථа¶У а¶ЄаІНඕඌ඙ථ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶З а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶ђа¶ња¶Вප පටа¶ХаІЗа¶∞ а¶ЧаІЛаІЬа¶ЊаІЯ а¶ЬаІЗа¶ЧаІЗ а¶Уආඌ а¶Па¶Х а¶ЙටаІНටаІЗа¶Ьථඌ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Еа¶ІаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ ඕаІЗа¶ХаІЗ බаІВа¶∞аІЗ ඕඌа¶ХටаІЗ а¶ђа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶У а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§
а¶ЄаІЗа¶З а¶ЙටаІНටаІЗа¶Ьථඌ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Еа¶ІаІНа¶ѓа¶ЊаІЯа¶Яа¶њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЄаІНඐබаІЗපаІА а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤а¶®а•§
а¶ђа¶ЄаІНටаІБටа¶Г බаІЗපаІАаІЯ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶њ ටඌබаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶З а¶Іа¶∞ථаІЗа¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞ට а¶®а¶Ња•§ а¶ѓа¶Њ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ь පඌඪථаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІЛа¶ІаІА ටඌ а¶Ыа¶ња¶≤ බаІЗපаІАаІЯ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓа¶ЧаІБа¶≤ගටаІЗ ථගඣගබаІНа¶Іа•§ ආගа¶Х а¶Па¶З а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗа¶З а¶ХаІБа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ ඁථ බගа¶≤аІЗа¶У а¶ђа¶ЮаІНа¶Ъගට а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Па¶З а¶ЙටаІНටаІЗа¶Ьථඌ ඕаІЗа¶ХаІЗа•§ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶Ха¶≤а¶ХඌටඌаІЯ а¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථටඌ а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ѓаІБа¶ХаІНට а¶≤аІЛа¶Ха¶ЬථබаІЗа¶∞ а¶ЙаІОа¶Єа¶Ња¶є а¶ѓаІЛа¶ЧඌටаІЗ ඙ඌа¶∞ටаІЗථ, а¶ХගථаІНටаІБ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶За¶Єа¶ђ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Еа¶∞аІНඕ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶∞а¶Ња¶ЬටаІНа¶ђ а¶єа¶Ња¶∞а¶Ња¶®а•§
а¶ђаІИа¶ХаІБථаІНආ඙аІБа¶∞ ඃබග බаІЗපаІАаІЯ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ѓаІЗට а¶Жа¶∞ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶њ а¶Яа¶Ња¶Йථ ඃබග යට а¶ЄаІЗа¶З а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ь඲ඌථаІА ටඐаІЗ ටඌа¶∞ а¶ЪаІЗа¶єа¶Ња¶∞а¶Њ යට а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶∞а¶Ха¶Ѓа•§ а¶ђа¶ња¶Вප පටа¶ХаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶≠а¶Ња¶ЧаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶ЄаІЗ а¶Яа¶Ња¶Йථ а¶єаІЯаІЗ а¶Йආට ථඌ а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Х а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНඃටඁ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞а•§ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ ඙аІБа¶ХаІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞аІЗ а¶ЧаІЬаІЗ а¶Йආට ථඌ ඪපඪаІНටаІНа¶∞ а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථаІЗа¶∞ а¶ЄаІНඐ඙аІНථ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓаІБа¶ђа¶ХබаІЗа¶∞ а¶Жа¶ЦаІЬа¶Ња•§ а¶ЪගටаІНටа¶∞а¶ЮаІНа¶Ьථ බඌපаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ЧаІЬаІЗ а¶Йආට ථඌ а¶Яа¶Ња¶ЙථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Ха•§ ඙аІНа¶∞බаІЗප а¶Ха¶Ва¶ЧаІНа¶∞аІЗа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Єа¶≠ඌ඙ටග а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶≤аІЛа¶Ѓа¶Ца¶ЊаІЬа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ђа¶ХаІНටඐаІНа¶ѓ а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗථ ථඌ а¶ЄаІБа¶≠а¶Ња¶Ја¶ЪථаІНබаІНа¶∞а•§ а¶Ха¶∞а¶≤а¶Њ ථබаІА а¶≤а¶Ња¶ЧаІЛаІЯ а¶ђа¶ња¶∞а¶Ња¶Я а¶ЃаІЯබඌථаІЗ а¶Єа¶≠а¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗථ ථඌ а¶ЃаІЛයථබඌඪ а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶ЪථаІНබ а¶ЧඌථаІНа¶ІаІАа•§
а¶Жа¶∞ а¶Ьа¶ЧබаІАථаІНබаІНа¶∞බаІЗа¶ђ а¶∞а¶ЊаІЯа¶Хටа¶У а¶єа¶Ња¶≤ а¶Іа¶∞ටаІЗථ ථඌ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Њ а¶Ха¶Ва¶ЧаІНа¶∞аІЗа¶ЄаІЗа¶∞а•§
а¶Па¶З а¶ѓаІЗ ථаІЗа¶Яа¶ња¶≠ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶Я ථඌ а¶єаІЯаІЗ а¶ЙආටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶Њ, а¶Па¶З а¶ѓаІЗ а¶ђаІИа¶ХаІБථаІНආ඙аІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬඌබаІЗа¶∞ а¶Ьඁගබඌа¶∞аІЗ ඙а¶∞а¶ња¶£а¶§ а¶єа¶УаІЯа¶Њ --- а¶Па¶Яа¶Ња¶З а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Яа¶Ња¶Йථ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶ња¶∞ а¶Па¶Х а¶ђа¶ња¶∞а¶Ња¶Я а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶Ча•§ а¶Ъа¶Њ පගа¶≤аІН඙аІЗа¶∞ а¶Жа¶ђа¶ња¶∞аІНа¶≠а¶Ња¶ђа¶ХаІЗ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Чට පටа¶ХаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶≠а¶Ња¶Ч ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶Яа¶Ња¶ЙථаІЗа¶∞ а¶Еа¶∞аІНඕථаІАටග а¶Єа¶ЃаІГබаІНа¶І а¶єа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤а•§ පගа¶≤аІН඙඙ටගа¶∞а¶Њ, а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶ЊаІЯаІАа¶∞а¶Њ, පගа¶ХаІНඣගට а¶Ѓа¶ІаІНඃඐගටаІНටа¶∞а¶Њ а¶Ха¶ЦථаІЛ ඙аІНа¶∞а¶ХඌපаІНа¶ѓаІЗ а¶Ха¶ЦථаІЛ а¶ЧаІЛ඙ථаІЗ а¶Яа¶Ња¶ЙථаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Х а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶ХඌථаІНа¶°аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ѓаІЛа¶Ьа¶Х а¶єаІЯаІЗ а¶Йආа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ѓаІБа¶ђа¶ХබаІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗ а¶ЦаІБа¶≤аІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤ බаІЗපඪаІЗа¶ђа¶Ња¶∞ ථටаІБථ බගа¶ЧථаІНа¶§а•§
а¶ЧаІЛаІЬа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶Яа¶Ња¶ЙථаІЗа¶∞ බаІБа¶ЯаІЛ а¶≠а¶Ња¶Ча•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶≠а¶Ња¶Ч а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІАаІЯа•§ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථ ඙аІЛа¶ЄаІНа¶Яඌ඙ගඪаІЗа¶∞ а¶ЃаІЛаІЬ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ѓаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ බа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£аІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ ටඌа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Б බගа¶Х а¶Іа¶∞аІЗ а¶Ха¶∞а¶≤а¶Њ ථබаІА а¶ђа¶∞а¶Ња¶ђа¶∞ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶ЬබаІЗа¶∞ а¶ђа¶Єа¶§а¶ња•§ а¶ЄаІЗ а¶ѓаІЗථ а¶ЫаІЛа¶ЯаІНа¶Я а¶Па¶Х а¶ЯаІБа¶Ха¶∞аІЛ а¶ђа¶ња¶≤аІЗа¶§а•§ а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ђ, а¶ШаІЛаІЬබаІМаІЬаІЗа¶∞ ඁඌආ, а¶Ыа¶ња¶Ѓа¶Ыа¶Ња¶Ѓ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶Ша¶∞, а¶ЙබаІНඃඌථ а¶Жа¶∞аІЛ а¶Хට а¶ХаІА! а¶ђа¶ња¶≤аІЗටаІЗа¶∞ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЯаІБа¶Ха¶∞аІЛа¶Яа¶њ а¶Ыа¶ња¶≤ බаІЗපගаІЯ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ථගඣගබаІНа¶Іа•§ а¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ча¶Ња¶ЫаІЗа¶∞ а¶Ьа¶ЩаІНа¶Ча¶≤аІЗа¶∞ а¶Ђа¶Ња¶Ба¶Х බගаІЯаІЗ а¶≠аІЗа¶ЄаІЗ а¶Йආට ටඌа¶∞ а¶ЪаІЗа¶єа¶Ња¶∞а¶Ња•§ а¶Яа¶Ња¶Йථ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ха¶ња¶В а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ а¶Ша¶Ња¶Я ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶Ѓа¶Ња¶≤඙ටаІНа¶∞ а¶Єа¶єа¶ЬаІЗ ඐයථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶∞аІЗа¶≤ а¶≤а¶Ња¶За¶®а•§
а¶Па¶З ‘а¶ђа¶ња¶≤аІЗට’-а¶Па¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ а¶ђа¶Ња¶Ха¶њ а¶Яа¶Ња¶Йа¶®а•§ ‘ටа¶∞а¶Ња¶З а¶ЙаІОа¶∞а¶Ња¶З’ ථඌඁа¶Х а¶ЄаІНа¶ђа¶∞а¶Ъගට а¶Й඙ථаІНа¶ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶ЯаІБа¶Цඌථග а¶Па¶З ඙аІНа¶∞а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ටаІБа¶≤аІЗ බගа¶≤аІЗ а¶Жපඌ а¶Ха¶∞а¶њ а¶Ж඙ථඌа¶∞а¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗථ а¶®а¶Ња•§
“а¶Й඙аІЗථ а¶Ча¶ЊаІЯаІЗ а¶Ъඌබа¶∞ а¶ЬаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Хබඁටа¶≤а¶Ња¶∞ බගа¶ХаІЗа•§ පයа¶∞а¶Яа¶ЊаІЯ ඙ඌа¶Ха¶Њ а¶Жа¶∞ а¶ђаІЬаІЛ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶Ша¶∞ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ථаІЗа¶За•§ а¶ђаІЗපගа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ча¶З а¶ЯගථаІЗа¶∞ а¶ЦаІЬаІЗа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶≤ а¶Ыа¶Ња¶Йථග බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶ХඌආаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња•§ а¶Па¶∞а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ѓаІЗ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶∞ බаІЗаІЯа¶Ња¶≤ ඙ඌа¶Ха¶Њ а¶ђа¶≤аІЗ ඁථаІЗ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, ටඌ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶ђа¶Ња¶БපаІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶Єа¶ња¶ЃаІЗථаІНа¶ЯаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶≤аІЗ඙ а¶≤а¶Ња¶Ча¶Ња¶®а•§ а¶Й඙аІЗථаІЗа¶∞ ඁථаІЗ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ѓаІЗ а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З а¶ЄаІЗ ඙ඌඐаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶ЄаІНටаІЗ а¶Жа¶ЄаІНටаІЗ а¶ђаІБа¶ЭаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Ѓа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶∞ ඁටаІЗ а¶ђаІЬаІЛ а¶ЬаІЛа¶∞ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ ඙а¶Ба¶Ъගප а¶≤аІЛа¶Х ඕඌа¶ХаІЗ පයа¶∞аІЗа•§ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ-බаІАа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІЗ а¶≤аІЛа¶Ха¶ЬථаІЗа¶∞ а¶ђаІЗප а¶ЙаІОа¶Єа¶Ња¶єа•§ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Њ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤ ඐඌබ බගа¶≤аІЗа¶У а¶ђаІЗа¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІА а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗа¶∞ а¶Еа¶≠а¶Ња¶ђ ථаІЗа¶За•§ а¶Й඙аІЗථ а¶ѓаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ බගаІЯаІЗ а¶єа¶Ња¶Ба¶Яа¶Ыа¶ња¶≤ ටඌа¶∞ බаІБ –඙ඌපаІЗ а¶ђаІЗප а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Ва¶Ха•§ а¶ЙටаІНටа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ බа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£аІЗ ඕඌථඌа¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶Па¶З а¶ЫаІЛа¶ЯаІНа¶Я а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌа¶Яа¶ња¶ХаІЗ පයа¶∞аІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶ХаІЗа¶∞ а¶°а¶Ња¶ХаІЗ ‘а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶За¶≠ а¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶Я’ а¶ђа¶≤аІЗа•§ а¶≤а¶Ња¶≤ а¶За¶ЯаІЗа¶∞ ඙а¶∞ ඙а¶∞ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ බаІЛටа¶≤а¶Њ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶єа¶≤аІЛ а¶Жа¶∞аІНа¶ѓ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Ва¶ХаІЗа¶∞ а¶≠а¶ђа¶®а•§ а¶Й඙аІЗථ а¶ЄаІЗа¶З а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌаІЯ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ъа¶ХаІНа¶Ха¶∞ а¶ХаІЗа¶ЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Хබඁටа¶≤а¶Ња¶∞ බගа¶ХаІЗа•§ පаІЛа¶≠а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶∞а¶ђаІАථаІНබаІНа¶∞ථඌඕаІЗа¶∞ а¶ђа¶З а¶ХගථටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§
“а¶Й඙аІЗථ а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗ а¶ЦаІБа¶ђ පයа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Ха¶Ѓ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶З а¶ђаІЗаІЬа¶Њ а¶ђа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАа¶∞ බගаІЯаІЗ а¶ШаІЗа¶∞а¶Ња•§ а¶Па¶Х а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶∞аІЗа¶Х а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌаІЯ а¶ѓаІЗටаІЗ පа¶∞аІНа¶Яа¶Ха¶Ња¶Я а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶Па¶∞ а¶Уа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ а¶ЙආаІЛථ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Ња¶Яа¶Ња¶З а¶Еа¶≤а¶ња¶Цගට ථගаІЯа¶Ѓа•§ а¶ХаІЗа¶Й а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а¶Ња•§ а¶ЧаІЛаІЬඌටаІЗ а¶Й඙аІЗථаІЗа¶∞ а¶Еа¶ЄаІНа¶ђа¶ЄаІНටග යට, а¶Па¶Цථ а¶ЄаІЗ а¶Цඌථගа¶Ха¶Яа¶Њ а¶∞඙аІНට а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ьගථගඪа¶У а¶ЄаІЗ а¶∞඙аІНට а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ а¶ђа¶ЩаІНа¶Ха¶ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ы ඕаІЗа¶ХаІЗа•§ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶єа¶≤аІЛ බаІЗපග а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња•§ а¶Па¶З а¶≠аІВа¶ЦථаІНа¶°аІЗа¶∞ а¶Жබග ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞а¶Њ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗа¶З а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІАа•§ а¶Па¶БබаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶Й඙аІЗථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶ЧаІЛаІЬඌටаІЗ බаІБа¶∞аІНа¶ђаІЛа¶ІаІНа¶ѓ ඁථаІЗ а¶єа¶§а•§ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ а¶Жа¶ЄаІЗ-඙ඌපаІЗ а¶Ча¶Њ-а¶Ча¶ЮаІНа¶ЬаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ХаІЛථаІЛ а¶Ѓа¶ња¶≤ ථаІЗа¶З ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞а•§ а¶Еඕа¶Ъ а¶Ѓа¶Ња¶Ѓа¶Њ а¶Пඁථ а¶Ха¶њ පаІЛа¶≠а¶Ња¶У බගඐаІНа¶ѓа¶њ а¶ђа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶Па¶З а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња•§ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶њ පයа¶∞ а¶ЧаІЬаІЗ а¶Уආඌа¶∞ ඙а¶∞ ථඌථඌ ඙аІНа¶∞ඌථаІНට ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶≠а¶Ња¶ЧаІНඃඌථаІНа¶ђаІЗа¶ЈаІА ඁඌථаІБа¶Ј а¶Па¶ЄаІЗ а¶≠а¶њаІЬ а¶Ьа¶Ѓа¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Па¶ЦඌථаІЗа•§ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІАබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Па¶∞а¶Њ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶≠а¶Ња¶Яа¶њаІЯа¶Њ а¶ђа¶Њ а¶≠а¶Ња¶Яа¶њ බаІЗපаІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶Ха•§
“а¶Хබඁටа¶≤а¶ЊаІЯ а¶ЖඪටаІЗ а¶ЖඪටаІЗ а¶ЕථаІНа¶Іа¶Ха¶Ња¶∞ ථаІЗа¶ЃаІЗ а¶Па¶≤аІЛа•§ а¶ђа¶З-а¶Па¶∞ බаІЛа¶Хඌථබඌа¶∞ ඙аІЗа¶ЯаІНа¶∞аІЛа¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛа¶Яа¶Њ а¶ЬаІНа¶ђа¶Ња¶≤а¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶ЭаІБа¶Ба¶ХаІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶∞ බගа¶ХаІЗ ටඌа¶Ха¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Й඙аІЗථ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶Яа¶Ња¶ХаІЗ а¶ЪගථටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶≤а•§ а¶ХаІЯаІЗа¶Х බගථ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶ђа¶ЩаІНа¶Ха¶ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Ша¶Яа¶Ха¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ ඙аІЗа¶Ыථ බගаІЯаІЗ а¶ђаІЗа¶ЧаІБථа¶Яа¶Ња¶∞а¶ња¶∞ බගа¶ХаІЗ පа¶∞аІНа¶Яа¶Ха¶Ња¶ЯаІЗ а¶єа¶Ња¶Ба¶Яа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Па¶З а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶Яа¶Њ а¶ђа¶ЩаІНа¶Ха¶ња¶Ѓа¶ХаІЗ බඌа¶БаІЬ а¶Ха¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶ХаІА а¶Ьඌථග а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Й඙аІЗථ ඙а¶∞аІЗ а¶ЬаІЗථаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶Яа¶Ња¶∞ ථඌඁ а¶Ѓа¶єаІЗථаІНබаІНа¶∞а•§”
පа¶∞ටаІЗ ඙аІБа¶ЬаІЛа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ а¶Яа¶Ња¶Йථ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶≤а¶Ња¶ЗථаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ බඌа¶БаІЬඌට а¶єа¶∞аІЗа¶Х а¶Ѓа¶Ња¶≤ а¶ђаІЛа¶Эа¶Ња¶З а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶∞аІЗа¶≤аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞а¶Ња•§ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Ња¶З බаІЛа¶Ха¶Ња¶®а•§ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЄаІЗа¶∞а¶Њ а¶Ьගථගඪ а¶ђа¶Ња¶Ыа¶Ња¶З а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЄаІЗа¶ЬаІЗ а¶Жඪට а¶ЄаІЗа¶З а¶∞аІЗа¶≤බаІЛа¶Ха¶Ња¶®а•§ а¶Яа¶Ња¶ЙථаІЗа¶∞ ඁඌථаІБа¶Ј а¶≠а¶њаІЬ а¶Ьඁඌට а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථаІЗ ඙аІБа¶ЬаІЛа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓа•§ а¶ЄаІЗ а¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶Ъа¶Њ а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗа¶∞ පаІНа¶∞а¶Ѓа¶ња¶ХබаІЗа¶∞ а¶ђаІЗටථ а¶Ыа¶ња¶≤ ටаІБа¶≤ථඌаІЯ а¶ђаІЗප а¶≠а¶Ња¶≤аІЛа•§ ඙аІБа¶ЬаІЛа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶ђа¶ЊаІЬටග а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ ඙аІЗаІЯаІЗ ටඌа¶Ба¶∞а¶Ња¶У а¶≠а¶њаІЬ а¶ЬඁඌටаІЗථ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථаІЗа¶∞ ප඙ගа¶В а¶Ѓа¶≤-а¶Па•§ බаІВа¶∞-බаІВа¶∞ඌථаІНට ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЖඪටаІЗථ ඐගටаІНටපඌа¶≤аІА ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞а¶Ња•§
පаІЗаІЯа¶Ња¶≤බඌ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Па¶Х а¶∞ඌටаІНටගа¶∞ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶њ а¶Яа¶Ња¶ЙථаІЗ ඙аІМа¶Ба¶Ыа¶ђа¶Ња¶∞ а¶∞аІЗа¶≤ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶ЄаІЗ а¶Ха¶Ња¶≤аІЗа¶∞ ථගа¶∞а¶ња¶ЦаІЗ а¶ЙථаІНථට а¶ѓаІЛа¶Ча¶Ња¶ѓаІЛа¶ЧаІЗа¶∞ බаІГа¶ЈаІНа¶ЯඌථаІНа¶§а•§ а¶Па¶Яа¶Ња¶З а¶Ыа¶ња¶≤ බඌа¶∞аІНа¶Ьа¶ња¶≤а¶ња¶В а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶™а¶•а•§ а¶Па¶З а¶∞аІЗа¶≤ а¶ѓаІЛа¶Ча¶Ња¶ѓаІЛа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗа¶З а¶Яа¶Ња¶Йථ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶њ а¶єаІЯаІЗ а¶ЙආаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ ඐගපаІЗа¶Ј а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£а•§ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌ ඕаІЗа¶ХаІЗ බඌа¶∞аІНа¶Ьа¶ња¶≤а¶ња¶В-а¶Па¶∞ ඙ඕ а¶Іа¶∞а¶Њ ඃඌටаІНа¶∞аІАа¶∞а¶Њ а¶≠аІЛа¶∞ а¶Ыа¶Яа¶ЊаІЯ а¶Па¶З а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථаІЗ ථаІЗа¶ЃаІЗ а¶Ъа¶Њ ඙ඌථ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶®а•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЙаІОа¶ХаІГа¶ЈаІНа¶Я බඌа¶∞аІНа¶Ьа¶ња¶≤а¶ња¶В а¶Ъа¶ЊаІЯаІЗа¶∞ а¶ЄаІБа¶ђа¶Ња¶ЄаІЗ а¶≠а¶∞аІЗ а¶Йආට а¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶ґа¶®а•§ ටа¶ЦථаІЛ а¶Єа¶ња¶Яа¶ња¶Єа¶њ а¶Жа¶ЄаІЗ а¶®а¶ња•§
а¶Жа¶∞аІЗа¶Х බගථ а¶Па¶З а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථ а¶≠а¶∞аІЗ а¶ЙආаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ පаІЛа¶Ха¶Ња¶∞аІНට ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶≠аІАаІЬаІЗа•§ බඌа¶∞аІНа¶Ьа¶ња¶≤а¶ња¶В-а¶П а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗථ බаІЗපඐථаІНа¶ІаІБ а¶ЪගටаІНටа¶∞а¶ЮаІНа¶Ьථ а¶¶а¶Ња¶Єа•§ а¶Яа¶Ња¶ЙථаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Х а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ѓа¶∞බаІЗа¶є а¶ЄаІЗබගථ а¶Яа¶Ња¶ЙථаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථаІЗ а¶ПථаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ ඃඌටаІЗ а¶Яа¶Ња¶ЙථඐඌඪаІА පаІЗа¶Ј ථඁඪаІНа¶Ха¶Ња¶∞а¶Яа¶њ а¶ЬඌථඌටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§
а¶Яа¶Ња¶ЙථаІЗа¶∞ а¶ЃаІВа¶≤ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌа¶∞ ථඌඁ а¶Жа¶ЬаІЛ а¶°а¶ња¶ђа¶ња¶Єа¶њ а¶∞аІЛа¶° а¶ђа¶Њ බаІЗපඐථаІНа¶ІаІБ а¶ЪගටаІНටа¶∞а¶ЮаІНа¶Ьථ а¶∞аІЛа¶°а•§
(а¶Ъа¶≤а¶ђаІЗ)
Have an account?
Login with your personal info to keep reading premium contents
You don't have an account?
Enter your personal details and start your reading journey with us
Design & Developed by: WikiIND
Maintained by: Ekhon Dooars Team