










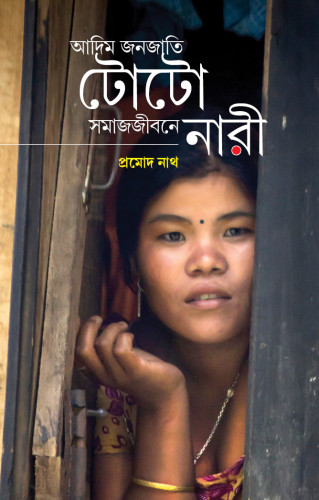



 সব্যসাচী দত্ত
সব্যসাচী দত্ত

উত্তরবঙ্গের সম্পূর্ণ জনপদে প্রাচীন সাংস্কৃতিক ধারা বহমান। ইতিহাস সেই সাংস্কৃতিক ধারাকে করেছে সমৃদ্ধ। প্রকৃতি কেন্দ্রিক আচার ও সংস্কৃতি এই অঞ্চলকে করেছে ভারতের অন্য জনপদ থেকে স্বতন্ত্র পরিচয়ের। পাহাড়-অরণ্য-সমতল-নদী; অর্থাৎ প্রাকৃতিক বৈচিত্র সংস্কৃতিকেও বৈচিত্রপূর্ণ করেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জনজাতী তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই বিদ্যমান। উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৈচিত্রপূর্ণ জেলা জলপাইগুড়ি। প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র যেন তাকে ‘ছোট ভারতবর্ষ’-এর রূপ দিয়েছে। হিমালয় পর্বত, পর্বতের সানুদেশের তরাই-অরণ্য অঞ্চল, চা-বাগিচা ও ছোট-বড় অসংখ্য নদী প্রাকৃতিক রূপকে করেছে মোহময়ী। এই অঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতি ও উপজাতি সমূহ নিজস্ব সংস্কৃতি-আচার-সমৃদ্ধ। নদী ও কৃষিকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে জলপাইগুড়িতে।
জলপাইগুড়িতে প্রবাহিত অধিকাংশ নদীসমূহ বরফ গলা জলে পুষ্ট। তাই সারাবছর নদীগুলিতে জল থাকে। বর্ষার সময় অনেক নদীই তার দু’পারের অঞ্চলকে প্লাবিত করে দেয়। তিস্তা-রায়ডাক-জলঢাকা-মূর্তি ইত্যাদি বিখ্যাত নদী যেমন আছে তেমনই খান পঞ্চাশেক করলা-ঝুমুর-জরদা-র মত অনামী নদী জলপাইগুড়ির মাটিকে করেছে উর্বর। এছাড়াও আছে অসংখ্য শাখানদী-উপনদী-খাল-বিল-নালা-বিল-দীঘি-পুকুর। তাই এদের পাশে পিঠে যে জমি-জিরেত আছে তাতে আছে সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ ও সবুজের সমারোহ। যা চোখকে শান্তি দেয়, মনকে দেয় মিঠে অনুভূতি। এত জলধারা সঙ্গে বৃষ্টি ও অরণ্যের সবুজের কারণে আবহাওয়ায় অনেক ভেজা ভাব। তাই এখানকার সংস্কৃতিও এত রসসিক্ত।
জলপাইগুড়ির সংস্কৃতিতে রাজবংশী প্রভাব সুষ্পষ্ট। আছেন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ভাটিয়া বা বাঙাল। আছেন রাভা, মেচ, তামাং, সাঁওতাল, মুন্ডা, কোরা তাঁদের নিজের সংস্কৃতি সাথে ক’রে। হিন্দু-মুসলিম-খ্রীষ্টান-বৌদ্ধ-জৈন বহন ক’রে চলেছেন নিজেদের সংস্কৃতি। একদা গভীর অরণ্যের এ অঞ্চলে বিভিন্ন ধারার মানুষ এসে বসবাস করেছেন। আবার চলেও গেছেন। আমাদের এই লেখায় উত্তরবঙ্গের ইতিহাস আলোচনার সময় আমরা দেখেছি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ঘটেছে অনেক ঘটনা। তার প্রভাবও রয়ে গেছে। মহাভারতে আমরা এই অঞ্চলের উল্লেখ পাই। করতোয়া নদী অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী।
কোনও অঞ্চলের স্থাননাম সেখানকার পরিচয় বহন করে। তাতে স্থানমাহাত্ম্যও প্রকাশিত হয়। কেন এ অঞ্চলের নাম হ’ল জলপাইগুড়ি সে সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে অনেক। বিতর্কও আছে স্বাভাবিক ভাবেই। জলপাইগুড়ি গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে— ‘Jalpaiguri is said to have derived its name from the olive trees (Jalpai in Bengali) which grows in the town and were seen even in 1900’. এইটি যথার্থ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় এবং অনেক ঐতিহাসিক বিষয়টি মানতে চাননি বলা বাহুল্য। সেকারণে আবার বলা হয়েছে— ‘The name might as well be associated with Jalpes, the presiding deity (Siva) of the entire region who had been in the minds of men here from time immemorial’. ফলে জল্পেশ থেকেও এই নাম আসতে পারে। কিন্তু এর স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন সময়ে Julpaigoree, Julpaigorie ইত্যাদি নাম কেউ কেউ ব্যবহার করেছেন। যার সঙ্গে জল্পেশ বা জলপাই কোনওটিরই সম্পর্ক নেই।
জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিশ্বসিংহ ভাই শিশ্বসিংহ-কে বৈকুন্ঠপুরের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান এবং তাঁর উপাধি হয় রায়কত। এই বৈকুন্ঠপুরে নাম হয় জলপাইগুড়ি। এবিষয়ে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও সমাজকর্মী পরিতোষ দত্ত লিখেছেন, ‘ইতিহাসের পৃষ্ঠা একটু উল্টানো দরকার। বৈকুন্ঠপুরাধিপতি দুর্গদেব (১৭২৮-১৭৯৩ খ্রিঃ) ভূটানের দেবরাজের বিরুদ্ধে ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহার রাজের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হ’লে ভূটানকে খুশি করার জন্য বৈকুন্ঠপুরের তিস্তার পূর্বপারের বহু অংশ দিয়ে দেয়। ফালাকাটা, জল্পেশ সহ বৈকুণ্ঠপুরের সাতাত্তরটি মৌজা দেবরাজকে দেওয়া হয়। রায়কতদের দেবস্থান জল্পেশের শোক ভুলতেই ওইনামের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে অপর পারে জলপাইগুড়ির পত্তন হয় বলে আমাদের অনুমান। এটা নিছক অনুমান মাত্র— তেমন তথ্য সমৃদ্ধ এ দাবি রাখা যাচ্ছে না।’
জলপাইগুড়ির উত্তরে রয়েছে নেপাল ভূটান চিন তিব্বত। যাদের সাংস্কৃতিক প্রভাব জলপাইগুড়িতে পড়েছে। এ বিষয়ে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর লেখায় তিব্বত, নেপাল ও ভূটানের প্রত্যক্ষ প্রভাব জলপাইগুড়িতে লক্ষ্য করা যায় বলে উল্লেখ করেছেন। বহু প্রাচীন কাল থেকেই শিবরাত্রী উপলক্ষ্যে জল্পেশে যে মেলা হয় তাতে নেপাল, ভূটান, তিব্বত থেকে ঘোড়া, কুকুর ও বিশেষত কম্বল ও উলের পোশাক আসতো। এই ঘটনার সঙ্গে জলপাইগুড়ি নামের উৎপত্তির বিষয়টি জড়িত আছে বলে পরিতোষ দত্ত উল্লেখ করেছেন। তিনি জলপাইগুড়ি নামটি বিশ্লেষন করেছেন এভাবে—
Jelepegori
JE-LE—বিনিময় কেন্দ্র।
PE—উল বা কম্বল বা গরম বস্ত্র।
GO—দরজা বা দুয়ার।
RI—পাহাড়।
অর্থাৎ পাহাড় থেকে যে পথে বা যেখানে গরম জামাকাপড় বিক্রির জন্য আসতো। এই Jelepegori ধীরে ধীরে Jalpaiguri-তে রূপান্তরিত হয়। এই বিষয়টি অনেক ঐতিহাসিক বিশ্বাসযোগ্য মনে করেছেন। আবার ‘জল্পেশ্বর’, ‘জল্পীশ’ বা ‘জল্পেশ’ জলপাইগুড়ি নামের পরিচিতি ঘটার ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা অস্বীকার করা যায় না। তা সে যেভাবেই জলপাইগুড়ি নামের উৎপত্তি হোক না কেন জেলাটি প্রাচীন ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। সংস্কৃতি ও বৈচিত্রে পূর্ণ এই জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবার ফিরে দেখা যাক।
জলপাইগুড়ির ইতিহাসের সঙ্গে কোচবিহারের সম্পর্ক খুব কাছের। কোচবিহারের প্রথম শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান রাজা বিশ্বসিংহ কোচ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এতটাই ঘটিয়ে ফেলেছিলেন যে তা একজায়গায় বসে সুষ্ঠুভাবে পরিচলনা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাই রাজ্যকে ভাগ ক’রে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশ্বসিংহ তাঁর ছোটভাই শিশ্বসিংহ-কে ‘রায়কত’ উপাধি দিয়ে বৈকুন্ঠপুর পাঠিয়ে দিলেন। এটা ষোড়শ শতকের প্রথম দিকের ঘটনা। যে স্থানে এই বংশের রাজপাট প্রথমে স্থাপন করা হয়েছিল তা বর্তমানে জলপাইগুড়ি শহরের উত্তরে রংধামালি ছাড়িয়ে আরও দশ মাইল উত্তরে। যার উত্তরে ভূটান, পূর্বে তিস্তা, পশ্চিমে গভীর অরণ্য, মহানন্দা নদী ও দক্ষিণে কোচবিহার। বিশ্বসিংহ ভাইকে একটি অঞ্চলের দায়িত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু তার সীমানা নির্দিষ্ট ক’রে দেননি। কারণ মূল শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা হ’ত কোচবিহার থেকেই। একই বংশের দু’টি ধারা বয়ে চলত পাশাপাশি। তাঁরা সুখে-দুঃখে একসঙ্গে চলতেন দীর্ঘকাল। কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের শেষদিকে গৃহবিবাদ, ষঢ়যন্ত্র ও মুঘলদের আক্রমণে কোচ রাজারা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েন। সুবিশাল রাজ্যপাট সংকুচিত হয়ে যায়। তখন থেকেই কোচ রাজবংশে রায়কত বংশের পূর্বাবস্থান নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে বৈকুন্ঠপুর কোচ রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে যায়। রায়কত বংশ নিজের একটি পৃথক পরিচিতি তৈরি ক’রে নেয়। কোচবিহার তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেনি। নরনারায়ণের পরবর্তী রাজাদের সে শক্তিও ছিল না। ফলে বৈকুন্ঠপুর নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব প্রাকৃতিক সীমানাবেষ্টিত স্থানে স্থির করেছিল। এই সময় সিকিম রাজ্য বিস্তারে মন দেয়। কিন্তু তারা বৈকুন্ঠপুর আক্রমণ করেনি। মুঘল শক্তি বা বাংলার সুবাদারগণও এই অঞ্চলে শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করেননি। ফলে শান্তিপূর্ণভাবে ও নির্বিঘ্নে রাজকার্য পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছিল। এই অবসরে ধর্মদেব রায়কত বৈকুন্ঠপুরের রাজপাট তুলে নিয়ে আসেন বর্তমান জলপাইগুড়িতে।
কিন্তু এই শান্তি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ধর্মদেবের পরের রায়কত ভূপদেবের সময় পর্যন্ত এই শান্তি বজায় ছিল। তৎপরবর্তী রাজা বিক্রমদেব রায়কতের সময় বাংলার নবাব ছিলেন সুজা খাঁ। বৈকুন্ঠপুরের ওপর রংপুরের নায়েব সৌলতজঙ্গ ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং বৈকুন্ঠপুর জয় ক’রে বিক্রমদেব ও তাঁর ভাই দর্পদেবকে বন্দি করলেন। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৭৩৬ থেকে ১৭৩৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। এই পরাজয়ের ফলে বৈকুন্ঠপুর রংপুরের পরগনায় পরিণত হ’ল। আর বিক্রমদেবের স্থলাভিষিক্ত হলেন দেব রায়কত। বিক্রমদেব ও দর্পদেবের অনুপস্থিতিতে বৈকুন্ঠপুরে চরম অরাজকতা শুরু হয়। দীর্ঘ সতের বছর তাঁরা অন্তরীপ ছিলেন। ১৭৪০ সাল থেকে মুর্শিদাবা দের মনযোগ রংপুরের ওপর থেকে কমে আসতে থাকে। কারণ মুর্শিদাবাদ আফগান ও মারাঠা শক্তির ক্রমাগত আক্রমণে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। এসময় রংপুরের ফৌজদার কাশিম আলি ১৭৪৯-৫০ সালে বিক্রমদেব ও দর্পদেবকে মুক্তি দিয়ে বৈকুন্ঠপুরে পুনরায় অভিষিক্ত করেন। এর পেছনে একটি সুনির্দিষ্ট কারণ আছে বলে মনে করা হয়। কাশেম আলি ভেবেছিলেন রংপুরের পাশাপাশি বিশৃঙ্খল বৈকুন্ঠপুরকে সংগঠিত ক’রে আফগান ও মারাঠাদের বিপক্ষে মুর্শিদাবাদের লড়াইয়ে সাহায্য পাবেন। কিন্তু তাঁর সে আশা বিফল হয়েছিল। কারণ বিক্রমদেব সেরকম কিছু করতে পারলেন না। তাঁর মৃত্যু হ’লে ছোটভাই দর্পদেব বৈকুন্ঠপুরের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। তাঁর সে আশা অমূলক ছিল না। কারণ বাংলা সেসময় রাজনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত ছিল। কিন্তু তিনি যেটা বুঝতে পারেননি তা হ’ল অল্প দিনের মধ্যেই বাংলা বিহার ওড়িষা ইংরেজের অধীনে চলে যাবে। আর ইংরেজরা কোনও শাসককেই স্বাধীনভাবে চলতে দেবে না। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব ইংরেজদের কাছে পরাজিত হ’লে বাণিজ্য করতে আসা মুনাফালোভী ইংরেজ রাজদন্ড হাতে নিল। শাসক রূপে ভারতে অধিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করল।
জলপাইগুড়ির ইতিহাস প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হবে কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা। যা সংগঠিত হয়েছিল রংপুর বৈকুন্ঠপুর অঞ্চলে। ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে কুখ্যাত—তাতে উত্তরবঙ্গের এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায় এবং বিস্তীর্ণ জনপদ শ্মশানে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় ইংরেজ সরকার রাজস্ব আদায়ে ছাড় দেয়নি। অত্যন্ত অমানবিক দৃষ্টান্তের পরিচয় দেয় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। উলটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় অতিরিক্ত কর আদায় করা হবে। পূর্বের তুলনায় বার্ষিক সত্তর হাজার টাকা বেশি অর্থ কোষাগারে জমা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে রংপুর জেলাটি তুলে দেওয়া হয় দুর্ধর্ষ ইজারাদার দেবী সিংহের হাতে। সেসময় রংপুরের বিস্তৃতি ছিল অসমের গোয়ালপাড়া থেকে পশ্চিমে পূর্ণিমা পর্যন্ত। অর্থাৎ বৈকুন্ঠপুর তথা জলপাইগুড়ির বিস্তৃত অঞ্চল রংপুরের অন্তর্ভূক্ত ছিল। আর এতবড় অঞ্চলের কর সংগ্রহের জন্য দেবী সিংহ নিযুক্ত করলেন আঞ্চলিক সর্দার। যারা তাঁর এজেন্ট হিসেবে কাজ করত। দেবী সিংহ রংপুরের পাশাপাশি মালদা, দিনাজপুর এবং শিলিগুড়ি মহকুমা ইজারা হিসেবে পেয়েছিলেন। এতবড় অঞ্চল একার পক্ষে সামলানো অসম্ভব ছিল। তাতে আঞ্চলিক সর্দাররা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল। আর দেবী সিংহ মুনাফা লোটার এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না। তিনি পুনর্বন্টনের সময় শুধু রংপুরের রাজস্বের পরিমাণ হাঁকলেন ষাট হাজার টাকা।
জনগণের ওপর শুরু হ’ল চরম অত্যাচার। দেবী সিংহের নিযুক্ত এসব সর্দার লাঠির জোরে যতখুশি রাজস্ব আদায় করতে লাগল। এরা প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছিল ব্যবস্থাটা অল্পদিনের জন্য। ফলে যা পারো লুটে নাও নীতি অবলম্বন করেছিল তারা। মানুষের প্রতি অমানবিক খেলায় মেতে উঠল এই সমস্ত লোকগুলি। খাজনা অনাদায়ে প্রজাদের হাত-পা বেঁধে আটকে রাখা হ’ত গাদাগাদি ক’রে। চলত বেতের আঘাত, চাবুকের ঘা। দিনের পর দিন খাবার দেওয়া হ’ত না বন্দি অসহায় প্রজাদের। খাজনা অনাদায়ে অনেক জমিদারকে পর্যন্ত উৎখাত হ’তে হয়েছিল।
প্রবল অত্যাচারে একসময় সাধারণ মানুষের ধৈর্যের বাধ ভেঙে যায়। শুরু হ’ল বিদ্রোহ। রংপুরের অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সন্ন্যাসী-ফকিরদের নেতৃত্বে স্থানীয় কৃষক ও জনসাধারণ শাসকের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন। শুরু হ’ল গণ অভ্যুত্থান। হিন্দু-মুসলিম মিলিত এই অভ্যুত্থান শুধু বিদ্রোহ ছিল না। এ ছিল যেন এতদঞ্চলের স্বাধীনতা ঘোষণা। গড়ে ওঠে বিকল্প সরকার। সে সরকার মহম্মদ নুরুলুদ্দিনকে নবাব ও দয়ারাম শীলকে দেওয়ান নিযুক্ত করে।
শুরু হ’ল রাজস্ব আদায়কারী সর্দারদের ওপর আক্রমণ। অজস্র কাছারিবাড়ি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হ’ল। বিদ্রোহীদের দল ছুটলো দেবী সিংহের কাছারিবাড়ি ধ্বংস করতে। এসময় দেবী সিংহ বারংবার ইংরেজদের কাছে সৈন্যের সাহায্য চাইলে প্রত্যখ্যাত হয়েছেন। গত্যন্তর না দেখে দেবী সিংহ ইজারাদারের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। দেবী সিংহের এক কুখ্যাত নায়েব গৌরমোহনকে বিদ্রোহী সরকার মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে কার্যকর করল। এদিকে রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি ও বিদ্রোহ সৃষ্টির কারণরূপে দেবী সিংহকে দোষী সাব্যস্ত ক’রে ইংরেজরা বন্দি করল। তাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হ’ল বিচারের জন্য।
(ক্রমশ)
Have an account?
Login with your personal info to keep reading premium contents
You don't have an account?
Enter your personal details and start your reading journey with us
Design & Developed by: WikiIND
Maintained by: Ekhon Dooars Team