




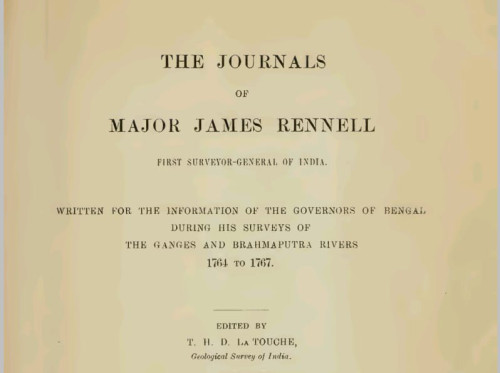








 පаІБа¶≠аІНа¶∞ а¶Ъа¶ЯаІНа¶ЯаІЛ඙ඌ඲аІНа¶ѓа¶ЊаІЯ
පаІБа¶≠аІНа¶∞ а¶Ъа¶ЯаІНа¶ЯаІЛ඙ඌ඲аІНа¶ѓа¶ЊаІЯ
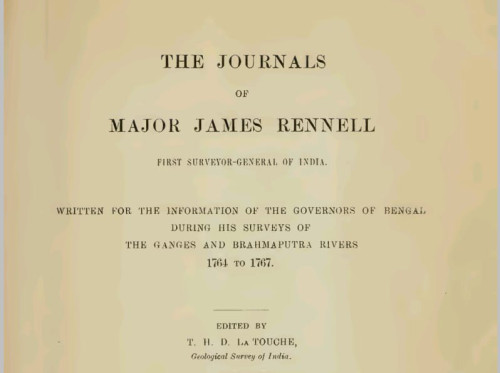
аІІаІ≠аІђаІ™ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ЂаІЗа¶ђаІНа¶∞аІБаІЯа¶Ња¶∞а¶њ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶ЧаІЛаІЬа¶ЊаІЯ а¶∞аІЗථаІЗа¶≤ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ а¶Ђа¶∞а¶Ња¶Єа¶°а¶Ња¶Ща¶ЊаІЯ ඙ඌ බගа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Хබගථ а¶Жа¶ЧаІЗ, а¶ЬඌථаІБаІЯа¶Ња¶∞а¶ња¶∞ පаІЗа¶ЈаІЗ ටගථග ඃඌටаІНа¶∞а¶Њ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ බаІЗа¶УаІЯඌථа¶Ча¶ЮаІНа¶Ь ඕаІЗа¶ХаІЗ, а¶ѓаІЗа¶Цඌථ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙аІВඐබගа¶ХаІЗ ටගඪаІНටඌа¶∞ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓ ඙ඌаІЬаІЗа¶∞ බаІВа¶∞ටаІНа¶ђ ටගථ а¶Ѓа¶Ња¶За¶≤а•§ а¶∞аІЗථаІЗа¶≤аІЗа¶∞ ඁටаІЗ, ටගඪаІНටඌ а¶≠аІЛа¶Яඌථ ඕаІЗа¶ХаІЗ ථаІЗа¶ЃаІЗ а¶Жа¶Єа¶Њ а¶ђаІЬ ථබаІАа•§ а¶Па¶ђа¶Ња¶∞ ටගථග ටගඪаІНටඌа¶∞ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓ ඙ඌаІЬ а¶Іа¶∞аІЗ а¶ЙටаІНටа¶∞аІЗ а¶Ъа¶≤а¶ђаІЗа¶®а•§ а¶Па¶∞඙а¶∞ ථථаІНබථ඙аІБа¶∞, а¶ђаІЛаІЯа¶Ња¶≤а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶њ, ඁථаІНа¶°а¶≤а¶Ша¶Ња¶Я а¶єаІЯаІЗ ටඌа¶∞ а¶Йа¶Ъගට а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶њ а¶Яа¶Ња¶ЙථаІЗ ඙аІМа¶Ба¶Ыа¶®а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Яа¶Ња¶Йථ ටаІЛ ටа¶Цථ а¶Ыа¶ња¶≤ ථඌ ටඌа¶З а¶∞аІЗථаІЗа¶≤ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶ња¶∞ ඐබа¶≤аІЗ а¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Па¶≤аІЗථ, ටඌа¶∞ ථඌඁ а¶Ђа¶∞а¶Ња¶Єа¶°а¶Ња¶Ща¶Ња•§
ඁඌථа¶ЪගටаІНа¶∞ а¶Жа¶Ба¶Ха¶Ња¶∞ а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Юටඌ ථගаІЯаІЗ а¶∞аІЗථаІЗа¶≤ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ьа¶Ња¶∞аІНථඌа¶≤ а¶∞а¶Ъථඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗа¶З ටගථග බගа¶ЪаІНа¶ЫаІЗථ а¶Ђа¶∞а¶Ња¶Єа¶°а¶Ња¶Ща¶ЊаІЯ а¶Жа¶Єа¶Ња¶∞ а¶Ца¶ђа¶∞а•§ а¶Па¶З а¶Ђа¶∞а¶Ња¶Єа¶°а¶Ња¶Ща¶Њ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶Яа¶Ња¶ЙථаІЗа¶∞ а¶Чටа¶ЬථаІНа¶Ѓа•§ ටගඪаІНටඌа¶∞ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓ ඙ඌаІЬаІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶Ђа¶∞а¶Ња¶Єа¶°а¶Ња¶Ща¶Њ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶∞аІЗථаІЗа¶≤аІЗа¶∞ ඁථаІНටඐаІНа¶ѓ: After crossing the Jabbonau & Ponga two shallow Rivers we came to Farsydunga, a Bazar Village lying on the Teesta & about 6 miles NNE from Taledaar. The Countrey here is open & well cultivated on the West side of the River, but the East side (which is part of Boutan) is Jungly & desart. We perceived pieces of different kinds of Trees lying on the Sands in the River: these the Countrey People informed me are brought down from the Boutan Mountains by the Freshes: amongst many other kinds of fine Timber I perceived the stump of a Firr Tree of which I brought away several pieces.
а¶Ђа¶∞а¶Ња¶Є а¶°а¶Ња¶Ща¶ЊаІЯ ඥаІЛа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ බаІБа¶ЯаІЛ а¶Еа¶Ча¶≠аІАа¶∞ ථබаІА ඙аІЗа¶∞а¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶∞аІЗථаІЗа¶≤а•§ ටඌа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ponga а¶ѓаІЗ ඙ඌа¶ЩаІНа¶Ча¶Њ, а¶Па¶Яа¶Њ а¶ђаІЛа¶Эа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶Яа¶Њ ථබаІАа¶∞ ථඌඁ а¶єа¶≤аІЛ Jabbonau. а¶Па¶Яа¶Њ а¶ХаІЛථ ථබаІА ටඌ ථගаІЯаІЗ а¶Па¶Цථ ඁඌඕඌ а¶Ша¶Ња¶Ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶Ыа¶њ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶Яа¶Њ а¶≤аІБ඙аІНටа¶У යටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ ථඌඁ ඐබа¶≤аІЗ а¶ѓаІЗටаІЗа¶У ඙ඌа¶∞аІЗа•§
а¶Ђа¶∞а¶Ња¶Єа¶°а¶Ња¶Ща¶Њ а¶ЫаІЗаІЬаІЗ а¶∞аІЗථаІЗа¶≤ Sannyasigota, ඁඌථаІЗ ඪථаІНථаІНа¶ѓа¶Ња¶ЄаІАа¶Ха¶Ња¶Яа¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗа¶®а•§ ටඌа¶∞඙а¶∞ ඁයඌථථаІНබඌ, а¶ЃаІЗа¶Ъа¶њ ථබаІА а¶єаІЯаІЗ а¶Цඌථගа¶Ха¶Яа¶Њ ටඌа¶∞а¶Ња¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ а¶ШаІБа¶∞аІЗ ටගඪаІНටඌ ඙аІЗа¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ъа¶ХаІНа¶Ха¶∞ බගаІЯаІЗ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶П඙ඌаІЬаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ටඕаІНа¶ѓ බගа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ ඙а¶∞аІЗ а¶≤а¶ња¶Ца¶Ыа¶ња•§
а¶Ђа¶∞а¶Ња¶Є а¶°а¶Ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶Яа¶Ња¶З а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐට ටගඪаІНටඌа¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЄаІЗ а¶ђа¶ња¶≤аІАа¶®а•§ а¶ђа¶Ња¶Ха¶ња¶Яа¶Њ а¶Жа¶Ьа¶ХаІЗа¶∞ а¶Яа¶Ња¶ЙථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ђа¶ња¶≤аІБ඙аІНට а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶З а¶Йа¶Ъа¶ња¶§а•§ а¶Па¶ђа¶В а¶Па¶З а¶Ђа¶∞а¶Ња¶Єа¶°а¶Ња¶Ща¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤, а¶ђаІИа¶ХаІБа¶£аІНආ඙аІБа¶∞ ථаІЯ, а¶∞а¶В඙аІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЄаІАඁඌථඌаІЯа•§ а¶ЄаІЗа¶Цඌථ ඕаІЗа¶ХаІЗ බаІБ а¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶За¶≤ а¶ЙටаІНටа¶∞аІЗа¶З පаІЗа¶Ј а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶∞а¶В඙аІБа¶∞ ථඌඁа¶Х ‘а¶Ъа¶Ња¶Ха¶≤а¶Њ’-а¶∞ а¶ЄаІАа¶Ѓа¶Ња•§ පаІБа¶∞аІБ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ "ඐටаІНටගප а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞аІЗ" а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓа•§ а¶Па¶Яа¶Њ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶ђаІИа¶ХаІБа¶£аІНආ඙аІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶Еа¶∞аІНඕථаІИටගа¶Х а¶®а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ХаІБа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ ඙ටаІНටථ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඙а¶∞ а¶ђаІИа¶ХаІБа¶£аІНආ඙аІБа¶∞аІЗ а¶ЙаІО඙ථаІНථ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ЄаІНа¶ђаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶Ѓа¶Ња¶£ ථගа¶∞аІНа¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ ඐටаІНа¶∞ගප а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ЄаІЗа¶Ха¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Ња•§
а¶ЄаІБටа¶∞а¶Ња¶В ඐටаІНටගප а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ь඲ඌථаІА а¶ѓаІЗ а¶∞а¶В඙аІБа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶Ха¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЯගටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ ථඌ, а¶Па¶Яа¶Њ а¶≠а¶Ња¶ђа¶Ња¶З а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶∞а¶В඙аІБа¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђаІЛබඌ-а¶∞ а¶Ъа¶Ња¶Ха¶≤а¶Њ а¶ђа¶Њ а¶ђаІЬ а¶ЯаІБа¶Ха¶∞аІЛа•§ а¶Йබඌයа¶∞а¶£: а¶Ъа¶Ња¶Ха¶≤а¶Њ а¶Ъа¶Ња¶Ха¶≤а¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ха¶Ња¶Яа¶Ња•§ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Жа¶ЧаІЗа¶Ха¶Ња¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗ බаІБа¶ЯаІЛ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶Њ බа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а•§ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶Вප а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶З යට а¶ЫаІЛа¶Яа•§ а¶Па¶Ха¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Њ-а¶Па¶∞ ඁඌ඙аІЗа¶∞ а¶єаІЯටаІЛа•§ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶Вපа¶З а¶ХаІЛථа¶У ථඌ а¶ХаІЛථа¶У а¶ђаІЬ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶ХаІЗ а¶Ца¶Ња¶Ьථඌ බගаІЯаІЗ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථ а¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶З а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶Ња¶§а•§
а¶ђаІИа¶ХаІБа¶£аІНආ඙аІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶Жа¶Ха¶Ња¶∞а¶У а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ ඁටаІЛа¶За•§ а¶Па¶∞ а¶Па¶Хබගа¶Х а¶≠аІЛа¶Яඌථ, а¶Жа¶∞аІЗа¶Хබගа¶ХаІЗ а¶ЃаІЛа¶Ша¶≤බаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ, а¶Жа¶∞аІЗа¶Хබගа¶ХаІЗ а¶ХаІБа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞а•§ а¶ПබаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶∞а¶Ња¶З а¶ђаІЬ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња•§ а¶Ха¶Ња¶Ча¶ЬаІЗ а¶Ха¶≤а¶ЃаІЗ а¶ђаІИа¶ХаІБа¶£аІНආ඙аІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶∞аІНටඐаІНа¶ѓ а¶єа¶≤аІЛ а¶ХаІБа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЖථаІБа¶ЧටаІНа¶ѓ а¶ЄаІНа¶ђаІАа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ ටඌа¶ХаІЗ а¶Ца¶Ња¶Ьථඌ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња•§ а¶ђаІИа¶ХаІБа¶£аІНආ඙аІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶Єа¶ђ а¶Єа¶ЃаІЯ ඁඌථаІЗථ а¶®а¶ња•§ а¶≠аІЛа¶ЯඌථаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ ඀ථаІНබග а¶Па¶Ба¶ЯаІЗ а¶ХаІБа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞а¶ХаІЗ а¶Эа¶Ња¶ЃаІЗа¶≤а¶ЊаІЯ а¶ЂаІЗа¶≤ටаІЗа¶У ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ ඙ගа¶Ы඙ඌ යටаІЗථ а¶®а¶Ња•§
а¶∞аІЗථаІЗа¶≤ а¶ѓа¶Цථ а¶Пබගа¶ХаІЗ а¶єа¶Ња¶Ба¶Яа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, ඁඌථаІЗ а¶ЄаІЗа¶З аІІаІ≠аІђаІ™ ථඌа¶Чඌබ а¶ђаІИа¶ХаІБа¶£аІНආ඙аІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ь඲ඌථаІА а¶ѓаІЗ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථ а¶ЄаІНඕඌථаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗ ථග, а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶ЃаІЗථаІЗ ථаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓаІЗටаІЗа¶З ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶∞аІЗථаІЗа¶≤ а¶ђаІИа¶ХаІБа¶£аІНආ඙аІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ь඲ඌථаІАа¶∞ ථඌඁа¶У а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ц а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗථ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ьа¶Ња¶∞аІНථඌа¶≤аІЗа•§ ඪථаІНථаІНа¶ѓа¶Ња¶ЄаІАа¶Ха¶Ња¶Яа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ ටගථග ඐටаІНටගප а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ь඲ඌථаІАටаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђаІЬ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа•§ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶Єа•§ а¶∞а¶Ња¶Ь඲ඌථаІАа¶∞ ථඌඁ Parpour.
а¶∞аІЗථаІЗа¶≤аІЗа¶∞ а¶Ьа¶Ња¶∞аІНථඌа¶≤аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙ඌබа¶Х ඙ඌබа¶Яа¶ња¶Ха¶ЊаІЯ а¶ЬඌථගаІЯаІЗ බගаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ а¶ѓаІЗ а¶Па¶З parpour а¶єа¶≤аІЛ а¶∞аІЗථаІЗа¶≤аІЗа¶∞ ඁඌථа¶ЪගටаІНа¶∞аІЗа¶∞ jelpigore. а¶Жа¶∞аІЛ а¶ЬඌථගаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ а¶ѓаІЗ, ඙ඌа¶∞඙аІМа¶∞аІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬඌබаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ь඲ඌථаІА а¶Жа¶ЧаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђаІИа¶ХаІБа¶£аІНආ඙аІБа¶∞аІЗа•§ а¶ЃаІЛа¶Ша¶≤බаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Жа¶ЄаІЗ parpour-а¶Па•§ а¶Па¶Цථ parpour а¶ЦаІБа¶ђ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐට ඙ඌයඌаІЬ඙аІБа¶∞а•§ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъа¶Ња¶∞а¶£аІЗ ඙ඌа¶∞඙аІБа¶∞ а¶ЪаІЗа¶єа¶Ња¶∞а¶Њ ඙аІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Па¶ђа¶В а¶∞аІЗථаІЗа¶≤ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Ња¶З පаІБථаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§
а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Њ а¶Ьа¶ЧබගථаІНබаІНа¶∞බаІЗа¶ђ а¶∞а¶ЊаІЯа¶Хට а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ඙аІЛа¶ЈаІНඃ඙аІБටаІНа¶∞ а¶Па¶ђа¶В а¶ЄаІЗа¶З а¶єаІЗටаІБ а¶ЃаІВа¶≤ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Еа¶≠а¶ња¶≠а¶Ња¶ђа¶Х а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ පඌඪථ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶ђа¶≤аІЗ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶ђа¶≤а¶Њ යට ඙аІЛа¶ЈаІНа¶ѓа¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња•§ а¶ЕථаІНඃබගа¶ХаІЗ බаІЗපඐථаІНа¶ІаІБ а¶ЪගටаІНටа¶∞а¶ЮаІНа¶Ьථ බඌප а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬගටаІЗ а¶ђаІЗප а¶Ьථ඙аІНа¶∞а¶њаІЯටඌ ඙аІЗටаІЗа¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ъа¶≤ටග ථඌඁ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Єа¶њ а¶Жа¶∞ а¶¶а¶Ња¶ґа•§ а¶Па¶З ටа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶ЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶≤аІЛа¶Х а¶Уа¶З බаІБа¶Ьථа¶ХаІЗ ඙а¶∞а¶Ѓ පаІНа¶∞බаІНа¶Іа¶ЊаІЯ а¶ђа¶≤ට ඙පаІБа¶∞а¶Ња¶Ьа¶Њ а¶Па¶ђа¶В පගаІЯа¶Ња¶≤ а¶¶а¶Ња¶Єа•§ а¶Е඙ඁඌථ පඐаІНබаІЗ ථаІЯ, а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъа¶Ња¶∞а¶£аІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶ЄаІБටа¶∞а¶Ња¶В ඙ඌයඌаІЬ඙аІБа¶∞ а¶ѓаІЗ parpour ථаІЯ, ටඌ а¶ђа¶≤а¶њ а¶ХаІА а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ? а¶Па¶З ඙ඌයඌаІЬ඙аІБа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶∞а¶Ња¶Ь඲ඌථаІА а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗ а¶Яа¶Ња¶ЙථаІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ ඪඌඕаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗ jelpigore ථඌඁа¶Яа¶Ња¶Уа•§ а¶Па¶Єа¶ђаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶З а¶ЧаІЬаІЗ а¶ЙආаІЗа¶ЫаІЗ ‘а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶њ’ පඐаІНа¶¶а•§
а¶∞аІЗථаІЗа¶≤аІЗа¶∞ а¶Ьа¶Ња¶∞аІНථඌа¶≤аІЗа¶∞ а¶≠ගටаІНටගටаІЗ ඁථаІЗ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗ ඐටаІНටගප а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ь඲ඌථаІА ඙аІНа¶∞ඕඁаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђаІИа¶ХаІБа¶£аІНආ඙аІБа¶∞а•§ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Еа¶∞а¶£аІНа¶ѓ а¶ђаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶§а•§ а¶Па¶∞඙а¶∞ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶ЄаІНඕඌථඌථаІНටа¶∞ගට а¶єаІЯ jelpigre-ටаІЗ а¶Па¶ђа¶В ටа¶Цථ ටඌа¶∞ ථඌඁ а¶єаІЯ ඙ඌයඌаІЬ඙аІБа¶∞а•§ а¶Жа¶∞аІЛ ඙а¶∞аІЗ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶њ-а¶∞ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඌඐථඌ ටаІИа¶∞а¶њ а¶єа¶≤аІЗ а¶∞а¶Ња¶Ь඲ඌථаІА а¶ђа¶∞аІНටඁඌථ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ а¶Жа¶ЄаІЗа•§ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ ටටබගථаІЗ ඐටаІНටගප а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞аІЗ а¶≤аІБ඙аІНට а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶У ඙а¶∞а¶ња¶£а¶§ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ а¶Ьඁගබඌа¶∞аІЗа•§ ටඌа¶З а¶ђа¶∞аІНටඁඌථ а¶Жа¶Ѓа¶ђа¶ЊаІЬа¶њ-а¶Ђа¶Ња¶≤а¶Ња¶Ха¶Ња¶Яа¶Њ ඪථаІНථගයගට jelpigore а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНа¶ђ а¶єа¶Ња¶∞а¶Ња¶≤а•§ ඐබа¶≤аІЗ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶њ а¶ЧаІЬаІЗ а¶Йආа¶≤ а¶єаІЯ ටаІЛ а¶ђа¶Њ а¶Ђа¶∞а¶Ња¶Єа¶°а¶Ња¶Ща¶Ња¶∞а¶З а¶Ѓа¶Ња¶ЯගටаІЗа•§
ථගа¶∞ඌ඙ටаІНටඌа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗ а¶∞а¶ЊаІЯа¶ХටබаІЗа¶∞ а¶Яа¶Ња¶ЙථаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Жа¶Єа¶Ња¶Яа¶Ња¶З а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Й඙ඃаІБа¶ХаІНට ඪගබаІН඲ඌථаІНа¶§а•§ а¶Яа¶Ња¶Йථ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶ЬබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Па¶Яа¶Њ а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶єаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶∞а¶ња¶Х а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗа•§ а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶∞а¶ња¶Х а¶Ша¶Ња¶Ба¶Яа¶њ а¶ЄаІНඕඌ඙ථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶ЄаІНඕඌථа¶Яа¶њ а¶≠аІЛа¶ЯඌථаІЗа¶∞ а¶Чටගඐග඲ග а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Ња¶∞ ඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗ а¶Жබа¶∞аІНа¶ґа•§
а¶Па¶ђа¶Ња¶∞ а¶ѓаІЗ ඙аІНа¶∞පаІНථа¶Яа¶Њ а¶Жа¶Єа¶ЫаІЗ ටඌ а¶єа¶≤аІЛ: а¶ѓаІЗ а¶ЬаІЗа¶≤аІН඙ගа¶ЧаІЛа¶∞аІЗ-ටаІЗ ඙ඌයඌаІЬ඙аІБа¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤, а¶ЄаІЗа¶З а¶ЬаІЗа¶≤аІН඙ගа¶ЧаІЛа¶∞аІЗ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶ХаІА а¶Ыа¶ња¶≤? а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶Ха¶њ ඙аІБа¶∞ථаІЛ а¶ХаІЛථа¶У а¶Ьථ඙බ? а¶ХаІЛථа¶У а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Њ а¶єа¶Ња¶Я? а¶ЄаІЗ а¶ѓаІБа¶ЧаІЗа¶∞ ථගа¶∞а¶ња¶ЦаІЗ а¶ЬаІЗа¶≤аІН඙ගа¶ЧаІЛа¶∞аІЗ-а¶∞ а¶≠аІМа¶ЧаІЛа¶≤а¶ња¶Х а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌථ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђаІЗප а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£а•§ යටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶Па¶Яа¶Ња¶З а¶Ыа¶ња¶≤ а¶∞а¶ЊаІЯа¶Хට а¶∞а¶Ња¶ЬඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђ а¶Ъа¶Ња¶ЗටаІЗ а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Ьа¶®а¶™а¶¶а•§
а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶Яа¶њ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶∞ а¶Е඙аІЗа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶∞а¶Ња¶ЦаІЗа•§
а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ьа¶∞а¶Њ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶њ ථඌඁа¶Х а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶ХаІЗ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶њ а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Чආථ а¶Ха¶∞аІЗථ аІІаІЃаІђаІѓ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ аІІа¶≤а¶Њ а¶ЬඌථаІБаІЯа¶Ња¶∞а¶ња•§ а¶ЈаІЛа¶≤ а¶ђа¶Ыа¶∞ ඙а¶∞ аІІаІЃаІЃаІЂ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ аІІа¶≤а¶Њ а¶П඙аІНа¶∞а¶ња¶≤ а¶Чආථ а¶Ха¶∞аІЗථ ඙ඌа¶Ба¶Ъа¶Яа¶њ а¶УаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶° ඐගපගඣаІНа¶Я а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶њ ඙аІБа¶∞а¶Єа¶≠а¶Њ а¶ђа¶Њ а¶Яа¶Ња¶Йථ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶ња•§ ටа¶Цථ а¶Яа¶Ња¶ЙථаІЗа¶∞ а¶ЖаІЯටථ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Єа¶ЊаІЬаІЗ ටගථ а¶ђа¶∞аІНа¶Ч а¶Ѓа¶Ња¶За¶≤ а¶Жа¶∞ а¶≤аІЛа¶Ха¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ а¶Жа¶Я а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඪඌඁඌථаІНа¶ѓ а¶Ха¶Ѓа•§ ථටаІБථ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Њ, ථටаІБථ а¶Яа¶Ња¶Йථ --- а¶Ђа¶≤аІЗ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ ඪථаІН඲ඌථаІЗ а¶≤аІЛа¶Ха¶Ьථ а¶Па¶ЄаІЗ а¶≠а¶њаІЬ а¶ЬඁඌටаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶∞а¶єа¶ња¶Ѓ а¶ђа¶ХаІНа¶Є а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ඙аІЗපа¶Ха¶Ња¶∞а•§ ටගථග а¶Яа¶Ња¶ЙථаІЗ ටаІЗටаІНа¶∞ගප а¶ђа¶ња¶Ша¶Њ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶ѓаІЗ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ ඐඌථඌа¶≤аІЗථ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Ња¶ХаІЗ а¶≤аІЛа¶ХаІЗ а¶ђа¶≤ට ථඐඌඐ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња•§
а¶Еа¶Ъа¶ња¶∞аІЗа¶З а¶Яа¶Ња¶Йථ а¶Ьа¶ЃаІЗ а¶Йආа¶≤а•§ а¶Ж඙ගඪ-а¶Жබඌа¶≤ට-а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤ а¶єа¶≤аІЛа•§ а¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞а¶њ ථගаІЯаІЗ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌ а¶У а¶Жප඙ඌපаІЗа¶∞ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞а¶Њ а¶Па¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Жа¶Зථග а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶Ња¶∞ а¶ЄаІВටаІНа¶∞аІЗ а¶≤аІЛа¶ХаІЗа¶∞а¶Њ а¶Па¶≤аІЗථ ඙аІБа¶ђ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗа•§ а¶ЧаІЛаІЬа¶ЊаІЯ ඥඌа¶Ха¶Њ а¶Жа¶∞ ඙ඌඐථඌа¶∞ а¶≤аІЛа¶Ха¶Яа¶Ња¶З а¶ђаІЗа¶ґа¶ња•§ а¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Па¶≤аІЗථ පаІНа¶∞а¶Ѓа¶ЬаІАа¶ђаІАа¶∞ බа¶≤а•§ а¶∞а¶єа¶ња¶Ѓ а¶ђа¶ХаІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ЧаІЗ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Па¶≤аІЗථ а¶ЃаІБа¶∞аІНපගබඌඐඌබ, ථаІЛаІЯа¶Ња¶Ца¶Ња¶≤а¶њ, а¶ХаІБа¶Ѓа¶ња¶≤аІНа¶≤а¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗа•§ а¶Па¶≤аІЛ а¶Ъа¶Њ а¶У ටඌа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ча¶Ња¶®а•§ а¶Па¶≤аІЛ а¶Яа¶Ња¶Йථ а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ђ, а¶Жа¶∞аІНඃථඌа¶ЯаІНа¶ѓа•§
පаІБа¶∞аІБа¶∞ ඙а¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ХаІЯаІЗа¶Х බපа¶Х а¶Яа¶Ња¶ЙථаІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶Х а¶Яа¶Ња¶Йථ а¶Чආථ ථගаІЯаІЗа¶З а¶ЃаІЗටаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЛථа¶У а¶Яа¶Ња¶ЙථаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶Па¶Х а¶∞аІЛа¶Ѓа¶Ња¶ЮаІНа¶Ъа¶Ха¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯа•§
(а¶Ъа¶≤а¶ђаІЗ)
Have an account?
Login with your personal info to keep reading premium contents
You don't have an account?
Enter your personal details and start your reading journey with us
Design & Developed by: WikiIND
Maintained by: Ekhon Dooars Team