




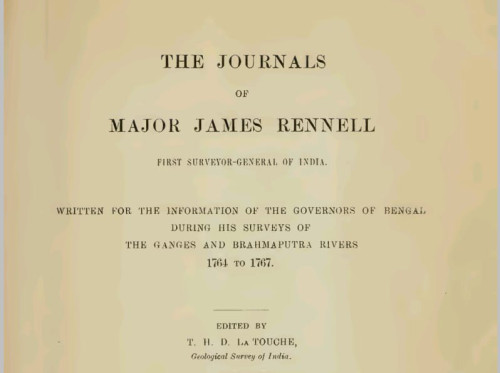








 а¶ЬඃඊබаІА඙ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞
а¶ЬඃඊබаІА඙ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞

а¶ЦаІБа¶ђ а¶ђаІЗපග බගථаІЗа¶∞ ඙аІБа¶∞ථаІЛ а¶Ча¶≤аІН඙ ථඃඊ, а¶Жа¶Ь ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ьа¶Ња¶ЄаІНа¶Я а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶ХаІБа¶°а¶Ља¶њ а¶Жа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Ха¶•а¶Ња•§ а¶Ча¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞ а¶П඙ඌа¶∞аІЗ а¶ѓаІЗ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓа¶ђа¶ЩаІНа¶Ч, а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶Ч ථඌඁаІЗ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ ඁඌථаІБа¶Ј а¶ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ЪаІЗථаІЗ, а¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ ඙аІБа¶ЬаІЛа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶Љ а¶ђаІЗධඊඌටаІЗ а¶Па¶≤аІЗ а¶Пථа¶ЬаІЗ඙ග а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථаІЗ ථаІЗа¶ЃаІЗа¶З а¶Ѓа¶Ња¶Ђа¶≤а¶Ња¶∞ ඙а¶∞ටаІЗ а¶єа¶ѓа¶Љ, ඙ඌа¶ЫаІЗ а¶єа¶ња¶ЃаІЗа¶≤ а¶єа¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶∞ а¶ЫаІЛа¶Ба¶ѓа¶Ља¶Ња¶ѓа¶Љ ථගа¶Йа¶ЃаІЛථගඃඊඌ ථඌ а¶єа¶ѓа¶Љ, а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ ඪඌටа¶Яа¶њ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞аІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Ња¶З а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъපගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ ඲ථ а¶Ыа¶ња¶≤, а¶ЄаІЗа¶Яа¶њ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶Ч ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶Ља•§ а¶Жа¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЄаІЗа¶З ඪඌට а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ ඲ථаІЗа¶∞ බаІБа¶Яа¶њ а¶ђаІЛථ, а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶Ч а¶ЃаІЗа¶°а¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ а¶Ха¶≤аІЗа¶Ь а¶Жа¶∞ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБа¶°а¶Ља¶њ а¶За¶ЮаІНа¶Ьගථගඃඊඌа¶∞а¶ња¶В а¶Ха¶≤аІЗа¶Ьа•§ ටа¶Цථ а¶ЧаІЛа¶Яа¶Њ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ЃаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞а¶Ња¶З а¶За¶ЮаІНа¶Ьගථගඃඊඌа¶∞а¶ња¶В ඙ධඊටаІЗ බа¶≤аІЗ බа¶≤аІЗ බа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£ а¶≠а¶Ња¶∞ට а¶ЫаІБа¶Яа¶§а•§ ටඌа¶∞඙а¶∞ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶Па¶З පටа¶ХаІЗа¶∞ а¶ЧаІЛа¶°а¶Ља¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђаІЗප а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶За¶≠аІЗа¶Я а¶За¶ЮаІНа¶Ьගථගඃඊඌа¶∞а¶ња¶В а¶Ха¶≤аІЗа¶Ь а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶°а¶Љ а¶Еа¶ВපаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ща¶Ња¶≤а¶њ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ЃаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ьа¶≤а¶єа¶Ња¶УඃඊඌටаІЗа¶З ඙аІНа¶∞а¶ѓаІБа¶ХаІНටගඐගබ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞ටаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞а¶≤а•§ ඃබගа¶У а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶≠а¶ња¶Жа¶За¶Яа¶њ а¶ђа¶Њ а¶Па¶Єа¶Жа¶∞а¶Па¶Ѓ а¶ђа¶Њ а¶ђа¶ња¶Жа¶За¶Яа¶ња¶Па¶Є а¶Ха¶ња¶Ва¶ђа¶Њ а¶ХаІЗа¶Жа¶За¶Жа¶За¶Яа¶њ-а¶Па¶∞ ඁටаІЛ а¶Па¶°аІБа¶ХаІЗපථ а¶єа¶Ња¶ђ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Жа¶Ьа¶У а¶Ча¶°а¶ЉаІЗ а¶УආаІЗ а¶®а¶ња•§ а¶ХаІЛථаІЛ බаІНඐගඁට ථаІЗа¶З, ඁඌථඐ а¶Єа¶ЃаІН඙බаІЗа¶∞ а¶Ша¶Ња¶Яටගа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ ථඃඊ, а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Х ඪබගа¶ЪаІНа¶Ыа¶Ња¶∞ а¶Еа¶≠а¶Ња¶ђ а¶Па¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ බඌඃඊаІАа•§ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶ѓа¶Љ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЛථаІЛ а¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶Єа¶Ва¶Ха¶Яа¶ХаІЗ а¶ЃаІЛа¶Ха¶Ња¶ђа¶ња¶≤а¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Ъа¶Яа¶Ьа¶≤බග а¶∞а¶ња¶≤а¶ња¶ЂаІЗа¶∞ ඐථаІНබаІЛа¶ђа¶ЄаІНට а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶њ а¶ђа¶Ња¶∞а¶ђа¶Ња¶∞, ඙аІЗа¶Зථ а¶Ха¶ња¶≤а¶Ња¶∞ බගඃඊаІЗ а¶ђаІНඃඕඌ а¶ХඁඌථаІЛа¶∞ ඁටаІЛ, බаІАа¶∞аІНа¶Ша¶ЃаІЗඃඊඌබаІА а¶ЄаІБа¶ЄаІНඕටඌа¶∞ ඙ඕ а¶ХаІЛථаІЛබගථа¶З ථගа¶З а¶®а¶ња•§ а¶ѓаІЗඁථ ඙аІНа¶∞аІЗа¶Єа¶ња¶°аІЗථаІНа¶Єа¶њ а¶Ха¶≤аІЗа¶Ь ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Еа¶ІаІНඃ඙а¶ХබаІЗа¶∞ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶ѓа¶Љ ඐබа¶≤а¶њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶ѓа¶Љ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ බගටаІЗ а¶ЪаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ыа¶њ ඙аІНа¶∞ඌථаІНටගа¶Х а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ЃаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗබаІЗа¶∞, а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙аІНа¶∞аІЗа¶Єа¶ња¶°аІЗථаІНа¶Єа¶њ а¶Ха¶≤аІЗа¶ЬටаІБа¶≤аІНа¶ѓ а¶Ха¶≤аІЗа¶Ь а¶ЧධඊටаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶ђа¶Њ ඐගථගඃඊаІЛа¶Ч а¶Ха¶∞а¶ња¶®а¶ња•§ а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶ѓ а¶ђаІНа¶∞а¶ЬаІЗථаІНබаІНа¶∞ ථඌඕ පаІАа¶≤ а¶ѓаІЗ а¶Ха¶≤аІЗа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶£аІНа¶°а¶Ња¶∞аІА а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Па¶Хබගථ, а¶ЄаІЗа¶Яа¶ња¶ХаІЗа¶У а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ЄаІЗථаІНа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Еа¶Ђ а¶Па¶ХаІНа¶ЄаІЗа¶≤аІЗථаІНа¶Є а¶Ха¶∞аІЗ ටаІБа¶≤ටаІЗ а¶ЄаІЗа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶Ч ථගа¶З ථග а¶ХаІЛථаІЛа¶¶а¶ња¶®а•§
а¶Па¶З පටа¶ХаІЗа¶∞ පаІБа¶∞аІБටаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъපගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ѓаІЗ а¶єа¶Ња¶Ђ а¶°а¶Ьථ ඙аІНа¶≤а¶Ња¶Є ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶Љ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЄаІЗа¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶∞ а¶Єа¶ђа¶ЧаІБа¶≤аІЛටаІЗ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶ђа¶ња¶Ја¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъපගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶Ч а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ЄаІНටඐ а¶Па¶Яа¶Ња¶З а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ѓаІЗ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЃаІЗа¶Іа¶Ња¶ђаІА а¶ЫඌටаІНа¶∞а¶∞а¶Њ පаІБа¶ІаІБ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ ථඃඊ, ඪඌයගටаІНа¶ѓ а¶ђа¶Њ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ ථගඃඊаІЗа¶У а¶ЄаІНථඌටа¶ХаІЛටаІНටа¶∞ ඙ධඊටаІЗ а¶ЄаІНඐ඙аІНථ බаІЗа¶ЦටаІЛ බаІБа¶ЯаІЛ ඁඌටаІНа¶∞ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶Љ а¶Ша¶ња¶∞аІЗ, а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌ а¶Жа¶∞ ඃඌබඐ඙аІБа¶∞а•§ а¶ЄаІНථඌටа¶Х а¶ЄаІНටа¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞аІЗа¶Єа¶ња¶°аІЗථаІНа¶Єа¶њ а¶ђа¶Њ а¶ЄаІЗථаІНа¶Я а¶ЬаІЗа¶≠а¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶∞аІНа¶Є, а¶ђаІЗඕаІБථаІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ха¶≤аІЗа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶∞аІЗа¶Ь а¶Ыа¶ња¶≤, а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЄаІНථඌටа¶ХаІЛටаІНටа¶∞аІЗа¶∞ а¶Е඙පථ а¶Ха¶≤а¶ХඌටඌටаІЗа¶У а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЦаІБа¶ђа¶З а¶ЄаІАඁගට, а¶ђа¶Ња¶Ха¶њ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶ѓа¶Љ ටаІЛ а¶Жа¶∞аІЛ а¶Ха¶Ѓа•§ ටඌа¶З а¶ђа¶Ыа¶∞ බපаІЗа¶Х а¶Жа¶ЧаІЗ ඙а¶∞аІНඃථаІНටа¶У, а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ ඁටаІЛ ඙аІНа¶∞ඌථаІНටබаІЗප ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ බаІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶њ, а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЄаІНථඌටа¶ХаІЛටаІНටа¶∞ а¶°а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶њ а¶≤а¶Ња¶≠аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ЫඌටаІНа¶∞ ඙ඌධඊග බගට а¶≠а¶Ња¶Ча¶≤඙аІБа¶∞, а¶Хඌථ඙аІБа¶∞-а¶Па¶∞ ඁටаІЛ а¶Ьа¶Ња¶ѓа¶Ља¶Ча¶Ња¶ѓа¶Ља•§ а¶≠аІВа¶ЧаІЛа¶≤, а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ьа¶њ а¶Па¶З а¶Єа¶ђ а¶ђа¶ња¶Ја¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤ а¶Єа¶Ња¶∞аІНа¶≠а¶ња¶Є а¶ХඁගපථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЪаІБа¶∞ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Х ථаІЗа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ යටаІЛ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶ђа¶Ыа¶∞, а¶Па¶ђа¶В а¶Пට а¶ЄаІНථඌටа¶ХаІЛටаІНටа¶∞ а¶ЫඌටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶ѓаІЛа¶Чඌථ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶Ља¶ЧаІБа¶≤аІЛ බගටаІЗ ඙ඌа¶∞ටаІЛ ථඌ ටа¶Ца¶®а•§ а¶ЄаІЗа¶За¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶Љ а¶Хඌථ඙аІБа¶∞, а¶≠а¶Ња¶Ча¶≤඙аІБа¶∞аІЗа¶∞ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶Ља¶ЧаІБа¶≤аІЛ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГට а¶Еа¶∞аІНඕаІЗа¶З а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶єа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ බඌа¶Ба¶°а¶Ља¶ња¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§
а¶ђа¶Ыа¶∞ බපаІЗа¶Х ඙а¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ЄаІНඕගටග а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶Хබඁа¶З ඐබа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶Цථ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ѓа¶Љ ඙аІНа¶∞ටග а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶ѓа¶Љ ථаІНа¶ѓаІВථටඁ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶Љ а¶Ча¶°а¶ЉаІЗ а¶ЙආаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶Цථ а¶Жа¶∞ а¶ЫඌටаІНа¶∞බаІЗа¶∞ а¶Хඌථ඙аІБа¶∞ а¶ЫаІБа¶ЯටаІЗ а¶єа¶ѓа¶Љ а¶®а¶Ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЯаІНа¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶°а¶њ а¶Па¶Яа¶Ња¶З а¶ѓаІЗ а¶Жа¶Ь ඕаІЗа¶ХаІЗ ටаІНа¶∞ගප-а¶Ъа¶≤аІНа¶≤ගප а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗа¶У а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъපගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶ЄаІЗථаІНа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Еа¶Ђ а¶Па¶ХаІНа¶ЄаІЗа¶≤аІЗථаІНа¶Є а¶ѓаІЗ බаІБа¶ЯаІЛ а¶Ыа¶ња¶≤, ටඌа¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ ටаІГටаІАа¶ѓа¶Љ ථඌඁ а¶ЦаІБа¶ђ а¶ЬаІЛа¶∞аІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъа¶Ња¶∞а¶£ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ ඁටаІЛ ඙а¶∞а¶ња¶ЄаІНඕගටග а¶Жа¶Ьа¶У а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶њ а¶®а¶ња•§ а¶ђа¶∞а¶В а¶Уа¶З බаІБа¶ЯаІЛටаІЗа¶У ථаІЛа¶Ва¶∞а¶Њ а¶∞а¶Ња¶ЬථаІАටගа¶∞ а¶Ха¶Ња¶≤а¶њ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ђаІЗපග а¶≤а¶Ња¶Ча¶ња¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞аІЗа¶ХаІНඣගට ඃබග බаІЗа¶Ца¶њ, а¶Ѓа¶Ња¶≤බඌ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЧаІМа¶°а¶Ља¶ђа¶ЩаІНа¶Ч ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶Љ а¶ђаІЗප а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶Яа¶Њ а¶Жа¶∞ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඙а¶ЮаІНа¶Ъඌථථ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶Њ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶Љ ඪඌඁඌථаІНа¶ѓ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඙а¶∞а¶ња¶ХඌආඌඁаІЛ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙аІЗа¶∞аІЗа¶ЫаІЗ, а¶ђа¶Ња¶Ха¶ња¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶Па¶Хබඁа¶З а¶ЦаІЛа¶БаІЬа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ බа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£ බගථඌа¶Ь඙аІБа¶∞ а¶Жа¶∞ බඌа¶∞аІНа¶Ьа¶ња¶≤а¶ња¶В а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶Љ බаІБа¶ЯаІЛ а¶Жа¶Ь ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶Й඙ඌа¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶ѓ а¶Ыа¶Ња¶°а¶Ља¶Њ බаІНඐගටаІАа¶ѓа¶Љ а¶ХаІЛථаІЛ а¶Жа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞а¶ња¶Х а¶ђа¶Њ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Х ඙බ ඙ඌඃඊ ථග, ඃබගа¶У а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЪаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Ъ а¶Па¶З а¶Єа¶ђ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶Љ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЄаІНථඌටа¶ХаІЛටаІНටа¶∞ а¶°а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶њ а¶≤а¶Ња¶≠ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа•§ а¶Жප඙ඌපаІЗа¶∞ а¶Ха¶≤аІЗа¶Ьа¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶∞ පගа¶ХаІНа¶Ја¶ХබаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђаІЗа¶ЪаІНа¶ЫඌපаІНа¶∞а¶ЃаІЗ а¶ХаІЛථаІЛа¶∞а¶Ха¶ЃаІЗ а¶°а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶њ බаІЗа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, ටඌа¶∞ а¶ђаІЗපග а¶ХаІЛථаІЛ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඙аІНа¶∞ටаІНඃඌපඌ а¶Ха¶∞а¶Ња¶У а¶ЕථаІНа¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Ља•§ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГට а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъපගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ ථаІНа¶ѓаІВථටඁ ඙а¶∞а¶ња¶ХඌආඌඁаІЛ а¶Ыа¶Ња¶°а¶Ља¶Њ а¶ѓаІЗ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ЃаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞а¶Њ а¶°а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶њ ඙ඌа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶Љ ටаІЛ ථаІЗа¶За¶З, а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ХаІЛථаІЛ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ЄаІБ඙ඌа¶∞ගප а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ ඁටаІЛ а¶ХаІЛථаІЛ ඙බඌ඲ගа¶Ха¶Ња¶∞аІАа¶У ථаІЗа¶За•§ а¶Жа¶≤ග඙аІБа¶∞බаІБа¶ѓа¶Ља¶Ња¶∞ а¶Ха¶≤аІЗа¶Ь, а¶ЙටаІНටа¶∞аІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ථඌඁаІА а¶Ха¶≤аІЗа¶Ь, ටඌа¶ХаІЗ ටаІБа¶≤аІЗ බගඃඊаІЗ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶Љ а¶Ха¶∞аІЗ බаІЗа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ а¶єа¶≤а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶Ь а¶Еа¶ђа¶Іа¶њ а¶ХаІЛථаІЛ а¶Жа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞а¶ња¶Х, ථටаІБථ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Х ඙බ, а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ХаІЛථаІЛ а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶Ч а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З ටаІИа¶∞а¶њ а¶єа¶≤аІЛ а¶®а¶Ња•§
а¶ЙටаІНටа¶∞аІЗа¶∞ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶Ља¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶°а¶Љ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Х а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІЗ ඪඌයගටаІНа¶ѓ а¶ђа¶Њ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ ටඐаІБ а¶ЬаІЛධඊඌටඌа¶≤а¶њ බගඃඊаІЗ а¶Ъа¶≤а¶ЫаІЗ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ ඙ධඊඌථаІЛа¶∞ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶≠а¶ѓа¶Ља¶Ња¶ђа¶єа•§ а¶ХаІЛථаІЛ а¶ХаІЛථаІЛ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Па¶ЦථаІЛ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ ධග඙ඌа¶∞аІНа¶Яа¶ЃаІЗථаІНа¶Яа¶ЧаІБа¶≤аІЛටаІЗ а¶ХаІЛථаІЛ ඙аІНа¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶Яа¶ња¶Ха¶Ња¶≤ а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶Є а¶Ха¶∞ඌථаІЛа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌ ථаІЗа¶З, а¶Еඕа¶Ъ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗ а¶ЄаІНථඌටа¶ХаІЛටаІНටа¶∞ а¶°а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶њ а¶ЄаІЗа¶Цඌථ ඕаІЗа¶ХаІЗ ථගඃඊаІЗ а¶ђаІЗа¶∞аІЛа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗ а¶ЃаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞а¶Ња•§ а¶ђаІЗපගа¶∞а¶≠а¶Ња¶Ч а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ЃаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Па¶З а¶Еа¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌа¶∞ පගа¶Ха¶Ња¶∞ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ ථඌ а¶ЬаІЗථаІЗ ථඌ а¶ђаІБа¶ЭаІЗ а¶≠а¶∞аІНටග а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ, а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Па¶З а¶ЫඌටаІНа¶∞а¶ЫඌටаІНа¶∞аІАබаІЗа¶∞ а¶ђа¶°а¶Љ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Еа¶Вප а¶Ђа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІНа¶Я а¶ђа¶Њ а¶ЄаІЗа¶ХаІЗථаІНа¶° а¶ЬаІЗථඌа¶∞аІЗපථ а¶≤а¶Ња¶∞аІНථඌа¶∞а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЪගථаІНටඌපаІАа¶≤ ඙аІНа¶∞а¶ЪаІБа¶∞ ඁඌථаІБа¶Ј а¶Па¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶У а¶ђа¶Ња¶Є а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ටඌа¶∞а¶Њ а¶ХගථаІНටаІБ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ЃаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗබаІЗа¶∞ ථගටඌථаІНට බඌඃඊаІЗ ථඌ ඙ධඊа¶≤аІЗ а¶Па¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶ЫаІЗථ а¶®а¶Ња•§ ඙аІНа¶∞ඕඁට ටඌа¶∞а¶Њ а¶ЬаІЗථඌа¶∞аІЗа¶≤ а¶ХаІЛа¶∞аІНа¶Є ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ЃаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗබаІЗа¶∞ а¶Єа¶∞а¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ ථගа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ ථගа¶ЪаІНа¶ЫаІЗථ ථඌ, ටඌа¶∞а¶Ња¶У а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ බаІНඐගටаІАа¶ѓа¶Љ а¶ђа¶Њ ටаІГටаІАа¶ѓа¶Љ а¶Єа¶Ња¶∞а¶ња¶∞ а¶Ха¶≤аІЗа¶Ь а¶єа¶≤аІЗа¶У а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗа¶З а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъа¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶Ѓа¶ња¶ХаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ЃаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗබаІЗа¶∞ ඙ඌආගඃඊаІЗ බගа¶ЪаІНа¶ЫаІЗථ, ඃඌටаІЗ а¶єаІЛа¶Ѓ а¶За¶Йථගа¶≠а¶Ња¶∞аІНа¶Єа¶ња¶Яа¶ња¶∞ а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶Ч ථගඃඊаІЗ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌ а¶Єа¶Ва¶≤а¶ЧаІНථ а¶ХаІЛථаІЛ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ЄаІНථඌටа¶ХаІЛටаІНටа¶∞ ඙ධඊඌа¶∞ а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶Ч а¶Ша¶ЯаІЗ, а¶Па¶З а¶Жа¶ґа¶Ња¶ѓа¶Ља•§ а¶Жа¶∞ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙а¶Ьගපථඌа¶≤ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶°а¶≠ඌථаІНа¶ЯаІЗа¶Ь ටаІЛ а¶Жа¶ЫаІЗа¶За•§ а¶ЗථаІНа¶Яа¶Ња¶∞ථаІЗа¶Я ඐග඙аІНа¶≤а¶ђ ඃටа¶З а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗ ටඕаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶≠ඌථаІНа¶°а¶Ња¶∞ а¶ЙථаІНа¶ЃаІБа¶ХаІНට а¶Ха¶∞аІБа¶Х ථඌ а¶ХаІЗථ, ඃටа¶З а¶ЬаІЗ-а¶ЄаІНа¶ЯаІЛа¶∞ а¶ђа¶Њ а¶≤а¶ња¶ђ-а¶ЬаІЗථ ඕаІЗа¶ХаІЗ ථගඁаІЗа¶ЈаІЗа¶З а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶°а¶Ња¶Йථа¶≤аІЛа¶° а¶Ха¶∞аІЗ ථගටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶њ ඙аІНа¶∞а¶ѓа¶ЉаІЛа¶ЬථаІАа¶ѓа¶Љ а¶ђа¶З, а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ха¶≤аІЗа¶Ь а¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞аІАа¶Я, а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶Яගප а¶≤а¶Ња¶За¶ђаІНа¶∞аІЗа¶∞аІА, ථаІНඃඌපථඌа¶≤ а¶≤а¶Ња¶За¶ђаІНа¶∞аІЗа¶∞аІА, а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЧаІЛа¶≤඙ඌа¶∞аІНа¶Х а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъа¶Ња¶∞а¶Ња¶≤ а¶ЄаІЗථаІНа¶Яа¶Ња¶∞, а¶ђа¶Њ а¶Жа¶ЃаІЗа¶∞а¶ња¶Хඌථ а¶≤а¶Ња¶За¶ђаІНа¶∞аІЗа¶∞аІА а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඙ඌඐ а¶ХаІЛඕඌඃඊ? ඪඌයගටаІНа¶ѓ а¶ђа¶Њ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶ЫඌටаІНа¶∞аІЗа¶∞ ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶ЃаІЗа¶Іа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶Хඌප ටаІЛ а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶Є а¶∞аІБа¶ЃаІЗ а¶Ша¶ЯаІЗ ථඌ, а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶Ња¶°аІЗа¶ЃаІА а¶ђа¶Њ ථථаІНබථ а¶ЪටаІНа¶ђа¶∞ ටаІЛ ටඌа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶З, а¶ѓа¶Њ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ ථаІЗа¶З, а¶ЕථаІЗа¶Х а¶єа¶Њ ඙ගටаІНа¶ѓаІЗපаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗ යඃඊට а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ථඌа¶ЯаІНа¶ѓ а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ а¶ЬаІЛа¶ЯаІЗ а¶ђа¶°а¶Ља¶ЬаІЛа¶∞а•§
ටඐаІЗ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ а¶Ха¶≤аІЗа¶Ьа¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗප ථගඃඊаІЗ а¶Еа¶≠а¶ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ХබаІЗа¶∞ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНට ථаІЗа¶З, ඐගපаІЗඣට а¶За¶Йථගඃඊථඐඌа¶Ьа¶њ ථගඃඊаІЗ ටඌа¶∞а¶Њ а¶ђа¶ња¶∞а¶ХаІНа¶§а•§ ඃඌබඐ඙аІБа¶∞ ඐගපаІНඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶ЃаІН඙аІНа¶∞ටගа¶Х а¶Ша¶Яථඌ а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗ а¶Жа¶ЩаІНа¶ЧаІБа¶≤ බගඃඊаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Ха¶ња¶ЫаІБ බаІЗа¶Ца¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ බගа¶≤а•§ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞ පගа¶ХаІНа¶Ја¶ХබаІЗа¶∞а¶У а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Х а¶Ъඌ඙аІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Ж඙аІЛа¶Ј а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞аІЗа¶ХаІНඣගටаІЗ, а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶Ч ඕаІЗа¶ХаІЗа¶У, а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъපගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Ьධඊගට, а¶ђа¶ња¶Чට а¶Ха¶ѓа¶ЉаІЗа¶Х а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗ බаІЗа¶Ца¶Ыа¶њ, а¶Єа¶ЪаІЗටථ а¶Еа¶≠а¶ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ХබаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Еа¶Вප а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ЃаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗа¶ХаІЗ а¶Ха¶Ња¶∞а¶ња¶Ча¶∞а¶њ а¶ђа¶Њ а¶Ъа¶ња¶Ха¶њаІОа¶Єа¶Њ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ ථඃඊ, а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъපගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗа¶У බගа¶≤аІНа¶≤а¶ња¶∞ а¶Ха¶≤аІЗа¶Ьа¶ЧаІБа¶≤аІЛටаІЗ ඙ඌආඌа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Па¶ђа¶В а¶Па¶З а¶ѓаІЗ а¶ЯаІНа¶∞аІЗථаІНа¶° ටඌа¶∞ а¶Ђа¶≤а¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІВ඙ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶Ч ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞ ඁටаІЛ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආගට а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъපගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ а¶У а¶ђа¶Ња¶Ба¶ХаІБа¶°а¶Ља¶Њ-а¶ђа¶∞аІН඲ඁඌථ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ а¶ђа¶∞аІН඲ඁඌථ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶Љ ථගඃඊаІЗа¶У а¶Па¶Ха¶З а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ, ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶Ђа¶ња¶°а¶Ња¶∞ а¶≤а¶Ња¶Зථ а¶єа¶Ња¶∞а¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶∞а¶ХаІНටඌа¶≤аІН඙ටඌඃඊ а¶≠аІБа¶Ча¶ЫаІЗа•§ а¶Єа¶ђ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶ЄаІНඕගටග а¶ЦаІБа¶ђа¶З යටඌපඌа¶∞а•§ а¶Й඙ඌа¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶ѓ ථගඃඊаІЛа¶Ч ථගඃඊаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНඃ඙ඌа¶≤ а¶Єа¶Ва¶Шඌට ථගඃඊаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඃට ථගа¶Йа¶Ь඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Я а¶ђа¶Њ а¶Па¶ѓа¶Ља¶Ња¶∞ а¶Яа¶Ња¶За¶Ѓ а¶Ца¶∞а¶Ъ а¶Ха¶∞а¶Ыа¶њ, ටඌа¶∞ а¶≠а¶ЧаІНථඌа¶Вපа¶У а¶Па¶З а¶Єа¶ђ а¶ЃаІВа¶≤ а¶За¶ЄаІНа¶ѓаІБ ථගඃඊаІЗ а¶≠а¶Ња¶ђа¶≤аІЗ යඃඊට ඙а¶∞а¶ња¶ЄаІНඕගටගа¶∞ ඐබа¶≤ යටаІЗ ඙ඌа¶∞ටаІЛа•§
Have an account?
Login with your personal info to keep reading premium contents
You don't have an account?
Enter your personal details and start your reading journey with us
Design & Developed by: WikiIND
Maintained by: Ekhon Dooars Team