



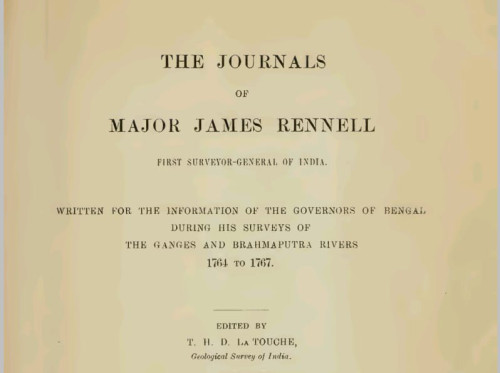








 সব্যসাচী দত্ত
সব্যসাচী দত্ত

বৈরাতি নাচ
অন্য সকলের মতই রাজবংশী জনজাতির জীবনে বিবাহ অত্যন্ত আনন্দঘন একটি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দু’টি হৃদয়ের সঙ্গে দু’টি পরিবার, তাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যার গুরুত্ব সমাজে অপরিসীম। একটি মেয়ে একটি ছেলে অনুঘটক ও মূল পাত্র-পাত্রী। রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েক প্রকারের বিবাহের প্রচলন রয়েছে। যেমন ফুল-বিহা, গাও-গোছ, পানি-ছিটা, পানি-সরপন, ছত্রদানী, ঘর সোঁধানী বিয়াও ইত্যদি। তাদের মধ্যে সবথেকে গ্রহণযোগ্য ও নিয়মিত বিবাহ পদ্ধতি হ’ল ‘ফুল-বিহা’। এই পদ্ধতি ফুল বিয়াও বা ফুলমারা বিহা নামেও পরিচিত। এই বিয়েতে একজন ছেলে একজন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করে পরিবারের সম্বন্ধ অনুযায়ী। এই বিবাহ সম্পর্কে চারুচন্দ্র স্যান্যাল তাঁর বিখ্যাত ‘রাজবংশীস অফ নর্থবেঙ্গল’ বইতে লিখেছেন—This is the form of marriage generally adopted and accepted by the society as a real marriage. In this form the boy always married to virgin girl. The marriage settled by the elders through a karca (Match Maker). In this form the marriage crown (Phul or Sehera) is bed on the head of the bride and bride-groom. In no other form this is done. The word ‘Phul’ denotes a virgin and also the marriage crown. A priest or Odhikary is esseintial in the type of marriage. A Kamrupi Brahman whose ancestors are said to have been recruited by Biswa Singha from Srihatta (Sylhet), is generally employed in advanced families. এর সঙ্গে Karoa সম্পর্কে লিখেছেন—“A ‘Karoa’ is a matchmaker like the ‘Ghottocks’ of South Bengal, he is usually a Rajbanshi. He carries on his usual occupation of cultivation and acts as a match maker as a side business whenever called upon to do so. A very near relatives of the boy or of the girl dose not act as a ‘Karoa’…”
বিবাহের এই পদ্ধতি অবলম্বন করেই সৃষ্টি হয়েছে ‘বৈরাতী নৃত্য’। সম্পূর্ণ নৃত্যানুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় বিয়ের গান ও নাচকে নির্ভর ক’রে। একটি সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে সংগ্রহ ক’রে এই নির্মাণ যে খুব বেশি পুরোনো, তা কিন্তু নয়। অনুমান করি আজ থেকে কম বেশি একশ বছর আগে কোচবিহার জেলার খাগড়াবাড়ি অঞ্চলে পালাকার-অভিনেতা প্রয়াত ব্রজেন্দ্র রায় ‘সতী-বেউলা’ পালায় বিয়ের গান ব্যবহার করেছিলেন। যা সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে গ্রহণ ক’রে পালায় নাটকীয়ভাবে ব্যবহার করেছিলেন। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে বৈরাতী নৃত্য স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপনযোগ্য নাটকীয় রূপ পেতে শুরু করে। এবং খুব দ্রুত তা বদলে গিয়ে আধুনিক নাট্য নির্মাণের গুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে। গান নাচ অভিনয় সবকিছু মিলিয়ে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল একটি নাট্যধারা বহমান। আরও বিশেষ করে বললে বলতে হয় ‘গীতিনাট্যধারা’। প্রাচীন উৎসবকে নির্ভর ক’রে বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের নাট্য নির্মাণ ঘটেছে, তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।
এবার প্রশ্ন আসছে ‘বৈরাতী নৃত্য’ কেন বলা হচ্ছে বহমান এই ধারাটিকে? ‘বৈরাতী’ কথাটির অর্থই বা কী? রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে বিবাহ অনুষ্ঠানে যে সধবা মহিলারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে থাকেন তাঁরাই বৈরাতী বলে গণ্য হন। আমরা যাঁদের ‘এয়ো’ বলি। রাজবংশী সমাজে তাঁরাই হলেন বৈরাতী। বৈরাতীগণ গেয়ে নেচে বিবাহ অনুষ্ঠানকে উৎসবে পরিণত করেন। সেই উৎসবের একটি অংশ যেহেতু অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করা হয় তাই এটি বৈরাতী নৃত্য। বৈরাতী নৃত্যের উপস্থাপনায় একটি সম্পূর্ণ নাট্য নির্মাণের প্রয়োগ রয়েছে। নাট্য নির্মাণের মূল যে তিনটি উপাদান অর্থাৎ Action, Scene, Voice – সবটাই বৈরাতী নৃত্যে উপস্থিত। Action নির্মাণ করে গতি, ছন্দ, নাটকীয়তা। Scene তৈরি করে দৃশ্যসজ্জা, আর Voice গীত, সংলাপের মাধ্যমে ছবির পর ছবি ফুটিয়ে তুলতে থাকে। আবার ভরত মুনি নাট্য শাস্ত্রে বলেছেন আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য, স্বাত্তিক অভিনয়ের কথা। যা বৈরাতী নৃত্যে বর্তমান। এবার বৈরাতী নৃত্যের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক ঘটনাটি সত্য কিনা।
মঞ্চসজ্জাঃ ভরত নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী মঞ্চসজ্জা আহার্য্য অভিনয়ের অন্তর্গত। বৈরাতী নৃত্যে মঞ্চসজ্জায় বিয়ের আসর ফুটিয়ে তোলা হয়। দেড় থেকে দু’ফুট আন্দাজ চারটে কলাগাছ চার টুকরো বাঁশের দ্বারা যুক্ত করা হয় যাতে কলাগাছের চারাগুলি পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তা স্থাপন করা নিম্ন-মধ্য মঞ্চে (Down-Centre Stage) উচ্চ-ডান ও মধ্য-ডান মঞ্চ (Up-Right Stage & Middle- Right Stage) জুড়ে বসেন বাদ্যযন্ত্রীগণ ও গায়ক গায়িকারা। বাকী মঞ্চে চলে নৃত্য ও অভিনয়।
উপস্থাপনঃ দর্শক সম্মুখে মঞ্চ-উপস্থাপন ভরত নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী আঙ্গিক-বাচিক-স্বাত্তিক অভিনয়ের অন্তর্গত। বৈরাতী নৃত্যের শুরুতেই বাদ্যযন্ত্রী ও সঙ্গীত শিল্পীরা প্রবেশ করেন। বাদ্যযন্ত্রীদের বরণ করা হয় গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকে সানাই, ঢোল, আকড়াই, কাড়া-নাকাড়া, দোতারা ইত্যাদি। এরপর বৈরাতীগণ কন্যাকে মঞ্চে নিয়ে আসেন। হলুদ দ্বারা অঙ্গ রচনা করা হয় গীত, নৃত্য ও অভিনয়ে। এরপর সময় আসে বরের প্রবেশের। কন্যাকে নেপথ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। একসময় কন্যা কাঁদতে থাকে। কন্যাকে আদর করা হয়। কন্যার বন্ধু, বৈরাতী প্রত্যেকেই তার সঙ্গে নানা ভাব বিনিময় করেন। এই সময়ের উপযুক্ত আচরণ করেন। এই সময়ে গাওয়া হয় গীত। তার পদ অনেকটা এইরকম—
কইনা কাইন্দ না কাইন্দ না ঘরে
বিয়ার গাড়ি ওই বুঝি আইসে
ওই শোনা যায় আধা পথত
করেকার বাইজ পড়ে
কইনা কাইন্দ না কাইন্দ না কাইন্দ না ঘরে
ভটভটি বুদারুর মাও
আইসে কেনে জোগাড় দাও
বরণ বরের চাইলন বাতি নেও আগে দুয়ারে
ওই আসছে বিয়ার গাড়ি
ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুর করি
করেকা বাজে ঢোলকি বাজে
কইনা কাইন্দ না কাইন্দ না কাইন্দ না ঘরে…।
তবে গায়ে হলুদের অন্য গানও রয়েছে। বরের প্রবেশের সময় মেয়ের বাড়ির মূল কর্তা (সাধারণত মেয়ের পিতা) সমগ্র ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। বিয়ের বাজনা বাজাতে থাকেন বাদ্যযন্ত্রীরা। বর প্রবেশ করে। বরের সঙ্গে আসে বরযাত্রী ও বরের খাস বন্ধুরা। তারা আসে বরের আগে নাচতে নাচতে। বরের সঙ্গে আসে গোটা মাছ, মিষ্টির হাড়ি। বরকে বরণ করেন বৈরাতীরা। গীত, নৃত্য, অভিনয়ে ফুটে ওঠে দৃশ্যটি। বরকে বরণ করা হয় গীতের মাধ্যমে—
বরণ বরে চাইলন চায়
কইনারে নাকের নোলক ঢুল খেলায়
ওকি ওরে দেওরা দুলারী আই মোর
আচ্ছা বরণ বরিয়া নেও রে।
মাকিলা বাঁশের চাইলন বাতি
নবীন বয়সের বৈরাতী
ওকি ওরে ঢোল বাজে ক্যারেকা বাজে সানাই বাজে রে
আচ্ছা বরণ করিয়া নেও রে।
সারা মঞ্চ জুড়ে বিয়ের পরিবেশ। বর এসে আসরে বসে। কন্যাকে আনা হয়। পুরোহিত আসেন। বিবাহ কার্য চলে। পুরোহিত কন্যাপক্ষ ও পাত্রপক্ষ দু’তরফ থেকেই দক্ষিণা আদায় করেন। বরের সখা নানা ধরণের হাস্য উদ্রেককারী ঘটনা ঘটাতে থাকে। দু’পক্ষের লোকজনের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়। মজা হয়। বিবাহকার্য সমাধা হয়। কন্যাপক্ষের মেয়েরা বরকে নিয়ে মজা করে। খুনসুটি করতে থাকে। এই সময়ের গানের কথাগুলিও খুব মজার। পদ অনেকটা এইরকম—
ছিকো ছিকো মাই মরিয়া না যাই
ওটা কেমন দুলা ভাই
ছিকো ছিকো মাই মরিয়া না যাই
ওটা দুলাহার মাথাটা
ঢাল কাউয়ার বাসাটা
ছিকো ছিকো মাই মরিয়া না যাই
ওটা দুলাহার চখু দুইটা
হলদি থুবার কৌটাটা
ছিকো ছিকো মাই মরিয়া না যাই
ওটা দুলাহার পিটিখান
কাপড় ধোয়ার পিড়াখান
ছিকো ছিকো মাই মরিয়া না যাই।
এইভাবে গানের সময় বরকে কনের বন্ধুরা বিভিন্ন রকমভাবে উত্যক্ত করতে থাকে। গানের কথা অনুযায়ী অভিনয় করে ও বরের সঙ্গে তেমনই আচরণ করে।
এরপর পিতৃগৃহ থেকে কন্যার বিদায় নেওয়ার পালা। বরের সঙ্গে নতুন জীবনে প্রবেশ করবে সে। যে বাড়িতে বেড়ে উঠেছে সে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে অজানা অচেনা এক বাড়িতে। আনন্দের পরিবেশে নেমে আসে বিষাদের সুর। মাতা-পিতা-গুরুজনে যুগলে প্রণাম ক’রে বর ও কনে। বৈরাতীরা গেয়ে ওঠেন—
ধীরে বোলান গাড়ির গাড়োয়ান
আস্তে বোলান গাড়ি
আরেক নজর দেখিয়া নাও মুই
দয়াল বাপের বাড়ি রে গাড়িয়াল
আস্তে বোলান গাড়ি।
বিষাদের ছোঁয়া দর্শক-শ্রোতাদের মনেও। কন্যার বিদায়ের সঙ্গে নৃত্যাভিনয়েরও সমাপ্তি ঘটে। আর আমরা যাঁরা বিষয়টি উপভোগ করি আসনে বসে, পাই পূর্ণতার তৃপ্তি।
পোশাক ও রূপসজ্জাঃ আহার্য্য অভিনয়ের অন্যতম দু’টি বিষয় পোশাক ও রূপসজ্জা। বৈরাতী নৃত্যে পোশাক ও রূপসজ্জা ব্যবহার করা হয় চরিত্র অনুযায়ী। বৈরাতীরা পরেন লালপাড়-সাদা শাড়ি। কন্যার মাথায় থাকে শোলার তৈরি শ্যাহেরা এবং বরের মাথায় থাকে টোপর। পুরুষ চরিত্ররা ধূতি পাঞ্জাবি ব্যবহার করেন। রূপসজ্জার জন্য বিভিন্ন রকম রঙ, পাউডার, ফাউন্ডেশন, আলতা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। বাঁশের তৈরি বরণ ডালায় থাকে প্রদীপ, ফুলঝুড়ি(মুছি), কলা, পান-সুপারী, হলুদ, ধান ইত্যাদি।
বৈরাতী নৃত্যের উপস্থাপনটি লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারি সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে রয়েছে নাটকীয়তা। সে নাটকীয়তা অন্য কোনও নৃত্যানুষ্ঠানে দেখা যায় না। যে কোনও জনজাতি ও উপজাতি নৃত্য পরিবেশনায় সাধারণত কিছু নাট্য থাকেই। আর বৈরাতী নৃত্যে রয়েছে একটি নাট্য কাহিনি। যা অন্য সব নৃত্যের থেকে আলাদা। নাচ,গান,অভিনয়ে সম্পূর্ণ একটি উপস্থাপনা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে রাজবংশী বিবাহ অনুষ্ঠানে অধিকারী মহাশয়ের ভূমিকা প্রধান। যাঁকে ছাড়া বিবাহকার্য সম্ভব নয়। এই লেখায় উল্লিখিত গীতসমূহ ছাড়াও আরও অনেক গান আছে বলা বাহুল্য।
(ক্রমশ)
Have an account?
Login with your personal info to keep reading premium contents
You don't have an account?
Enter your personal details and start your reading journey with us
Design & Developed by: WikiIND
Maintained by: Ekhon Dooars Team