

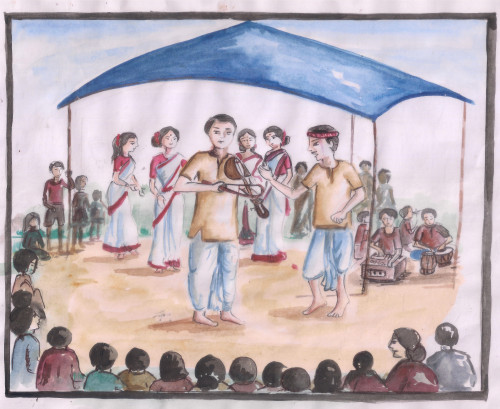
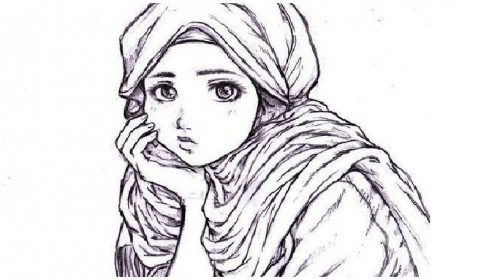


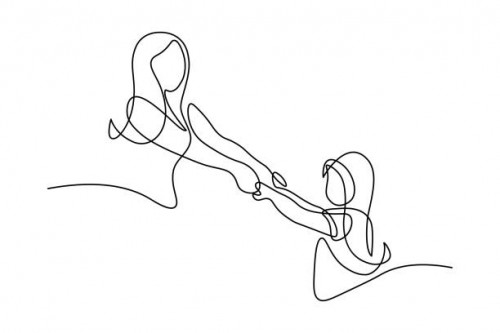


 প্রদোষ রঞ্জন সাহা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

হিমালয়ের কথা না হয় আলাদা, উত্তরের বাকি সমতল অংশেও বৈশাখ মানে কিন্তু গ্রীষ্মকাল নয়। কোনওকালেই ছিল না, আজও নয়। চল্লিশ-পঞ্চাশ বা পঁচাত্তর বছর আগে পশ্চিম বাংলার এই প্রান্তে বসন্ত শেষে যে শীতের নতুন করে প্রকোপ দেখা যেত তাতে একটি প্রবাদ এদিককার গ্রামীণ লোকমুখে চালুই ছিল – ‘চোত্রি মাসে হালের গরু বেচিয়া ল্যাপ-ক্যাথা কেনা লাগে’। এই হিমেল রেশ কিন্তু আজও এখানে চলে বৈশাখ জুড়ে। ঝড়-বৃষ্টির যুগলবন্দীর মাঝে কখনও কটা দিন রোদ্দুরের যদি বা দেখা মেলে তো তার সামান্য তাপেই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে উত্তরের নরমসরম মানুষগুলো। তাদের সে কষ্ট দেখে উদ্বেল হয়ে ওঠেন প্রকৃতিদেবী, ফের দিনভর আকাশ জুড়ে মেঘের গুড়গুড়, ফের রাতভর বারিধারা। ফলত ফ্যানের সুইচ অফ, চলন্ত বাসের জানালায় হিমেল শিরশিরানি, সন্ধ্যার পরে মোটরবাইকে চাপলে গায়ে গরম কাপড়, রাত্তিরে গায়ে হাল্কা চাদর ইত্যাদি ইত্যাদি।
গ্রীষ্মের দাবদাহে বৃষ্টিহীনতায় দক্ষিণের বাংলা যখন খাবি খায় তখন উত্তর প্রান্তের মনোরম আবহাওয়ার এই বৈপরীত্য আসলে ভীষণ বাস্তব ও চিরন্তন। তাই বলে কি সেখানে গ্রীষ্ম আসে না? আলবত আসে, কিন্তু মাসখানেক দেরিতে আসে। অখণ্ড দেশ বা রাজ্যের কথা বললে কিন্তু এই সামগ্রিক ছবির কথা মাথায় রাখতে হবে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য যদি আমাদের দীর্ঘলালিত সংস্কৃতি হয় তবে উষ্ণ উপকূল থেকে হিমেল শৃঙ্গ পর্যন্ত সব জলবায়ুর কথাই সমান ভাবে ভাবতে হবে। একের জীবন-অভ্যেস অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে তা হতভাগ্য বৈষম্যের সামিল হয়ে দাঁড়ায়। তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, একি তবে নিছক অজ্ঞানতা? নাকি অবজ্ঞা? বা অবহেলা?
আসলে গোলযোগটা বাধে কিন্তু এই অবুঝ চাপিয়ে দেওয়া থেকেই। বাংলার উত্তর ও দক্ষিণের গ্রীষ্মাবকাশ কখনও এক হতে পারে না – কলকাতায় বসে এই সামান্য সারসত্যটি না বুঝতে পারলে কোথাও বিশাল কোনও ক্ষতি হয়তো হয়ে যায় না, কিন্তু জলীয় বাষ্পের মতোই পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে বিরক্তি-হতাশা-ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে উত্তরে, দীর্ঘকালীন বঞ্চনার প্রশ্নগুলি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, আবেগের চোরা স্রোতে স্লুইস গেটের ছিটকিনি নড়বড়ে হয়ে যায়, অকাল প্লাবনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। আজ যদি উত্তরের কোনও ছাপোষা বাসিন্দা সত্যিই প্রশ্ন তোলেন, গত পঁচাত্তর বছরে মুখ্যমন্ত্রিত্ব দূরের কথা, সাহিত্য-সংস্কৃতি-ক্রীড়া–বিনোদন-রাজনীতি-প্রশাসন যে কোনও ক্ষেত্রে যে কোনও রাজ্যস্তরের সংস্থা বা দলের প্রধান কজন হতে পেরেছেন বাংলার উত্তর প্রান্ত থেকে? নাকি এদিকে থেকে কাউকে সেরকম যোগ্য পাওয়াই যায় নি কোনওকালে? আজও কলকাতার সীলমোহর না পেলে কোনও ক্ষেত্রেই কোনও কলকে মেলে না কেন বলুন তো? বাংলা বানান থেকে শুরু করে ভাষা-আচার-পোশাক সবকিছু কি কলকাতা থেকেই ঠিক করে দেওয়া হবে? উত্তরের প্রান্তিক ভূমি কি আজও চাকরির পানিশমেন্ট পোস্টিং কিংবা নেতা-মন্ত্রী-অমাত্যদের মৃগয়া ক্ষেত্র হিসেবেই থেকে যাবে?
এই সব বেমক্কা প্রশ্ন উত্থাপনকারী উত্তরের সেই ছাপোষা মানুষটিকে আপনি কী নামে দেগে দেবেন? বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির অর্বাচীন প্রতিনিধি? নাকি বিরোধী দলের অবিমৃষ্যকারী দালাল? কিন্তু ইতিহাস তো বলে যেখানে যেখানে স্বাধিকারের প্রশ্নে হাঁড়ি আলাদা করবার জিগির উঠেছে সেখানেই মেলে সুদীর্ঘ বঞ্চনা-অবহেলা ও শোষণের বোটকা গন্ধ। বাংলাকে কিছুতেই ভাগ হতে দেব না বলে আবেগে ভাসিয়ে যাঁরা যাঁরা এতদিন সমতলের ভোটব্যাঙ্ক সুনিশ্চিত করেছেন, পাহাড়ি মানুষগুলিকে তাঁরা আদৌ এক ইঞ্চিও হৃদয়ের কাছাকাছি আনতে পেরেছেন কিনা একবার খোঁজ নিয়ে দেখবেন তো! বরঞ্চ দেখি যে সব পাহাড়ি নেতারা কলকাতার শাসকের সঙ্গে সখ্যতা বাড়িয়েছেন তাঁদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে পাহাড়ের সাধারণ মানুষ, এক আধবার নয় বারবার, ইতিহাস সাক্ষী! এর কারণগুলি খুঁজে দেখেছেন কেউ?
আজ বিরোধীরা সুযোগের সদব্যবহার করতে বিভাজনের সলতেয় অগ্নিসংযোগ করবেন সেটাই তো স্বাভাবিক! কিন্তু যদি সম্ভব হয় আরো খোঁজ নিয়ে দেখবেন উত্তরের সাধারণ মনন প্রকৃতই কী চায়! বিভাজন যদি সমাধানের রাস্তা না হয় তবে অবদমনও সঠিক পথ নয়। যে সদর্থক ভাবনা থেকে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, উত্তরকন্যার সূচনা হয়েছিল তার সঠিক বাস্তবায়ন হলে কি আজ সত্যিই এই বিভাজনের ধূম্রজাল ঘনায়িত হওয়ার সুযোগ মিলতো? এটা তো আজ প্রমাণিত সত্য যে প্রান্তিক উত্তরের প্রকৃত উন্নয়ন চাইলে কেবল যে পাকা রাস্তা বা সেতু বানালেই হবে না, কেবল রাজধানীর ফরমান জারি করে দিলেই চলবে না, কেবল সদলবলে সপরিবারে ঘন ঘন বেড়াতে এলেই চলবে না! উত্তরের হৃদয় জিততে গেলে আগে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে সেখানকার জল-জঙ্গল-জনসত্তাকে। বুঝতে হবে, বাংলার উত্তরে বৈশাখ মানেই কিন্তু গ্রীষ্মকাল নয়!
Have an account?
Login with your personal info to keep reading premium contents
You don't have an account?
Enter your personal details and start your reading journey with us
Design & Developed by: WikiIND
Maintained by: Ekhon Dooars Team