








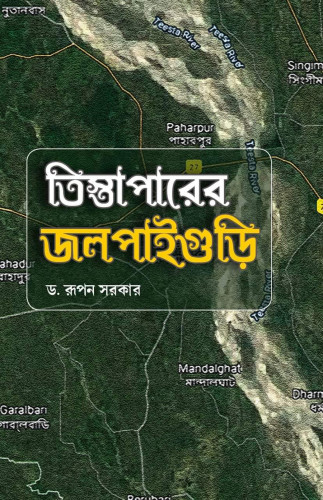


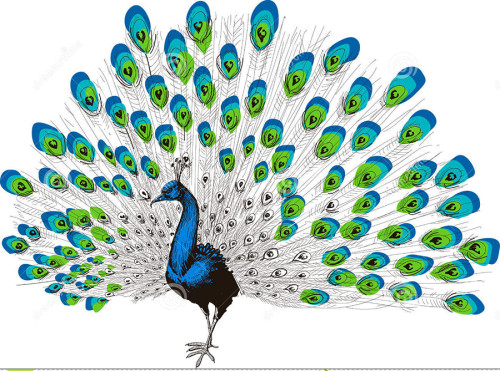





 সব্যসাচী দত্ত
সব্যসাচী দত্ত

প্রতিটি অঞ্চলে স্থানীয় কিছু মানুষ থাকেন যাঁরা মনের আনন্দে সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক কাজের সঙ্গে জুড়ে থাকেন আজীবন। সেসব কাজ মনে-প্রাণে-মস্তিষ্কে যে অনুরণন তোলে তা ক্রমশ শিল্পের প্রতি, সংস্কৃতির প্রতি দায়িত্ববান করে তোলে। সে কর্তব্য তাঁরা পালন করেন আজীবন। কোনও সম্মানের বা পুরষ্কারের অপেক্ষা করেন না, সত্যি অর্থে আকাঙ্খা করেন না। যেমন শ্বাস নেওয়া প্রয়োজন খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন বেঁচে থাকবার জন্য, তেমনই সে কাজ খুব দরকারী তাঁদের কাছে। তাঁদের জন্যই সমাজের অনেক কিছু হারিয়ে যেতে পারে না। কোচবিহারে প্রচলিত ষাইটল গান, কাতিপূজার গান, জাগ গান—ইত্যাদি বিভিন্ন ধারার আনুষ্ঠানিক উপস্থাপনাকে মঞ্চে তুলে নিয়ে এসেছেন গ্রামীন লোকসংস্কৃতিঅন্ত-প্রাণ এমন একজন মানুষ অমূল্য দেবনাথ। পুঁটিমারীতে বড় হয়ে ওঠা অমূল্য ছেলেবেলা থেকেই গ্রামে প্রচলিত বিভিন্ন ধারার সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা দেখেছেন। দেখেছেন বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান। যেগুলি তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছে। তাদের প্রভাব তাঁর মনে আজও আছে। পিতা গদাধর দেবনাথ মা কুসুম দেবনাথের সন্তান পরিবারের সূত্রেই পেয়েছেন দারিদ্র। প্রথাগত লেখাপড়াতেও স্কুলের গন্ডি পেরুতে পারেননি। সামান্য কৃষিকাজের ওপর নির্ভর তাঁদের জীবিকা। অমূল্যর জ্যাঠামশাই মহিম দেবনাথ ছিলেন কুশান পালাগানের মূল গীদাল। সব মিলিয়ে ছেলেবেলা থেকেই সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে সাথী ক’রে বড় হয়েছেন। কিন্তু দারিদ্র সে পথে ভীড়তে দেয়নি। আহারের সন্ধানে ঘুরতে হয়েছে এদিক ওদিক। কিছুদিনের জন্য ছিলেন ভুটানে। বছর তিনেক কাজ করেছেন সেখানকার জন-কারিগরি বিভাগে ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে।
বাড়ি ফিরতেই সন্তানকে থিতু করতে বাবা-মা বিয়ের আয়োজন করতে শুরু করলেন। তাতে অমূল্যর একেবারেই আগ্রহ ছিল না। বারবার পালিয়ে যাচ্ছিলেন এদিক ওদিক। কিন্তু শেষরক্ষা হ’ল না। পরিবারের পীড়াপীড়িতে বিয়েটা করতেই হ’ল। বিয়ের পর শুরু হ’ল খুব আর্থিক সংকট। কারণ বিয়ের পর তিনি আর ভূটানে ফিরে যাননি কাজের জায়গায়। অভাবের সঙ্গেই শুরু হয়ে গেল প্রবল দাম্পত্য কলহ। নাটাবাড়িতে আধিয়ার হিসেবে রইলেন কিছুদিন। তাও বছর দুয়েক। বউয়ের সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে ১৯৯০সালে ভেটাগুড়িতে চলে এলেন। নাটাবাড়ির সম্পত্তি বিক্রি করে অল্প কিছু জমি কিনলেন। চাষ-আবাদ করে জীবন অতিবাহিত করার সংগ্রাম চলতে লাগলো। লেখাপড়া তো কেবল স্কুল জীবন পর্যন্ত। প্রথমে লালবাহাদূর শাস্ত্রী বিদ্যাপিঠ। তারপর চৌপথি কমল্পিট বেসিক স্কুল। দাম্পত্য জীবন সুখের হ’ল না। ক্রমশ পারিবারিক অশান্তি নিত্য দিনের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। তাই এই দাম্পত্য সংসার থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে লাগলেন। তিনি ভালো থাকার পরিসর খুঁজে পেলেন প্রচলিত সংস্কৃতিতে ডুবে গিয়ে।
দেশভাগের গভীর প্রভাব সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে আমরা দেখেছি। বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ বাধ্য হয়েছেন ভিটেমাটি ছেড়ে এদেশে চলে আসতে। সত্তর-একাত্তর সালে এই সংখ্যাটা এত বেশি দাঁড়ালো যে তাতে বাংলাদেশ থেকে আসা বাঙালীর সংখ্যা (যাদের স্থানীয় মানুষ ‘ভাটিয়া’ বলছেন) বেড়ে গেল অনেক। স্থানীয় সংস্কৃতি সেকারণে যেন চ্যালঞ্জের সামনে পড়ে গেল! এসময় অমূল্য উপলব্ধি করলেন আপনার ভাষা, যে ভাষা মায়ের স্তন্য সুধার সঙ্গে প্রাপ্ত তা হারিয়ে যাচ্ছে। কোচবিহারের স্থানীয় মানুষ কথা বলেন যে ভাষায় তা কামতাপুরি ভাষা নামে পরিচিত। দেশি ভাষাও বলেন। এই ভাষা কামরূপ প্রভাবিত। সেই ভাষাটা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। নেপালীর সঙ্গে নেপালীর দেখা হলে তাঁদের নিজেদের কথ্যভাষাতেই কথা হয়। বিহারীর সঙ্গে বিহারীর দেখা হ’লে তাঁদের ভাষাতেই কথা হয়। অথচ বাংলা ভাষা এমন জাঁকিয়ে বসেছে যে কামতাপুরী যাঁদের মাতৃভাষা তাঁরা দুজন নিজের ভাষায় কথা বলেন না। অনেক সময় সে ভাষায় কথা বলতে তাঁরা লজ্জিত হন। অথচ ভাষা ও সংস্কৃতি হারিয়ে গেলে মানুষের অস্তিত্বই যে বিপন্ন হয়ে পড়বে। এই আশঙ্কা হয় তাঁর। তিনি এবিষয়ে আলোচনা করেন ছেলেবেলার দু’তিনজন বন্ধুর সঙ্গে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সকলে মিলে বাংলার ১৪০০ সালে (ইংরাজী ১৯৯৬) হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি বিষয়ে একটি মেলার আয়োজনের পরিকল্পনা করেন। তাতে গ্রামীন প্রচলিত খেলার প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী (যেমন স্যাকা, প্যালকা, সিদলের আওতা, শামুকের হোড়পা, কবুতরের কষা, ঠাকুর কালাই ডাল, দই-চুড়া ইত্যাদি) তার সঙ্গে হুকা, গুয়া পানের ব্যবস্থাও রাখা হবে। প্রদর্শনীতে ধান, ডাল, কাথা, মাছমাড়ার যন্ত্রপাতি, শিকারের শুয়োর মারার জাল, ডাহুক, বগা, কুমারের চাক, বাঁশের জিনিসপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, লাঙল ইত্যাদি জীবন যাত্রার সবকিছু থাকবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভাওয়াইয়া, চোর-চুন্নী, মেয়েলি ব্রত অনুষ্ঠান (ষাইটল, কাতিপূজা, হুদুম দেও) ছেলেদের আচার-অনুষ্ঠান (কান্দেবের নাচ, গোরক্ষনাথ, জাগ-গান, চণ্ডি নাচ, জুগী গান, চারযুগের গান) ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে। মেলা হবে তিনদিনের। কিন্তু তিনমাস আগে থেকেই খেলার প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাতে চেমুনাতি, হা-ডু-ডু, আটঘরিয়া, ষোলপাইটা, চকরচাল, তেপাইতা, ঠুস, লাঠিখেলা, দাড়িয়া বান্দা, ছু-বুড়ি ইত্যাদি খেলাগুলির প্রতিযোগিতা হয়। খেলাগুলি চলতে চলতে তাদের ফাইনাল প্রতিযোগিতা হয়েছে মেলার সময়। ভেটাগুড়ির ফুটবল খেলার মাঠে মেলা হয়েছিল। খুব জমে উঠেছিল এই মেলা। মেলার নাম তাঁরা দিলেন ‘কুচবিহারী মেলা’। ভেটাগুড়ি তো বটেই এই মেলায় প্রচুর জনসমাগম হ’ল দিনহাটা, কোচবিহার সহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে।
অনেক প্রখ্যাত মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। সেই প্রথমবার কোনও অনুষ্ঠানে অতিথি বরণ করা হ’ল ‘বৈরাতি নৃত্য’ পরিবেশনের মাধ্যমে। যা আজ এতদঞ্চলের অনেক অনুষ্ঠানের উদ্বোধনেই পরিবেশিত হয়। প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ও সরকারী উচ্চপদাধিকারী সুখবিলাস বর্মাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁরা। তিনি খুব ব্যস্ত সেসময়। তাঁদের বলেন, অনেক কাজ আছে। তাই খুব অল্প সময়ের জন্য আমি উপস্থিত থাকতে পারবো। তিনি মেলায় এলেন তারপর মেলার পরিবেশ ও আয়োজন দেখে উচ্ছসিত হয়ে বললেন, অমূল্য আমি তিনদিনই থাকব। আর মেলার সমস্ত কিছু ভিডিও করবো। তার সমস্ত খরচ আমার। তোমাদের আর যা কিছু প্রয়োজন হবে আমায় বলবে। কারণ এমন একটি উদ্যোগের ডক্যুমেন্টেশন অত্যন্ত জরুরি।
কুচবিহারী মেলার খরচের অনেকটাই উঠেছিল কোচবিহার জেলার বিভিন্ন গ্রামপঞ্চায়েতের আর্থিক সহায়তায়। এছাড়াও পাওয়া গিয়েছিল ব্যক্তিগত সহায়তা। কিছু ছোট কোম্পানী ডোনেশনের মাধ্যমে কিছু টাকা প্রদান করেছিল। এই মেলার খরচ হয়েছিল পঞ্চান্ন হাজার টাকা। সব মিলিয়ে আর্থিক সহায়তা পাওয়া গিয়েছিল চল্লিশ হাজার টাকা। বাকী খরচ নিজেরাই বহন করেছিলেন। রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক শিক্ষিকা, সামাজিক ব্যক্তিত্বরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। যোগেশ বর্মন, দীনেশ ডাকুয়া সহ বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এই মেলার আয়োজনের জন্যেই।
এই মেলায় কৃতি মানুষদের দেওয়া হয় ‘ভালেটা’ উপাধি। যার অর্থ ‘অনেক বড়’। হরিশ পাল, সুখবিলাস বর্মা এই উপাধিতে ভূষিত হন। যুগান্তর ও বসুমতী পত্রিকায় এই মেলার প্রতিবেদন প্রতিদিন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। মেলার আয়োজন এতই সফল হ’ল যে তাঁরা খুব উৎসাহিত হলেন। ঠিক করলেন কোচবিহার জেলার প্রতিটি সাবডিভিশনে একটি করে মেলা হবে। দ্বিতীয় বছর ‘কুচবিহারী মেলা’ হ’ল বাণেশ্বরে। ‘ভেটাগুড়ি বিদ্যাসাগর সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি’ নামে একটি সংগঠন স্থাপনা ক’রে এই মেলার আয়োজন করা হয়। তৃতীয় বৎসর মাথাভাঙায় করা হয় এই মেলা। চতুর্থ বছর মেলা করবার আয়োজন হয়েছিল তুফানগঞ্জে। কিন্তু একটি রাজনৈতিক দলের কিছু কিছু মানুষ বাধা দেওয়ার জন্য এই মেলা সেখানে করা গেল না। বলা হ’ল এই মেলার উদেশ্য বিশেষ সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক স্বার্থে। এতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্ন হ’তে পারে। স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হ’তে পারে। আদতে অমূল্য বা তাঁর বন্ধুদের এমন কোনও ভাবনাই ছিল না। তাঁরা চেয়েছিলেন লুপ্ত হতে যাওয়া ভাষা সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে। তার নিয়মিত চর্চা যেন থাকে। ভাবনা ছিল কোচবিহারের পর জলপাইগুড়ি এবং অন্যান্য জায়গায় হবে। শুধুমাত্র ভুল বোঝার কারণে, অমূলক ভাবনার কারণে এমন একটি সুন্দর উদ্যোগ বন্ধ হয়ে গেল। এরপরেও জটেশ্বরে ‘উত্তরবঙ্গ মেলা’র আয়োজন করা হয়েছিল। অমূল্যর পরিকল্পনায় এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন জুগলকিশোর রায়গীর। তিনি ছিলেন সমতা পার্টির নেতা। তিনি গঠন করেছিলেন ভূমিপুত্রদের রাজনৈতিক দল ‘উজ্জাস পার্টি’।
‘কুচবিহারী মেলা’ রাজবংশী সংস্কৃতিতে অনেক পরিবর্তন নিয়ে এল। বদলে দিল অমূল্য-র জীবনও। বৈরাতি, সাইটল, কাতি পূজা, চন্ডি নাচ আচারধর্মী অবস্থান থেকে উঠে এল মঞ্চে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পাওয়া শুরু হ’ল তাঁদের। সুখবিলাস বর্মার উদ্যোগে ‘আব্বাসউদ্দীন স্মরণ সমিতি’-র আয়োজনে অমূল্য-র নেতৃত্বে অনুষ্ঠান পরিবেশন করে বৈরাতী, সাইটল, কাতি পূজা, চণ্ডি নাচ, গোরক্ষনাথ, সোনা রায়ের দল। খুব সাড়া ফেলল সে অনুষ্ঠান। সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সে সময়ের সচিব চন্দন চক্রবর্তী। তিনিও এই অনুষ্ঠান দেখে অভিভূত হন। এরপর তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের আমন্ত্রণে কোলকাতার কাছে ছিট-কালিকাপুরে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন শিল্পীরা অমূল্য-র নেতৃত্বে। এই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই ষাইটল সম্রাজ্ঞী ফুলতি গীদালী পরিচিতি পেতে শুরু করলেন। সরকারী বেসরকারী অনেক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেতে লাগলেন। ফুলতি বর্মণের উত্থান অমূল্যর উদ্যোগেই। অমূল্য কামতাপুরী ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করলেন। পত্রিকার নাম দিলেন ‘কানিয়াল’। তাঁর কবিতার বই ‘নিলুয়া দেওয়ার তলত’ খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু সেসময় বদলে যেতে শুরু করেছিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি। অতুল রায়ের নেতৃত্বে কামতাপুর পিপলস পার্টি বিভিন্ন দাবীতে আন্দোলন শুরু করল। কে এল ও-র উদ্যোগে শুরু হয়ে গেল বিচ্ছিন্নতাবাদী মারদাঙ্গার আন্দোলন। পুলিশ প্রশাসন কোমড় বেঁধে লাগল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে। শুরু হ’ল ধরপাকর। অমূল্য ও তাঁর বন্ধুরা ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন, কেবল যদি সন্দেহের বশে গ্রেফতার করা হয় তাঁদের তবে তো খুব মুশকিল। ‘কানিয়াল’ পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হ’ল। কবিতার বইও আর নতুন ক’রে ছাপা হ’ল না। তবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন চলতেই থাকলো। তিনি পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক দল তৈরি করলেন। ছেলেরা দলবেঁধে পরিবেশন করেন কান্দেবের গান, গোরক্ষনাথের গান, দখিন রায়ের গান, চণ্ডি নাচ। বলা বাহুল্য এই সবগুলি গানের সঙ্গে নাচ ও অভিনয়ও মিশে থাকে। আর মেয়েরা দলবেঁধে পরিবেশন করেন বৈরাতি নাচ, চণ্ডি নাচ, কাতিপূজার গান, সাইটল গান ও নাচ। দল নিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চল তো বটেই তার বাইরে দিল্লি, সিকিম, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট সহ অন্যান্য রাজ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।
পরিচিতি হয়েছে। নেতা মন্ত্রী সরকারী কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে ওঠা-বসাও হয়েছে। কিন্তু জীবন থেকে যায়নি দারিদ্র। স্ত্রী, তিন সন্তান, পিতা-মাতাকে নিয়ে খুব কষ্টে জীবন অতিবাহিত করেছেন। কোনও স্থায়ী কাজ ছিল না কোনওদিন। পেটে ভাতের অভাব ছিল কিন্তু নিজের সংস্কৃতির প্রতি অসীম মমতা ও ভালোবাসা। ছেলেরা বড় হয়েছে সাংস্কৃতিক পরিবেশে। পিতা-মাতা পরলোকে গমন করেছেন। বড় ছেলে গোসানিমারীতে ব্যবসা করে। বিয়ের পর সেখানেই থিতু হয়েছে, মেজো ছেলে, ছোট ছেলে চণ্ডিনাচের দলে যোগ দিয়েছে। স্ত্রী শিবানী দেবনাথকে সাইটল গানের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। মূল হিসেবে তৈরি করতে পারেন নি। সামান্য কিছু কৃষিজমি আছে। তাই দিয়ে স্ত্রী-সন্তান-নাতি-নাতনীদের নিয়ে জীবন অতিবাহিত হচ্ছে । ছেলেরা বড় হয়েছে কাজকর্ম শুরু করেছে তাতে পরিবারে আর্থিক সংকট কেটেছে অনেকটা।

(ক্রমশ)
Have an account?
Login with your personal info to keep reading premium contents
You don't have an account?
Enter your personal details and start your reading journey with us
Design & Developed by: WikiIND
Maintained by: Ekhon Dooars Team