







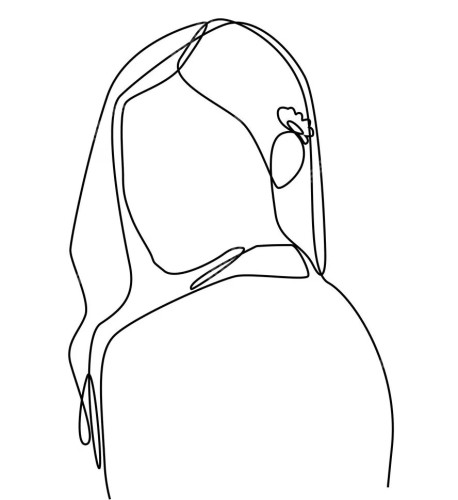



 а¶Єа¶ђаІНа¶ѓа¶Єа¶Ња¶ЪаІА බටаІНට
а¶Єа¶ђаІНа¶ѓа¶Єа¶Ња¶ЪаІА බටаІНට

а¶Ча¶ЃаІАа¶∞а¶Њ
ඥඌа¶ХаІЗа¶∞ ඐඌබаІНа¶ѓа¶њ ටඌа¶≤аІЗ ටඌа¶≤аІЗ а¶ђа¶Ња¶Ьа¶ЫаІЗ, ටඌа¶∞а¶З а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ථаІЗа¶ЪаІЗ ථаІЗа¶ЪаІЗ а¶Ча¶Ња¶За¶ЫаІЗථ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Ьථ ඙аІБа¶∞аІБа¶Ја•§ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Еа¶ЩаІНа¶Ча¶≠а¶ЩаІНа¶Ча¶њ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗаІНථ, а¶Ѓа¶Ьа¶Њ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗථ, а¶Еа¶≠а¶ња¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගටаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Хඌපගට а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶ЄаІЗ а¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶ЧаІБаІЭ а¶Еа¶∞аІНа¶•а•§ ඙а¶∞ථаІЗ а¶ІаІВа¶≤а¶њ-а¶ІаІВа¶Єа¶∞ගට а¶ІаІВටග а¶У а¶ЄаІНඃඌථаІНа¶°аІЛ а¶ЧаІЗа¶ЮаІНа¶Ьа¶ња•§ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Њ а¶Ча¶Ња¶Б а¶ШаІБа¶∞аІЗ а¶ШаІБа¶∞аІЗ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ ථඌа¶Ъ-а¶ЧඌථаІЗ а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНඕа¶ХаІЗ а¶ЦаІБපග а¶Х’а¶∞аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Чථ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Па¶Ба¶∞а¶Њ а¶≠а¶ХаІНа¶§а•§ පගඐаІЗа¶∞ а¶≠а¶ХаІНа¶§а•§ а¶Ча¶Ња¶БаІЯаІЗ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ ‘а¶ЦаІЗа¶≤а¶ЯаІБ’ а¶ђа¶Њ ‘඙аІЗа¶≤аІЗаІЯа¶Ња¶∞’а•§ ටඌа¶Ба¶∞а¶Ња¶З ‘ඪථаІНථаІНа¶ѓа¶Ња¶ЄаІА’а•§
а¶ЪаІИටаІНа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ පаІЗа¶Ј ඪඌටබගථ/඙ඌа¶Ба¶Ъබගථ/ටගථබගථ ‘а¶Ча¶Ѓа¶ња¶∞а¶Њ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Њ’ а¶єаІЯ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа•§ а¶ЃаІВа¶≤ට а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶њ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤а¶ња¶§а•§ පගඐа¶ХаІЗ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІЗ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЖථаІБа¶ЈаІНආඌථගа¶Х а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞а•§ а¶Єа¶ЃаІН඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗа¶∞ ටටаІНඐඌඐ඲ඌථаІЗ ඕඌа¶ХаІЗථ а¶Па¶Ха¶Ьථ ‘а¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶Юа¶Њ’а•§ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶Юа¶Њ පඐаІНබа¶Яа¶ња¶∞ а¶Еа¶∞аІНඕ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථ-඙аІНа¶∞а¶Іа¶Ња¶®а•§ а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО ඃගථග а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗа¶∞ а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Жа¶∞ ඕඌа¶ХаІЗථ ‘බаІЗа¶ђа¶Ња¶ВපаІА’а•§ а¶Ча¶Ња¶БаІЯаІЗа¶∞ а¶ХаІЛථа¶У а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞аІА, ඃගථග ඙аІВа¶Ьа¶Њ-а¶Еа¶∞аІНа¶Ъථඌ а¶Ха¶∞аІЗථ, а¶єаІЯටаІЛ а¶ђа¶Њ ටගථග ථගа¶ЬаІЗа¶У а¶ХаІЛථа¶У а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Ча¶Ѓа¶ња¶∞а¶Њ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Њ-аІЯ а¶Еа¶Вපа¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞ටаІЗථ, а¶Па¶Цථ а¶ђаІЯа¶Є а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ ටඌа¶З ටගථග බаІЗа¶ђа¶Ња¶ВපаІА а¶ђа¶Њ ඙аІБа¶∞аІЛа¶єа¶ња¶§а•§ а¶Еඕඐඌ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЗа¶Й බаІЗа¶ђа¶Ња¶ВපаІА а¶є’ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗථ—ඃගථග ඙аІВа¶Ьа¶Њ а¶Єа¶ЃаІНඐථаІНа¶ІаІАаІЯ а¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶Жа¶єа¶∞а¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶ња¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ЧаІБа¶≤ගටаІЗ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ ‘බаІЗа¶Йа¶ЄаІА’ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єаІЯа•§ ඙аІБа¶∞аІЛයගට а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶БබаІЗа¶∞ а¶ђаІБа¶Эа¶њ ටගථග ටаІЗඁථ а¶®а¶®а•§ ටගථග а¶ѓаІЗ ඙аІБа¶ЬаІЛ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථ а¶Ха¶∞аІЗථ ටඌටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ ථඌ බаІЗа¶ђа¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ ඁථаІНටаІНа¶∞аІЛа¶ЪаІНа¶Ъа¶Ња¶∞а¶£а•§ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђа¶ЬබаІЗа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ පаІБථаІЗ а¶Жа¶Єа¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Жа¶∞ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ ථගа¶∞аІНа¶Ѓа¶Ња¶£аІЗ а¶ЧаІЬаІЗ а¶Уආඌ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ පඐаІНබаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ЄаІЗа¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶Па¶Ха¶З ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞ ඁථаІНටаІНа¶∞ බаІЗа¶Йа¶ЄаІА а¶ђа¶Њ බаІЗа¶ђа¶Ња¶ВපаІА а¶≠аІЗබаІЗ ඐබа¶≤аІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Па¶З а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶Юа¶Њ а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗථ а¶Єа¶ђа•§ බаІЗа¶Йа¶ЄаІА ඙аІБа¶ЬаІЛ-а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗа¶®а•§ а¶Ча¶Ња¶БаІЯаІЗа¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ටа¶∞аІБа¶£ а¶У а¶ѓаІБа¶ђа¶Х а¶ЃаІВа¶≤ а¶Ча¶ЃаІАа¶∞а¶Њ а¶ЦаІЗа¶≤а¶ЊаІЯ а¶Еа¶Вපа¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ඥඌа¶ХаІЗа¶∞ ඐඌබаІНа¶ѓа¶ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶Хඐගටඌ а¶Жа¶ђаІГටаІНටග а¶Ха¶∞аІЗථ, а¶Чඌථ а¶Ха¶∞аІЗථ, ටඌа¶≤аІЗ ටඌа¶≤аІЗ ථаІГටаІНа¶ѓ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපථ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶У а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ පඌа¶∞аІАа¶∞а¶ња¶Х а¶Ха¶Єа¶∞аІО බаІЗа¶Ца¶Ња¶®а•§
а¶Ча¶Ѓа¶ња¶∞а¶Њ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ බගථ ‘පගඐ а¶Ча¶ЊаІЬа¶Њ’
а¶Па¶За¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට බаІЗඐටඌа¶ХаІЗ а¶Жа¶єаІНඐඌථ а¶Х’а¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞ඕඁ බගථаІЗа¶∞ පගඐ а¶ЄаІНඕඌ඙ථ а¶У ඙аІВа¶Ьа¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶ЃаІВа¶≤ට а¶Ѓа¶єаІЗබаІЗа¶ђаІЗа¶∞ ඙аІВа¶Ьа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯ, ටඐаІЗ බаІЗඐටඌ а¶Е඙බаІЗඐටඌ а¶Єа¶Ха¶≤а¶ХаІЗа¶З а¶Жа¶єаІНඐඌථ а¶ЬඌථඌථаІЛ а¶єаІЯа•§ а¶Ча¶Ња¶БаІЯаІЗа¶∞ а¶ХаІЛථа¶У а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЄаІНඕඌථаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Еа¶ЄаІНඕඌаІЯаІА පගඐаІЗа¶∞ ඕඌථ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶ХаІЛථа¶У а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЄаІНඕඌථ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІНа¶ЫථаІНථ а¶Х’а¶∞аІЗ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶∞ а¶ђаІЗබග ටаІИа¶∞а¶њ а¶Х’а¶∞аІЗ а¶ђа¶Њ ථඌ а¶Х’а¶∞аІЗ, ටඌටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶∞а¶Яа¶њ а¶ЦаІБа¶Яа¶њ බගаІЯаІЗ а¶У඙а¶∞аІЗ а¶ЦаІЬаІЗа¶∞ а¶Ыа¶Ња¶Йථග බගаІЯаІЗ а¶Па¶З ඕඌථа¶Яа¶њ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶Юа¶Ња¶∞ а¶ЖаІЯаІЛа¶ЬථаІЗ බаІЗа¶Йа¶ЄаІА ඙аІБа¶ЬаІЛ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ХаІЗа¶Й а¶ХаІЗа¶Й а¶ђа¶Вප ඙а¶∞а¶ЃаІН඙а¶∞а¶ЊаІЯ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶Юа¶Ња•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞аІБа¶∞ ඁඌථඪගа¶Х ඕඌа¶Ха¶≤аІЗ а¶ЄаІЗа¶У а¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶Юа¶Њ а¶єаІЯаІЗ ඙аІБа¶ЬаІЛа¶∞ а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට а¶Ца¶∞а¶Ъ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶Юа¶Ња¶З ඐයථ а¶Ха¶∞аІЗ ඕඌа¶ХаІЗа¶®а•§ а¶≠а¶ХаІНට а¶ђа¶Њ а¶ЦаІЗа¶≤а¶ЯаІБа¶∞а¶Њ ඃටබගථ а¶ШаІБа¶∞а¶ђаІЗ а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО ටගථ, ඙ඌа¶Ба¶Ъ, ඪඌටබගථ—а¶Па¶З බගථа¶ЧаІБа¶≤ගටаІЗ පගඐ а¶ЂаІБа¶≤ а¶Ьа¶≤ ඙ඌඐаІЗථ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶Юа¶Ња¶∞ යඌටаІЗа¶За•§ ඙аІНа¶∞ඕඁ බගථ බаІЗа¶Йа¶ЄаІА ඐග඲ග඙аІВа¶∞аІНа¶ђа¶Х ඙аІВа¶Ьа¶Њ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗа¶®а•§ ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞ ඙а¶∞аІЗ බаІЗඐටඌ а¶У බаІЗа¶Йа¶ЄаІАа¶∞ а¶ЖපаІАа¶∞аІНඐඌබ а¶У ඙аІНа¶∞ඪඌබ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Х’а¶∞аІЗ а¶≠а¶ХаІНටа¶∞а¶Њ а¶ђаІЗа¶∞а¶њаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа¶®а•§ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶Юа¶Ња¶∞ а¶ХගථаІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ ථටаІБථ а¶ІаІВටග а¶У а¶ЄаІНඃඌථаІНа¶°аІЛ а¶ЧаІЗа¶ЮаІНа¶Ьа¶њ а¶Ча¶ЊаІЯаІЗа•§ а¶Єа¶Ња¶∞ඌබගථ а¶Ча¶Ња¶БаІЯаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶ШаІБа¶∞аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Чථ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Њ а¶єаІЯ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗа¶З а¶∞ඌටа¶Яа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ѓа¶Ња¶®а•§ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗа¶З а¶Жа¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНа¶•а•§ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶Жа¶єа¶Ња¶∞ ටඌа¶БබаІЗа¶∞а•§ ථගа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ња¶Ј а¶°а¶Ња¶≤,а¶≠ඌට,а¶Єа¶ђа¶Ьа¶ња•§ а¶ѓаІЗа¶ХаІЛථа¶У а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНඕаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗа¶∞ а¶Жа¶ЩගථඌаІЯ а¶ђа¶Њ а¶ђа¶Ња¶∞ඌථаІНබඌаІЯ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ ඕඌа¶ХаІЗථ а¶Па¶Ха¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа•§ පаІБаІЯаІЗ а¶ШаІБа¶ЃаІЛථаІЛа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ХаІЛථа¶У а¶ђа¶ња¶Ыඌථඌ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶®а¶Ња•§ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ පගඐаІЗа¶∞ ‘а¶ЪаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶Њ’ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ටඌа¶З а¶Па¶З а¶Х’බගථ а¶≠аІВට-඙аІНа¶∞аІЗටаІЗа¶∞ ඁටа¶З ඕඌа¶ХаІЗථ а¶≠а¶ХаІНටа¶∞а¶Њ а¶ђа¶Њ а¶ЦаІЗа¶≤а¶ЯаІБа¶∞а¶Ња•§ а¶ЪаІБа¶≤ බඌа¶БаІЬа¶њ а¶Ха¶Ња¶ЯаІЗථ а¶®а¶Ња•§ а¶ЄаІНථඌථ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶®а¶Ња•§ а¶Ьа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Хඌ඙аІЬ ඐබа¶≤ඌථ а¶®а¶Ња•§ බඌа¶Бට а¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗථ а¶®а¶Ња•§ а¶Пඁථа¶Ха¶њ а¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶єа¶ЄаІНට ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶≤ථа¶У а¶Ха¶∞аІЗථ а¶®а¶Ња•§
а¶Ча¶Ѓа¶ња¶∞а¶Њ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Ња¶ХаІЗ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ а¶Х’а¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶ЕථаІЗа¶Ха¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶Хඌයගථගа¶∞ а¶ЕථаІНඃටඁ а¶Па¶З а¶Ча¶≤аІН඙а¶Хඕඌа¶Яа¶њ පаІБථගаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ а¶ЃаІЯථඌа¶ЧаІБаІЬа¶њ а¶ђаІНа¶≤а¶ХаІЗа¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶ЧаІБаІЬа¶њ ඙а¶ЮаІНа¶Ъа¶ЊаІЯаІЗටаІЗа¶∞ а¶Ъඌ඙а¶ЧаІЬ а¶Ча¶Ња¶БаІЯаІЗа¶∞ ථаІЗа¶ђаІБа¶ХඌථаІНට а¶∞а¶ЊаІЯа•§ ටගථග ථගа¶ЬаІЗ ‘බаІЗа¶Йа¶ЄаІА’ а¶ђа¶Њ ‘බаІЗа¶ђа¶Ња¶ВපаІА’ а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞аІАа•§ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථа¶Ха¶Ња¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶ХаІЯаІЗа¶Х ඙аІБа¶∞аІБа¶Ј ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ බаІЗа¶Йа¶ЄаІАа•§ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶Юа¶Ња¶У а¶§а¶ња¶®а¶ња•§ ඪඌටඌටаІНටа¶∞ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶ђаІЯа¶ЄаІА ථаІЗа¶ђаІБа¶ХඌථаІНට а¶ђа¶≤аІЗථ, а¶Ча¶Ѓа¶ња¶∞а¶Њ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Њ а¶Ха¶ђаІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට—а¶Па¶Хඕඌ а¶ЕථаІБඁඌථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Еа¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђа•§ а¶ХаІЗථ а¶Па¶З ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ථ а¶ЄаІЗа¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶Ња¶У а¶ЃаІБපа¶Ха¶ња¶≤а•§ ටඐаІЗ а¶ѓаІЗ а¶Хඌයගථග ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට ටඌ а¶Па¶За¶∞аІВ඙—පගඐаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶њаІЯ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඙ඌа¶Бආඌ (ථඌа¶Ха¶њ а¶Ја¶Ња¶БаІЬ) а¶єа¶Ња¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ЦаІЛа¶Ба¶Ь ථගаІЯаІЗ а¶Ьඌථඌ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ЄаІЗа¶Яа¶њ а¶ЪаІБа¶∞а¶њ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ ඙аІНа¶∞а¶њаІЯ а¶Па¶З ඙аІЛа¶ЈаІНа¶ѓа¶ХаІЗ а¶єа¶Ња¶∞а¶њаІЯаІЗ පගඐ а¶≠аІЯа¶ЩаІНа¶Ха¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗ඙аІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬටаІЗ а¶ђаІЗа¶∞аІБа¶≤аІЛ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЕථаІБа¶Ъа¶∞ а¶ђаІГථаІНа¶¶а•§ а¶ХаІЛඕඌа¶У ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ ටаІЛ а¶ЧаІЗа¶≤а¶З ථඌ, а¶Ьඌථඌ а¶ЧаІЗа¶≤ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£а¶ња¶Яа¶ња¶ХаІЗ а¶ХаІЗа¶Й а¶ХаІЗа¶ЯаІЗ а¶ЦаІЗаІЯаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶З а¶Ца¶ђа¶∞ පගඐаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ඙аІМа¶Ба¶ЫаІБටаІЗа¶З පගඐ ඪගබаІН඲ඌථаІНට ථගа¶≤аІЗථ а¶ЪаІЛа¶∞а¶ХаІЗ а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬаІЗ а¶ђаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶З а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶ХаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ! а¶∞ඌථаІНථඌ а¶Х’а¶∞аІЗ а¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඙පаІБа¶ХаІЗ а¶Ха¶Ња¶Яа¶ђа¶Ња¶∞ ඃථаІНටаІНа¶∞, а¶Жа¶ЧаІБථ, а¶У а¶Ьа¶≤ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьа¶®а•§ ටඌа¶З ඙аІНа¶∞ඕඁаІЗа¶З а¶ЧаІЗа¶≤аІЗථ а¶Еа¶ЧаІНථගа¶∞ බаІЗඐටඌ а¶ђаІНа¶∞а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа•§ а¶ђаІНа¶∞а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶Ѓа¶Њ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට а¶Ша¶Яථඌ පаІБථаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ а¶Пඁථ а¶Ха¶Ња¶∞аІБа¶∞ а¶∞ඌථаІНථඌ а¶Х’а¶∞аІЗ а¶Ца¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ца¶ђа¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ථаІЗа¶За•§ а¶Па¶∞඙а¶∞ පගඐ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗථ а¶Ьа¶≤аІЗа¶∞ බаІЗඐටඌ а¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶£аІБа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа•§ ටගථග පаІБථаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, а¶Жа¶Ѓа¶ња¶У а¶Ьඌථග ථඌ а¶Пඁථ а¶Ша¶Яа¶®а¶Ња•§ ඃථаІНටаІНа¶∞аІЗа¶∞ බаІЗඐටඌ ඐගපаІНа¶ђа¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶Ња¶У පගඐа¶ХаІЗ а¶Ьඌථඌа¶≤аІЗථ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа¶У а¶ХаІЛථа¶У а¶Ца¶ђа¶∞ ථаІЗа¶За•§ ටඐаІЗ!
පගඐ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ а¶Па¶Єа¶ђа¶З а¶ЈаІЬඃථаІНටаІНа¶∞а•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЃаІЗа¶Ьа¶Ња¶Ь а¶ЪаІЬටаІЗ а¶≤а¶Ња¶Ча¶≤аІЛа•§ а¶Йа¶ЈаІНа¶£ පаІЛථගට а¶ЫаІБа¶ЯටаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞а¶≤ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට පа¶∞аІАа¶∞аІЗа•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶≤а¶ња¶ЩаІНа¶Ч බаІАа¶∞аІНа¶Ша¶ЊаІЯගට а¶єаІЯаІЗ а¶ЃаІЗබගථаІА а¶≠аІЗබ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට а¶Ъа¶∞а¶Ња¶Ъа¶∞ а¶ІаІНа¶ђа¶Ва¶ЄаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЙබаІНඃට а¶єа¶≤а•§ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗ а¶≠аІЯ ඙аІЗаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ЫаІБа¶Яа¶≤аІЗථ ඙ඌа¶∞аІНඐටаІАа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа•§ а¶Ѓа¶єаІЗපаІНа¶ђа¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Њ ඙ඌа¶∞аІНඐටаІА а¶ђаІБа¶Эа¶≤аІЗථ а¶ШаІЛа¶∞ а¶Еа¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ а¶ЖඪථаІНа¶®а•§ а¶Па¶ЦаІБථග ථගа¶∞а¶ЄаІНට а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ а¶≠аІЛа¶≤а¶Њ ඐගපаІНඐථඌඕ а¶ХаІЗа•§ ටගථග ටඌа¶Ба¶ХаІЗ පඌථаІНට а¶Ха¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ѓаІЛථග а¶ЄаІНඕඌ඙ථ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ පගඐаІЗа¶∞ а¶ЙබаІН඲ට а¶≤а¶ња¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞а•§ а¶ПටаІЗ පගඐ පඌථаІНට а¶єа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙ඌа¶Бආඌа¶∞ а¶ХаІА а¶єа¶ђаІЗ! ඙ඌа¶∞аІНඐටаІА ඪඁඌ඲ඌථ බගа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, а¶Ж඙ථඌа¶∞ а¶≤а¶ња¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶ЄаІНඕඌ඙ගට а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ѓаІЛථගа¶∞ а¶Па¶Х඙ඌපаІЗ а¶≤аІМа¶єа¶Ха¶Ња¶Ба¶Яа¶Њ а¶Єа¶Ва¶ѓаІБа¶ХаІНට а¶Х’а¶∞аІЗ а¶У඙а¶∞ ඙ඌа¶∞аІНපаІНа¶ђаІЗ а¶Па¶Ха¶ЧаІБа¶ЪаІНа¶Ы ටаІГа¶£а¶ЄаІВටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶єа¶Ња¶ѓаІНа¶ѓаІЗ ටඌа¶ХаІЗ а¶ШаІЛа¶∞ඌටаІЗ а¶ђа¶≤аІБථ а¶Ж඙ථඌа¶∞ а¶ЕථаІБа¶Ъа¶∞ а¶ђаІГථаІНබа¶ХаІЗа•§ а¶Па¶З а¶≤аІМа¶єа¶Ха¶Ња¶Ба¶Яа¶ЊаІЯ а¶ЧаІЗа¶БඕаІЗ а¶Жа¶Єа¶ђаІЗ а¶ЄаІЗ а¶ЪаІЛа¶∞а•§
а¶Ѓа¶∞аІНට඲ඌඁаІЗ а¶ЄаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђа¶≤ а¶ШаІБа¶∞аІНа¶£а¶®аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶≤аІМа¶єа¶Ха¶Ња¶Ба¶Яа¶ЊаІЯ а¶ЧаІЗа¶БඕаІЗ а¶Па¶≤ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЪаІЛа¶∞а•§ а¶ЬаІЗа¶∞а¶Њ а¶Х’а¶∞аІЗ ටඌа¶ХаІЗ а¶Ьඌථඌ а¶ЧаІЗа¶≤—а¶єаІНа¶ѓа¶Ња¶Б ඙පаІБа¶Яа¶ња¶ХаІЗ а¶ЪаІБа¶∞а¶њ а¶Х’а¶∞аІЗ а¶ЦаІЗаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЄаІЗа¶З-а¶За•§ а¶ЄаІЗ ටඌа¶ХаІЗ а¶ХаІЗа¶ЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ බඌ බගаІЯаІЗ—а¶ѓа¶Њ ථගаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶єаІЯ පаІНඁපඌථаІЗа•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ ටඌටаІЗ ඐගපаІНа¶ђа¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶Њ ඕඌа¶ХаІЗථ а¶®а¶Ња•§ а¶∞ඌථаІНථඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗ а¶Єа¶ња¶ЮаІНа¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Ьа¶≤аІЗ (а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ѓаІЗ а¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶∞ а¶Ьа¶≤ а¶Іа¶Ња¶∞а¶ЊаІЯ ථаІЗа¶ЃаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗ), ටඌටаІЗ а¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶£аІБ ඕඌа¶ХаІЗථ а¶®а¶Ња•§ ටаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Жа¶ЧаІБථ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ ටඌටаІЗ а¶ђаІНа¶∞а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶Ѓа¶Њ ඕඌа¶ХаІЗථ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶З а¶Ша¶Яථඌ а¶ЬаІЗථаІЗ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗа¶З а¶ђа¶ња¶ЈаІНඁගට,඙аІБа¶≤а¶Ха¶ња¶§а•§ а¶ХаІА а¶ђаІБබаІНа¶Іа¶њ а¶ЪаІЛа¶∞аІЗа¶∞! а¶ѓаІЗ බගථ а¶Па¶Ша¶Яථඌ а¶Ша¶ЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЄаІЗබගථ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЪаІИටаІНа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ХаІНа¶∞ඌථаІНа¶§а¶ња•§ а¶Па¶З а¶Ша¶Яථඌа¶∞ а¶ЄаІНа¶Ѓа¶∞а¶£аІЗа¶З පаІБа¶∞аІБ а¶єаІЯ а¶ЪаІИටаІНа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ පаІЗа¶Ј ඪ඙аІНටඌයаІЗ ‘а¶Ча¶Ѓа¶ња¶∞а¶Њ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Њ’, а¶ЄаІЗ а¶ХаІЛථ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ а¶ѓаІБа¶ЧаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞පаІНථ а¶Ыа¶ња¶≤, а¶Па¶З а¶ЪаІЛа¶∞ а¶ЖබටаІЗ а¶ХаІЗ? ටඌа¶∞ а¶ХаІЛථа¶У а¶ЙටаІНටа¶∞ а¶Па¶Цථа¶У а¶Ха¶Ња¶∞аІБа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ඙ඌа¶За¶®а¶ња•§
඙аІВа¶Ьа¶Њ ඙බаІН඲ටග
පගඁаІБа¶≤ а¶Еඕඐඌ පඌа¶≤ а¶Ча¶Ња¶ЫаІЗа¶∞ а¶ЦаІБа¶Ба¶Яа¶ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඙ඌප а¶Ѓа¶Ња¶ЯගටаІЗ ඙аІНа¶∞аІЛඕගට а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶Жа¶ХඌපаІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶Е඙а¶∞ ඙ඌа¶∞аІНපаІНа¶ђаІЗ а¶Жа¶Яа¶Яа¶њ а¶ђа¶Ња¶Бප බගаІЯаІЗ ථගа¶∞аІНඁඌථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯ а¶ШаІБа¶∞аІНа¶£аІЛථа¶ХаІНа¶Ја¶Ѓ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඃථаІНටаІНа¶∞а•§ ටඌа¶ХаІЗ ‘а¶ЪаІЬа¶Ха¶њ’ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶ђа¶Ња¶БපаІЗа¶∞ ටаІИа¶∞а¶њ а¶ѓаІЗ а¶ЪаІЬа¶Ха¶њ ටඌа¶∞ а¶ЄаІНඕඌථаІАаІЯ ථඌඁ ‘а¶ХаІЗа¶∞а¶Ха¶њ’а•§ а¶Па¶З ඃථаІНටаІНа¶∞а¶Яа¶њ බаІЗа¶ЦටаІЗ а¶єаІЯ а¶ѓаІЛථගа¶∞ ථаІНа¶ѓа¶ЊаІЯа•§ පගඁаІБа¶≤ а¶ђа¶Њ පඌа¶≤аІЗа¶∞ а¶ѓаІЗ а¶ђаІГа¶ХаІНа¶Ј а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯ ටඌ පගඐа¶≤а¶ња¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගа¶Ха•§ а¶Жа¶∞ а¶У඙а¶∞аІЗа¶∞ ඃථаІНටаІНа¶∞а¶Яа¶њ ඙ඌа¶∞аІНඐටаІАа¶∞ а¶ѓаІЛථගа¶∞ а¶∞аІВа¶™а•§ а¶Па¶ХаІЗ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єаІЯ а¶Ъа¶∞а¶Ха¶ња•§
а¶ЪаІИටаІНа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ (а¶П඙аІНа¶∞а¶ња¶≤аІЗа¶∞ බаІНඐගටаІАаІЯ ඪ඙аІНටඌය) පаІЗа¶Ј ඙ඌа¶Ба¶Ъබගථ (а¶ђа¶Њ ටගථබගථ/ඪඌටබගථ) а¶≠а¶ХаІНටа¶∞а¶Њ а¶Ча¶Ња¶БаІЯаІЗа¶∞ а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНඕබаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶Чඌථ а¶У ථඌа¶Ъ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ඪඌඕаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ ඥඌа¶Х а¶У а¶Ха¶Ња¶Ба¶Єа¶∞ ඐඌබаІНඃඃථаІНටаІНа¶∞ а¶∞аІВ඙аІЗа•§ а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНටа¶ХаІЗ а¶ЦаІБපаІА а¶Х’а¶∞аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Чථ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ පаІБа¶ІаІБ а¶ѓаІЗ ථඌа¶Ъ-а¶Чඌථ а¶Ха¶∞аІЗථ ටඌ ථаІЯа•§ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶ђаІНа¶ѓа¶ЊаІЯа¶Ња¶Ѓ а¶У බа¶≤а¶Чට පඌа¶∞аІАа¶∞а¶ња¶Х а¶Ха¶Єа¶∞аІОа¶У බаІЗа¶Цඌථ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а•§ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶Чඌථ а¶Ча¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶Ча¶ЃаІАа¶∞а¶Ња¶∞ ථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Я а¶Чඌථ а¶ѓаІЗඁථ а¶Жа¶ЫаІЗ ටаІЗඁථගа¶З а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ЃаІЗа¶ЪаІЗථග а¶ЦаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Чඌථ, ටගඪаІНටඌ а¶ђаІБаІЬа¶ња¶∞ а¶Чඌථ, а¶≠а¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶ЗаІЯа¶Њ а¶ђа¶Њ ඙ඌа¶≤а¶Ња¶Яа¶њаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ча¶Ња¶®а•§ а¶Па¶З а¶Чඌථа¶ЧаІБа¶≤ගටаІЗ а¶ѓаІМථ а¶За¶ЩаІНа¶Чගට ඕඌа¶ХаІЗа•§
а¶Ча¶Ѓа¶ња¶∞а¶Њ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ පаІЗа¶Ј а¶єаІЯ а¶ЪаІИටаІНа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ХаІНа¶∞ඌථаІНටගа¶∞ බගථ а¶Ъа¶∞а¶Х ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓ බගаІЯаІЗа•§ а¶Ъа¶∞а¶Х ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞ ඙а¶∞аІЗа¶∞ බගථ පඌථаІНටග ඙аІВа¶Ьа¶Њ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආගට а¶єаІЯа•§ а¶≠а¶ХаІНටа¶∞а¶Њ а¶ЄаІНථඌථ а¶Х’а¶∞аІЗ ථටаІБථ а¶ђа¶ЄаІНටаІНа¶∞ ඙а¶∞ග඲ඌථ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ЄаІЗබගථ ථගаІЯа¶Ѓ а¶≠а¶ЩаІНа¶Ч а¶ђа¶Њ а¶ЃаІОа¶Єа¶ЃаІБа¶ЦаІАа¶∞ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථа¶У а¶єаІЯа•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶ѓаІЗ а¶Х’බගථ а¶Ча¶Ѓа¶ња¶∞а¶Њ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Њ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආගට а¶єаІЯ а¶ЄаІЗ а¶ХаІЯаІЗа¶Хබගථ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗ ථගа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ња¶Ј а¶Жа¶єа¶Ња¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Ча¶Ѓа¶ња¶∞а¶Њ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Њ а¶ђа¶Њ ඁයඌබаІЗа¶ђаІЗа¶∞ а¶Па¶З ඙аІБа¶ЬаІЛ පаІБа¶∞аІБ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђаІНඃඌථ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯа•§ а¶Пඁථ а¶Хඕගට а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ХаІЛථа¶У а¶ХаІЛථа¶У а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа•§ а¶Па¶З а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Њ а¶ХаІЛථ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, а¶ХаІЛඕඌаІЯ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Жа¶∞ а¶ХаІЛථ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞а¶З а¶ђа¶Њ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶П а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗ а¶Єа¶ЪаІНа¶Ы а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ а¶Ха¶Ња¶∞аІБа¶∞а¶З ථаІЗа¶За•§
а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ ටථаІНටаІНа¶∞ඪඌ඲ථඌ а¶У а¶Ча¶Ѓа¶ња¶∞а¶Њ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Њ
а¶ђа¶∞аІНටඁඌථаІЗ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶Вප а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ ඙аІВа¶Ьа¶Њ ඙බаІН඲ටග ටඌථаІНටаІНа¶∞а¶ња¶Х ඁටаІЗ а¶єаІЯа•§ а¶ђа¶Ња¶Ща¶Ња¶≤аІАа¶∞ පඌа¶∞аІЛබаІОа¶Єа¶ђ බаІБа¶∞аІНа¶Чඌ඙аІБа¶ЬаІЛ, а¶ХаІЛа¶Ьа¶Ња¶Ча¶∞аІА а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ЃаІА ඙аІВа¶Ьа¶Њ, а¶Ха¶Ња¶≤аІА ඙аІВа¶Ьа¶Њ а¶Еඕඐඌ а¶Еа¶Єа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶Ња¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓа¶Њ, බа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗа¶∞ ථඐа¶∞ඌටаІНа¶∞, а¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗаІНа¶∞ а¶ЧаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЧаІЯаІЗපаІНа¶ђа¶∞аІА а¶У а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶Ња¶ЧаІМа¶∞аІА, ඙ඌа¶ЮаІНа¶Ьа¶Ња¶ђаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ВаІЬа¶Њ බаІЗа¶ђаІА, а¶ЃаІБа¶ЃаІНа¶ђа¶Ња¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЃаІНඐඌබаІЗа¶ђаІА, ඙ඌа¶∞аІНඐටаІАපаІИа¶≤аІЗа¶∞ ඙ඌа¶∞аІНඐටаІА, а¶ХඌපаІНа¶ЃаІАа¶∞аІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІАа¶∞ а¶≠ඐඌථаІА—а¶ЗටаІНඃඌබග а¶Жа¶∞а¶У а¶ЕථаІЗа¶Х පа¶ХаІНටග඙аІБа¶ЬаІЛ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ ථаІЗ඙ඌа¶≤аІЗ а¶ЧаІБа¶єаІНа¶ѓаІЗපаІНа¶ђа¶∞аІА а¶У а¶Жа¶∞а¶У а¶ЕථаІНඃඌථаІНа¶ѓ බаІЗපаІЗа¶∞ ටථаІНටаІНа¶∞ඪඌ඲ථඌа¶∞ а¶Хඕඌ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ЬඌථටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ња•§ ටඐаІЗ ටථаІНටаІНа¶∞ ඪඌ඲ථඌаІЯ а¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ පа¶ХаІНටග ඙аІБа¶ЬаІЛа¶З а¶єаІЯ а¶®а¶Ња•§ ටථаІНටаІНа¶∞ ඪඌ඲ථඌа¶∞ ටගථа¶Яа¶њ а¶Іа¶Ња¶∞а¶Њ පаІИа¶ђ, а¶ђаІИа¶ЈаІНа¶£а¶ђ а¶У පඌа¶ХаІНа¶§а•§ ටඌа¶З පගඐ, ඁයඌබаІЗа¶ђ, а¶Ѓа¶єа¶Ња¶Ха¶Ња¶≤, а¶Ча¶ЃаІНа¶≠аІАа¶∞а¶Њ, а¶Ча¶Ѓа¶ња¶∞а¶Њ а¶ЗටаІНඃඌබග ටථаІНටаІНа¶∞඙аІБа¶ЬаІЛ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤а¶ња¶§а•§ а¶Жа¶ЫаІЗ ටථаІНටаІНа¶∞а¶∞а¶Ња¶Є а¶ЙаІОа¶Єа¶ђа¶Уа•§ ටථаІНටаІНа¶∞ ඪඌ඲ථඌа¶∞ බаІБа¶Яа¶њ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯ а¶ѓаІЛа¶ЧටථаІНටаІНа¶∞ а¶У а¶ХаІНа¶∞а¶њаІЯඌටථаІНටаІНа¶∞а•§ ටථаІНටаІНа¶∞ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶Х а¶Жа¶≤аІЛа¶ЪථඌаІЯ ඙аІНа¶∞а¶ЦаІНඃඌට ථගඐථаІНа¶Іа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЪගථаІНටඌයа¶∞а¶£ а¶Ъа¶ХаІНа¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІА а¶≤а¶ња¶Ца¶ЫаІЗථ, “ටථаІНටаІНа¶∞аІЛа¶ХаІНට а¶Й඙ඌඪථඌ а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ а¶Ха¶∞а¶ња¶≤аІЗ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Яа¶њ а¶ђаІИපගඣаІНа¶ЯаІНа¶ѓ ඙а¶∞а¶ња¶≤а¶ХаІНඣගට а¶єаІЯа•§ ඃඕඌ, а¶ЃаІВа¶≤ඁථаІНටаІНа¶∞, а¶ђаІАа¶ЬඁථаІНටаІНа¶∞, а¶ЃаІБබаІНа¶∞а¶Њ, а¶Жඪථ, ථаІНа¶ѓа¶Ња¶Є, බаІЗඐටඌа¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІАа¶Ха¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІВ඙ а¶ђа¶∞аІНа¶£-а¶∞аІЗа¶ЦඌටаІНа¶Ѓа¶Х ඃථаІНටаІНа¶∞, ඙аІВа¶Ьа¶ЊаІЯ а¶ЃаІОа¶Є, а¶Ѓа¶Ња¶Ва¶Є, ඁබаІНа¶ѓ, а¶ЃаІБබаІНа¶∞а¶Њ, а¶ЃаІИඕаІБථ—а¶Па¶З ඙а¶ЮаІНа¶Ъ а¶Ѓа¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞, а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ѓаІЗ ඪගබаІНа¶Іа¶ња¶≤а¶Ња¶≠аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶£, а¶Йа¶Ъа¶Ња¶Яථ, ඐපаІАа¶Ха¶∞а¶£ ඙аІНа¶∞а¶≠аІГටග а¶Ја¶ЯаІНа¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЖපаІНа¶∞аІЯ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Па¶ђа¶В а¶ѓаІЛа¶ЧඌථаІБа¶ЈаІНа¶†а¶Ња¶®а•§”
ටථаІНටаІНа¶∞ඁටаІЗ බаІЗයඪඌ඲ථඌа¶З а¶ЃаІВа¶≤а•§ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є а¶Ха¶∞аІЗථ බаІЗа¶єаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ а¶ХаІЛථа¶У а¶ЃаІВа¶≤ටටаІНа¶ђ ඕඌа¶ХටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶З ටථаІБа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶З а¶ђаІНа¶∞а¶ХаІНа¶ЈаІНඁඌථаІНа¶°а¶ђаІАа¶Ь ථගයගට а¶Жа¶ЫаІЗа•§ ටඌа¶За¶З පа¶ХаІНа¶§а¶ња•§ а¶ИපаІНа¶ђа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ඙аІМа¶Ба¶ЫаІБථаІЛа¶∞ а¶Й඙ඌаІЯ а¶Па¶З පа¶∞аІАа¶∞а•§ ‘а¶ђаІГයටථගа¶Ча¶Ѓ’ а¶ЧаІНа¶∞ථаІНඕаІЗ ටඌа¶З а¶Жа¶ЫаІЗ
а¶ЄаІНඕඌථа¶≠аІЗබаІЗ а¶У බаІЗа¶Йа¶ЄаІА (බаІЗа¶ђа¶Ња¶ВපаІА, ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞аІА) а¶≠аІЗබаІЗ а¶Ча¶Ѓа¶ња¶∞а¶Њ а¶ЦаІЗа¶≤а¶ЊаІЯ ඙аІВа¶Ьа¶Њ ඙බаІН඲ටග а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶єаІЯаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ а¶ХаІЛථа¶У а¶Ча¶Ња¶Ыටа¶≤а¶ЊаІЯ а¶ђа¶Њ а¶ЙථаІНа¶ЃаІБа¶ХаІНට а¶ЄаІНඕඌථаІЗ а¶ѓаІЗ පගඐඕඌථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶∞ а¶ђаІЗබග ටаІИа¶∞а¶њ а¶Х’а¶∞аІЗ ඙ඌඕа¶∞ а¶У ටаІНа¶∞ගපаІБа¶≤ පගඐаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගа¶Х а¶∞аІВ඙аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЯගටаІЗ а¶Ча¶Ња¶Бඕඌ а¶єаІЯа•§ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЯගටаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶∞аІЗа¶Ца¶Ња¶ЪගටаІНа¶∞а¶У а¶Еа¶ЩаІНа¶Хථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ ටථаІНටаІНа¶∞ ඪඌ඲ථඌаІЯ а¶ѓаІЗඁථ а¶ЧаІБа¶∞аІБа¶∞ а¶≠аІВа¶Ѓа¶ња¶Ха¶Њ а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£ ටаІЗඁථа¶З а¶Ча¶Ѓа¶ња¶∞а¶Њ а¶ЦаІЗа¶≤а¶ЊаІЯ බаІЗа¶Йа¶ЄаІАа•§ а¶≠а¶ХаІНටа¶∞а¶Њ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є а¶Ха¶∞аІЗථ බаІЗа¶Йа¶ЄаІАа¶∞ а¶ХаІНඣඁටඌටаІЗа¶З ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ ථගа¶∞аІНа¶ђа¶ња¶ШаІНථаІЗ а¶Єа¶ЃаІН඙аІВа¶∞аІНа¶£ ඙аІВа¶Ьа¶Њ а¶Єа¶Ђа¶≤а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗа¶®а•§
а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ц ඕඌа¶Ха¶Њ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьථ а¶ѓаІЗ ටථаІНටаІНа¶∞ ඪඌ඲ථඌаІЯ а¶ѓаІЗ ඙а¶ЮаІНа¶Ъ ‘а¶Ѓ’-а¶Па¶∞ (ඁබаІНа¶ѓ, а¶Ѓа¶Ња¶Ва¶Є, а¶ЃаІОа¶Є, а¶ЃаІБබаІНа¶∞а¶Њ а¶У а¶ЃаІИඕаІБථ) а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ ටඌ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶Цථ а¶Ча¶Ѓа¶ња¶∞а¶Њ а¶ЦаІЗа¶≤а¶ЊаІЯ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶ЕටаІАටаІЗ а¶єа¶≤аІЗа¶У යටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЯබගථ а¶Ча¶Ѓа¶ња¶∞а¶Њ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Њ а¶Ъа¶≤а¶ђаІЗ බаІЗа¶Йа¶ЄаІА, а¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶Юа¶Њ а¶У а¶≠а¶ХаІНටа¶Ча¶£ ඪ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗ ථගа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ња¶Ј а¶Жа¶єа¶Ња¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗа¶®а•§ а¶ЃаІОа¶Є, а¶Ѓа¶Ња¶Ва¶Є, ඁබаІНа¶ѓ, а¶ЃаІИඕаІБථ ඙а¶∞а¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗа¶®а•§ а¶ХаІЗа¶ђа¶≤ а¶Ха¶Цථа¶У а¶Ха¶Цථа¶У පගඐаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඪඌබ а¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІВ඙ а¶Ча¶ЮаІНа¶Ьа¶ња¶Ха¶Њ а¶ЄаІЗඐථ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶≠а¶ХаІНටа¶∞а¶Ња•§ а¶Пඁථа¶У а¶Йබඌයа¶∞а¶£ а¶Жа¶ЫаІЗ, а¶ѓаІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ а¶Ча¶Ѓа¶ња¶∞а¶Њ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Њ а¶єаІЯ а¶ЄаІЗа¶З а¶Ча¶Ња¶БаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට ඐඌඪගථаІНබඌ а¶Уа¶З а¶Х’බගථ ථගа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ња¶Ј а¶Жа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ථаІЗа¶ђаІБа¶ХඌථаІНට а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНඕ а¶Ча¶Ѓа¶ња¶∞а¶Њ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ ටගථ, ඙ඌа¶Ба¶Ъ, ඪඌටබගථ ථගа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ња¶Ј а¶Жа¶єа¶Ња¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶У а¶ЕථаІНඃඌථаІНа¶ѓ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට ථගаІЯа¶Ѓ а¶ЃаІЗථаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗа¶®а•§ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ а¶ХаІЗа¶Й ටඌа¶∞ а¶ЕථаІНඃඕඌ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗ а¶ЄаІЗа¶З ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗ а¶ХаІЛථа¶У ථඌ а¶ХаІЛථа¶У а¶ЕථගඣаІНа¶Я а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§
(а¶ХаІНа¶∞ඁප)
Have an account?
Login with your personal info to keep reading premium contents
You don't have an account?
Enter your personal details and start your reading journey with us
Design & Developed by: WikiIND
Maintained by: Ekhon Dooars Team