






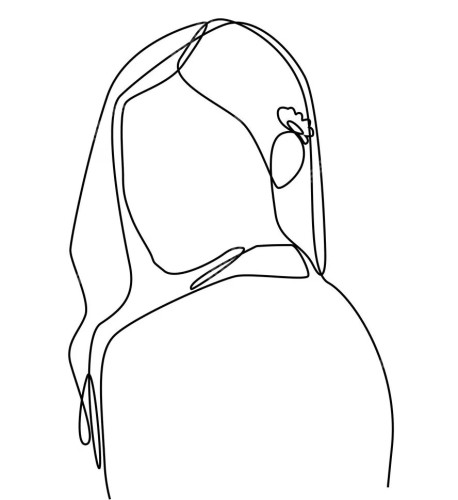



 নবনীতা সান্যাল
নবনীতা সান্যাল

শিলিগুড়ি শহরের ভৌগোলিক অবস্থান তাকে গড়ে তুলেছে বাণিজ্য নগরী হিসেবে-- এই তো সার কথা?
বোসকাকু বললেন “শোনো কথা! এ যেন একদিনেই হয়েছে?”
আমরা বেশ জাঁকিয়ে বসলাম। শীত পড়তে শুরু করেছে ভালোই। সন্ধের আড্ডা জমে উঠল। আমরা সব ছোট বুড়ো জ্যাঠা সবাই তাকে ঘিরে বসলাম পাড়ার ক্লাবঘরে। বোসকাকু শুরু করলেন।
“মোটামুটি ১৮৭৮ সাল। যদ্দূর শুনেছি ওই সময় রেলপথ তৈরি হল। অরণ্য ঘেরা শিলিগুড়ির অরণ্য চিরে প্রথম রেলপথ। আর সেটা মিটার গেজ। ১৮৮১ সালে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং-এর দিকে ট্রয়ট্রেন চলাচল শুরু করে। যে স্টেশনকে ঘিরে রেলযাত্রা শুরু তা আজ শিলিগুড়ি শহরের হেরিটেজ - শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন। বাংলাদেশের ইঁট এনে তৈরি করা হয়েছিল টাউন স্টেশন চত্বর। স্টেশনের চারদিকে ছিল আলোর ব্যবস্থা। সংলগ্ন এলাকা টিকিয়াপাড়া, মহাবীরস্থান আলোকিত হতো এই আলোর ছটায়। অফিস ঘরগুলি পুরোটাই, এমনকি ছাদও ইঁট দিয়ে তৈরি হয়েছিল। দেওয়ালে লাগানো হয়েছিল চীনা প্লেট। প্ল্যাটফর্ম সাজানো হয়েছিল পাথর দিয়ে। প্ল্যাটফর্মের ছাদও ছিল মজবুত। সেই সময় তৈরি করা হয়েছিল, দুটি ওভারব্রিজ। তবে, দুটি ব্রিজের কোনোটিই আর নেই। স্টেশনের গোলাকার টিনের ছাউনিও উধাও। নিচের লোহার পিলারও আর নেই। স্টেশনের বাইরের দেওয়ালে যে পয়েন্টেড ইটের বাহার ছিল, যাতে শ্যাওলা পড়ত না-- আশির দশকে তা বালির প্লাস্টারে ঢেকে দেওয়া হয়।”
দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বোসকাকু। সদ্য কলেজে পা দেওয়া টুকাই বলল— তা সেসব সংরক্ষণ করা যেতো না?
বোসকাকু বললেন, “হ্যাঁ, সে যেতোই। তবে, আমার কথা এখনো শেষ করিনি। পুরোটা শুনলে বুঝতে পারবে-- আসলে বাণিজ্যশহর না, রেলনগরী হিসাবেই শিলিগুড়ির প্রাথমিক যাত্রা শুরু হয়েছিল।”
আমি বললাম, তার কারণ?
বোসকাকু বললেন, “সম্ভবত একটা কারণ, এ সময়ের মধ্যে চা বাগানগুলির তৈরি হয়ে ওঠা। চা, কমলালেবু, পাহাড়ি মশলা এবং কাঠ রপ্তানির তাগিদ ছিল।”
তড়বড করে টুকাই বলে বসলো, ওহ্, ব্যবসার বিষয়টা তাহলে ছিলই বল?
বোসকাকু বললেন, “তা তো ছিলই। আর ছিল আবহাওয়া। দার্জিলিং-এর মনোরম আবহাওয়া একটি অন্যতম আকর্ষণ ছিল ব্রিট্রিশ কোম্পানিগুলির কাছে। সেজন্যই পরবর্তীকালে ন্যারোগেজের পাশাপাশি কলকাতা-শিলিগুড়ি ব্রডগেজ লাইন তৈরি হয়েছিল। ন্যারোগেজ লাইনে টাউন স্টেশন থেকে রেল চলত হিলকার্ট রোড পার হয়ে দার্জিলিং। রওনা হত টাউন স্টেশনে থেকে। তারপর উল্লেখযোগ্য ছিল মহানন্দা সেতু, তারপর ছিল বর্তমান দাগাপুর সংলগ্ন অঞ্চল। রেললাইন ধরে গড়ে উঠেছিল রেল কোর্য়াটার। শিলিগুড়ি তখন রেলকেন্দ্রিক ছোট জনপদই ছিল। ন্যারো গেজ লাইন বর্তমানের ভেনাস রোড পযর্ন্ত ছড়ানো ছিল।”
আমি বললাম, তাহলে গুরুত্ব হারাল কেন টাউন স্টেশন?
বোসকাকু বলে চললেন, “রেল শুরু হওয়ার চারদশক ধরে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন ছিল শহরের প্রধানতম আকর্ষণ। জানো তো পুজোর দিনগুলিতে প্ল্যাটফর্মে সিনেমা দেখানো হত ? ঝকঝকে স্টেশনে বসে একসঙ্গে সিনেমা দেখতেন শহরের মানুষ। ভাবতে পারো? পুজোর আগে কলকাতা থেকে বিশেষ বগিতে আসত প্রসাধন দ্রব্য, অলংকার, জুতো-- আর সেই সব নিয়ে শিলিগুড়ি স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকত । শহরের লোকজন তো বটেই, আশেপাশের চা বাগানের বিশেষ করে উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের পরিবারের মহিলারা কেনাকাটা করতে আসতেন এখানে।”
“মনে করো প্রায় পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত টাউন স্টেশন ছিল এইরকম ঝকঝকে তকতকে আর সদা কর্মব্যস্ত। সকাল সন্ধ্যায় স্টেশনের ব্যস্ততা ছিল চোখে পড়ার মত । সমস্ত রেলকর্মীদের পরনে থাকত রেলের উর্দি। এখানে ছিল রেলওয়ে ভোজনালয়, সেখানে কেতাদুরস্ত উর্দিধারী বাবুর্চি আর বেয়ারার দল! প্ল্যাটফর্মের পাশে ছিল সোরাবজির রেস্তোরাঁ। প্রথমদিকে এখানে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার ছিল না। এই প্রথা বন্ধ হল, কৃষক পার্টির নেতা ফজজুল হকের হস্তক্ষেপে। সে এক রাজকীয় অথচ প্রাণবন্ত আয়োজন ছিল!
“উনিশ শতকের বহু বিখ্যাত ব্যক্তির পদধূলি পড়েছে এই স্টেশনে। এসেছেন গান্ধীজি, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বোস, বাঘাযতীন, রবীন্দ্রনাথ, সুনীতি দেবী, সরোজিনী নাইডু, ফজলুল হক-- এমন অনেকেই। ১৯০৮ সালে বাঘাযতীনের সঙ্গে ইংরেজ পল্টনদের মুষ্টিযুদ্ধ তো এই স্টেশনের এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জন দাশ মারা যান দার্জিলিং-এ। এই শিলিগুড়ি স্টেশন বা আজকের টাউন স্টেশন দিয়ে তাঁর মরদেহ স্পেশাল ট্রেনে করে কলকাতায় রওনা হয়। রবি ঠাকুর অনেকবার এই স্টেশন থেকেই গিয়েছেন কালিম্পঙ আর মংপু। অসুস্থ অবস্থায় যখন কলকাতা যাচ্ছেন কবিগুরু, সেদিনের শিলিগুড়ির বহু মানুষ তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন এই স্টেশনে। গত শতাব্দীর তিরিশ-দশকে দার্জিলিঙ মেল সহ আরেকটি ট্রেনও এই স্টেশন থেকেই কলকাতায় যেত। তার নাম ছিল ‘নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস’। তাছাড়াও, গরমকালের জন্য ‘লাট স্পেশাল” ট্রেন ছিল বলে শুনেছি। আর পুজো স্পেশাল দার্জিলিঙ মেইলও চলত। এই স্পেশাল ট্রেনে খাওয়াদাওয়ার নাকি খুব ঘটা ছিল। শোনা কথা, ক্যাটারিং বগিতে থাকত নানারকমের খাবার, আর তার টানে যাত্রী ছাড়াও শহরবাসী অনেকেই সেসব খাবারের স্বাদ নিতে আসতেন! আর ট্রয় ট্রেন তো ছিলই! যাত্রীবাহী এবং মালবাহী দুই কাজেই দীর্ঘদিন ট্রয়ট্রেন ছিল পাহাড়ি অঞ্চলের একমাত্র পরিবহন মাধ্যম। সময় হিসেব করলে আজকের টাউন স্টেশনের বয়স সম্ভবত একশো বারো।”
বোসকাকু থামলেন। আমি আবার জিগ্যেস করলাম, তাহলে আজ তার এই দশা কেন?
কিছুক্ষণ সময় নিয়ে বোসকাকু ফের বলতে শুরু করলেন, “দেশভাগের একটা পরোক্ষ প্রভাব হয়ত আছেই। দেশভাগের পর রেলপথের পরিবর্তন হয়। ১৯৫০-এর ২৬শে জানুয়ারি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি রেল যোগাযোগ শুরু হল। এর ঠিক এক বছর আগে শিলিগুড়ি শহরের মাঝখান দিয়ে রেললাইন পাতা হল। মহানন্দার পাড় ঘেঁষে তৈরি হল শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন। শিলিগুড়ি থেকে বিশেষ করে উত্তরপূর্ব ভারতের যোগাযোগের ক্ষেত্রে শিলিগুড়ি জংশনের ভূমিকা হয়ে উঠল অনিবার্য এবং বিকল্পহীন। বিশেষ করে আশির দশকের সূচনা পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল শিলিগুড়ি শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত শিলিগুড়ি জংশন। এরপর ফরাক্কা ব্রিজ হওয়ার পর বাড়তে লাগল শিলিগুড়ি ছুঁয়ে যাওয়া ট্রেনের সংখ্যা। সারাভারতের সঙ্গে উত্তরপূর্বের সংযোগস্থল শিলিগুড়ির ভৌগোলিক একটা গুরুত্ব ছিলই। এর সঙ্গে যোগাযোগ ও পরিবহনের কারণে প্রয়োজন হল আরও একটি স্টেশনের। শিলিগুড়ি শহর থেকে ৩-৪ কিলোমিটার দূরে তৈরি হল তৃতীয় রেলস্টেশন। মোটামুটি ওই ১৯৬০ সালই হবে মনে হচ্ছে। প্রথমে এর নাম দেওয়া হয়েছিল ‘নিউ শিলিগুড়ি’। কিন্তু এর অবস্থান জলপাইগুড়ি জেলায় হওয়ার ফলে নাম বদলে রাখা হয় নিউ জলপাইগুড়ি। অনেকটা এলাকা জুড়ে, প্রচুর পরিসেবা আর বিরাট পরিকাঠামো নিয়ে শুরু থেকেই আকর্ষণীয় আর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল নিউ জলপাইগুড়ি জংশন। গুরুত্বহীন হয়ে যেতে থাকল শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন।”
কলেজপডুয়া টুকাই এবার আসরে নামল তার বিবিধ জ্ঞান নিয়ে। “শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন থেকে ন্যারোগেজ লাইনে ট্রয়ট্রেনে করে দার্জিলিং পৌঁছাতে প্রথমদিকে সময় লাগতো প্রায় দশঘণ্টা মত। অসাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতিতে জিগজ্যাগ রাস্তা তৈরি হয়েছিল, আর ছিল লুপ। এরই একটি ঘুম স্টেশনের কাছে বাতাসিয়া লুপ, যা এখন পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। হিলকার্ট রোডের দুধারে বসানো ছিল রেললাইন। এখনকার ভেনাস মোড় ছিল তখনকার রোড স্টেশন। এই ন্যারোগেজের নাম ছিল- ডিএইচআর (দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে)। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ডিএইচআর-কে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করেছে। শিলিগুড়িবাসীর কাছে এটা সত্যিই গর্বের বিষয়। তাছাড়া, এনজেপি বা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনই একমাত্র স্টেশন যেখানে ন্যারোগেজ, মিটার গেজ আর ব্রজগেজ লাইন একসঙ্গে ছিল। এই স্টেশন থেকে ভারতের সবখানে যাওয়া যায়। ১৪৪টারও বেশি ট্রেন এখন এই স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করে। এনজেপি স্টেশনের চাপ বাড়তে থাকায় মালগাড়ি রাখার জন্য এনজেপি থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে রাণীনগর স্টেশনটি তৈরি হয়েছে। এখান থেকে মুঙ্গের, সমস্তিপুর, দ্বারভাঙা -- এসব জায়গাতে তেল, কয়লা, ডলোমাইট যায়। অনেক গাড়ির যন্ত্রপাতি ও অংশবিশেষ বহন করে এই স্টেশন থেকে যাত্রা করে মালবাহী ট্রেনগুলি। এছাড়াও এনজেপি স্টেশনের মাধ্যমে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি আর এমনকি ছোটখাটো জায়গাগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রাখা যাচ্ছে -এতে ব্যবসা বাণিজ্যের বিরাট সুবিধা হয়েছে। এনজেপি রেলপথে ইলেকট্রিফিশেকনের কাজও শেষ হয়েছে বলা যায়, ফলে যোগাযোগ আরও ভালোই হবে - আশা করা যায়।
শিলিগুড়ি শহরের কাছেই বাগডোগরা এয়ারপোর্ট। ১৯৯৫ সালে প্রথম এখান থেকে সেখান থেকে শহরের জনসাধারণের জন্য বিমান চলাচল শুরু হয়। ১৯৯৮ সালে বাগডোগরা - কলকাতা বিমান চালু হয়। ইণ্টারন্যাশনাল ফ্লাইট চলাচল করে এখান থেকে। এখান থেকেই হেলিকপ্টারেও যাওয়া যায় সিকিম ও ভূটান।
আমি দেখলাম উত্তেজিত টুকাই-এর বাংলা ইংরেজি মিলেমিশে যাচ্ছে --আর সে অক্লান্ত একটা শহরের ফিরিস্তি দিয়েই যাচ্ছে! এ অবস্থায় কথা না বলাই ভালো, তাই তাকে বলতে দেওয়াই ভালো।
টুকাই বলে চলল, “এশিয়ান হাইওয়ে তৈরি হওয়ায় শহরের ভেতরে বাইরে যে কোনো জায়গায় যাওয়া সহজ হয়েছে। হিলকার্ট রোড এখন NH110 --এটা শিলিগুড়ি-দার্জিলিং সংযুক্ত করে। NH10 সেভক রোড থেকে গ্যাংটককে সংযুক্ত করেছে। সেভক রোড আর NH10 যেখানে মিশেছে সেখান থেকে শহরের পূর্ব দিকে গিয়েছে ইষ্টার্ণ বাইপাস। শহরের মাঝখানের যে বর্ধমান রোড তা এখন NH27। এশিয়ান হাইওয়ে AH2 শিলিগুড়ি শহরের ওপর দিয়ে যাওয়ায় ব্যবসা তো বেড়েইছে, টুরিজমও যথেষ্ট লাভবান হয়েছে।
শিলিগুড়ি শহরে অন্যতম বাসস্ট্যান্ড তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ড-- ১৯৯০ সালে তৈরি হয় । একে তো সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডও বলা হয়। উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ তো বটেই বিহার, আসাম রুটের বাসও চলাচল করে এই বাসস্ট্যান্ড থেকে। মহানন্দা ব্রিজের শেষ মাথায় আছে সিকিম গভর্নমেণ্টের এসএনটি স্ট্যাণ্ড। এখান থেকে সিকিম রুটের বাস চলাচল করে। সেভক রোডে ডন বসকো মোড়ের কাছে আছে পি সি মিত্তল বাসস্ট্যান্ড। এখান থেকে মালবাজার, চালসা, মেটেলি,, বানারহাট, এথেলবাড়ি, বীরপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলের বাস চলাচল করে। শিলিগুড়ির সবচেয়ে পুরোনো বাসস্ট্যান্ড অবশ্য শহরের কেন্দ্রে কোর্টমোড় বাসস্ট্যান্ড। এর জন্য অবশ্য শিলিগুড়ি শহরের যানজটও বেড়ে গিয়েছে। আবার মাটিগাড়া থেকে কিছুটা দূরে চামটা নদীর ওপরে ১৫০ একর জমি নিয়ে তৈরি হয়েছে পরিবহন নগরী। মূল উদ্দেশ্য অবশ্য ট্রাক টার্মিনাল তৈরি করা। এতে করে শহরের যানজট খানিকটা কমবে, আশা করা যেতে পারে। অবস্থানের কারনে ‘চিকেন নেক’ শিলিগুড়ির গুরুত্ব যেমন আছে, যোগাযোগ ব্যবস্থাও কিন্তু তাক লাগিয়ে দেওয়ার মত করেই নতুন নতুন ধরণে তৈরি হয়ে উঠছে!” এতখানি বলে একটু থামল টুকাই।
আমি বলতে যাচ্ছিলাম, এ সবই কী গুগলের দান? বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। নতুন প্রজন্ম ভাবছে যখন একটা শহর নিয়ে সেটা নেহাতই ফেলে দেওয়া যায় না। আমার ভালোই লাগছিল। বললাম, যেভাবেই তুমি সকাল দেখো সূর্য কিন্তু একটাই!
বোসকাকু নিঃশব্দে একটু হাসলেন। তারপর থেমে থেমে বললেন, “বাকিটা এবার আমি বলি!” আমাদের উৎসুক মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে বলতে থাকলেন— “রেলশহর থেকে বাণিজ্যশহর হয়ে ওঠার মধ্যেই শিলিগুড়ির শহরের ইতিহাস লেখা আছে। শিলিগুড়ি-দার্জিলিং ট্রয় ট্রেনের মধ্যে দিয়ে এই জার্নি শুরু। একটা স্টেশনকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল ছোট্ট একটা জনপদ--সেই স্টেশনটাই টাউন স্টেশন আর ছোট্ট শহরটা আজকের শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি শহরে আগে যাতায়াতের জন্য গরুর গাড়িই চলত। ১৯৫২ সাল থেকেই সম্ভবত রিক্সা চলাচল শুরু হয়। এ সময় ল্যাণ্ডরোভার গাড়ি খুব চলত-- পাহাড়ের রাস্তায় এই গাড়ি ভাড়াও খাটত। শহর থেকে গ্রামে চলত হাটবাস। হাটগুলির মধ্যে অন্যতম মাটিগাড়া হাট আজকেও সগৌরবে চলছে। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল শহর শিলিগুড়িকে। ভৌগোলিক গুরুত্ব তো ছিলই! এই শহরের উত্তর,দক্ষিণ, পশ্চিমে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসীমানা। উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ি! এই গুরুত্ব বুঝেই সংলগ্ন ব্যাঙডুবিতে তৈরি হয়েছিল মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট, বাগডোগরাতে এয়ারফোর্স ক্যান্টনমেণ্ট। সেনাবিভাগের ও তাদের পরিবারের নিত্য প্রয়োজনের জিনিসপত্র এবং শৌখিন জিনিসপত্র সেখানে সুলভে পাওয়া যেত। ষাটের দশকেই তৈরি হয়েছিল ৩১নং জাতীয় সড়ক। ১৯৮১ সালে নাথুলা পাস খুলে দেওয়া হয়। ১৯৯৭ সালে খুলে দেওয়া হয় ফুলবাড়ি বাংলাদেশ বর্ডার। বাণিজ্য তো বটেই পর্যটনের পালেও বাতাস লাগে এর ফলে।
“তবে, আরও দুটি কথা এখানে না বললে চলবে না। শিলিগুড়ি শহরের দক্ষিণ পশ্চিম দিক দিয়ে যে রাস্তা-- বর্ধমানের মহারাজের আনুকূল্যে তা তৈরি হয়েছিল বলে তার নাম বর্ধমান রোড-- সেটাই কিন্তু শহরের সবচেয়ে বড় এবং পুরোনো রাস্তা। বর্ধমান রোড মহানন্দা সেতুতে এসে হিলকার্ট রোডের সঙ্গে মিশেছে। আর মহানন্দা সেতুর কথাও বলতে হবে। ১৯৬৪-৬৫ সালে শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনের সঙ্গে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের সংযোগের জন্য মহানন্দা নদীর উপর দিয়ে একটি রেলসেতু তৈরি করা হয়েছিল। আর, তারও আগে মহানন্দা নদীর উপর প্রথম সড়ক সেতু তৈরি হয়েছিল। এরপর আরও সেতু তৈরি হয় মহানন্দার উপরে, এখন তো আরও সেতু তৈরির পরিকল্পনা চলছে। কিন্তু থাক --আজ সেতুর গল্প থাক। সে গল্প আরেকদিনের জন্য তোলা রইল। যানজট, ব্রিজ, নতুন প্রকল্প সেসব আজ আর হবেনা।”
আমাদের ঘোর কেটে গেল। আড্ডা ভেঙে গেল। টুকাই বলল- “বাকিটা বোলো কিন্তু, ভুলে যেও না।” মুচকি হেসে টুকাই-এর চুলটা ঘেঁটে দিয়ে বোসকাকু যেতে যেতে বললেন “পাগল! নিজের শহরের সংস্কৃতিকে কি ভুলে যেতে আছে?”
Have an account?
Login with your personal info to keep reading premium contents
You don't have an account?
Enter your personal details and start your reading journey with us
Design & Developed by: WikiIND
Maintained by: Ekhon Dooars Team