






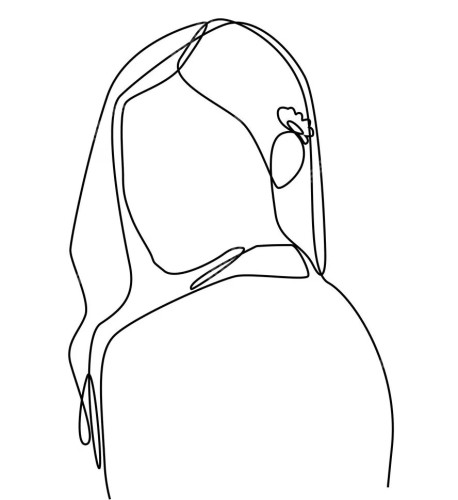



 শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

মোটামুটি বলা যায় যে টাউন ধীরে ধীরে টাউন হয়ে উঠল প্রথমত ইংরেজদের প্রয়োজনে, দ্বিতীয়ত শিক্ষিত সমাজের উৎসাহে এবং বিত্তশালীদের পৃষ্ঠপোষকতায়। লেখাপড়া জানা চাকরিজীবী এবং আইন ব্যবসায়ীদের ভূমিকা ছিল টাউনের চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে তাঁদের চরিত্রটা ছিল ইংরেজ ঘেঁষা। দেশের উন্নতি নিয়ে মাথাব্যথা থাকলেও ইংরেজমুক্ত ভারত তাঁরা ভাবতে পারতেন না।
টাউনে প্রথম দিকে যারা সরকারী চাকরি এবং আইন ব্যবসার সূত্রে এসেছিলেন তাঁরা এসবের ব্যতিক্রম ছিলেন না বলেই ধরা যেতে পারে। ক্রমে পরিস্থিত গোটা বঙ্গদেশ জুড়েই বদলাতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রভাব টাউনে কতটা পড়েছিল সে বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য নেই। একদিক দিয়ে ভাবলে বৈকুন্ঠপুর এবং কুচবিহার ছিল আলাদা রাজ্য। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব তাঁদের বিচলিত করার কথা নয়। কিন্তু টাউনের ভাটিয়া সমাজে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরূপ প্রভাব পড়বে, এটা ধরেই নেওয়া যায়।
অন্যদিকে উনবিংশ শতকের শেষ দিকটা ছিল হিন্দু পুনরুত্থানবাদের যুগ। বাঙালির তখন দরকার ছিল একজন অবতারের। সেটা পুরণ হলো রামকৃষ্ণের মাধ্যমে। টাউনে ‘আর্যনাট্য’ স্থাপন এবং রামকৃষ্ণ মিশনের আবির্ভাব ঘটতে দেরি হয় নি। জেলা শহর হওয়ার কারণে ইংরেজরা একটা ‘জেলা স্কুল’ চালু করে। এই স্কুল স্থাপিত হয় ১৮৭৮ সালে বর্তমান তিস্তা উদ্যানের উলটো দিকে। ১৯০৭ সালে স্কুলঘর অর্থাৎ টিনের ছাউনি দেওয়া কাঠের হলঘরটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ঘটনাটা ছিল বেশ রহস্যজনক। চারু সান্যালের বর্ণনা অনুযায়ী (তিনি তখন স্কুলেরই ছাত্র) বোতলে কেরোসিন ভর্তি করে কাঠের বাক্সে রাখা হয়। মোটা সলতে বোতলের মুখে লাগান ছিল। ওই রকম কয়েকটি বাক্স কাঠের হলঘরের খুব কাছে রেখে সলতেয় আগুন দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে অনেকটা আগুন ধরে যাওয়ার পর বোঝা গেছিল যে আগুন লেগেছে। তখন টাউনে দমকল ছিল না। স্কুলটিকে চোখের সামনে পুড়ে যেতে দেখা ছাড়া উপায় ছিল না কোনও।
চারুবাবুর টিপ্পনি, যারা আগুন লাগিয়েছিল তাঁরা ইঞ্জিনিয়ার হতে পারত।
এই আগুন লাগাবার ঘটনাটিকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী এবং স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন --- ইত্যাদি চিন্তা-ভাবনার ফসল বলে মনে করা হয়। পুড়ে যাওয়ার পর স্কুল আবার তিন মাস বাদে চালু হয় টাউন স্টেশানের কাছে নরেন ভিলার ব্যারাক লাগোয়া মাঠে। সেখানে বড় হলঘরটি তৈরি হয়েছিল খড় দিয়ে। ১৯০৯ সালে সেটাও আগুন লেগে পুড়ে যায়।
দ্বিতীয় অগ্নিকান্ডটা দুর্ঘটনা না পরিকল্পিত তা জানা যায় নি। এরপর স্কুল বর্তমান জায়গায় চলে আসে যেটা ছিল কর্নেল হেদায়েত আলীর বাসস্থান। তিনি কর্নেলত্ব প্রদর্শনের জন্য ইংরেজদের কাছ থেকে পেল্লায় থাকার জায়গা আর বিস্তর জায়গীর পেয়েছিলেন।
১৯১০ সালে জেলা স্কুলের হেড মাস্টার হয়ে আসেন রাজকুমার দাস। জলপাইগুড়িতে তাঁর আসাটা ছিল শাস্তিমূলক বদলি। প্রীতিনিধান রায়ের মতে, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রাজনৈতিক কারণে তাঁকে Degrade করে জলপাইগুড়ির মত ছোট স্কুলে বদলি করা হয়। তিনি ছিলেন বেণীমাধব দাসের বন্ধু লোক।
মুকুলেশ সান্যাল একটি রচনায় এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ধরিয়ে দিয়েছিলেন-- ‘ইংরেজরা জানত জলপাইগুড়ি রাজপরিবারের সঙ্গে কোচবিহার রাজপরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে এবং এই রাজপরিবারকে নিয়ন্ত্রণে রাখলে জেলার অধিকাংশ অধিবাসীর সঙ্গে অ-রাজবংশী শহুরে অধিবাসীদের তফাৎ বজায় রাখা যাবে। একদিকে ইংরেজরা যেমন সেই চেষ্টা করেছে, অপর দিকে শহরের মানুষ নিজেদের ত্রুটির জন্য বিরাট অংশের জেলাবাসীর সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারেন নি। এই পটভূমিতে বাস্তব কারণেই জলপাইগুড়ি জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলন বিলম্বিত ভিন্নতর রূপ লাভ করেছে।’
টাউনে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূত্র ধরেই স্বদেশী চিন্তাভাবনার আমদানি যে ঘটেছিল তার স্বপক্ষে অবশ্য একটা-দুটো তথ্য জানা যায়। ওই সময়ে টাউনের যুবকদের কেউ কেউ গুপ্তসমিতি, নির্জন স্থানে শারীরিক কসরৎ, লাঠি চালনা ইত্যাদি অভ্যাস করতেন এবং গীতা পড়তেন। কলকাতা থেকে কেউ কেউ এসে তাঁদের উৎসাহ যোগাতেন। ১৯০৫ সালেই বিলিতি কাপড়ে আগুন দিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার খবরও পাওয়া যায়। মুকুলেশবাবু এমন কিছু দলের কথা বলেছেন যারা কীর্তন গেয়ে বেড়াত আবার গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করত। টাউনে ওই সময়টায় বন্দুক চুরির পরিমাণ নাকি সাংঘাতিক বেড়ে গিয়েছিল।
বাঙলায় ইংরেজ বিরোধি সশস্ত্র আন্দোলনের সাথে গীতা পড়া এবং গীতা স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করার ব্যাপারটা ভালোমতই জড়িয়ে গিয়েছিল। গীতা হলো হিন্দু ধর্মের সাথে জড়িত গ্রন্থ। ফলে আন্দোলনের সেকুলার দিকটা কিঞ্চিৎ দুর্বল ছিল বলে মনে করা হয়। বিভিন্ন স্মৃতিচারণায় টাউনে ওই সময়কার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া যে সব যুবকদের নাম পাওয়া গেছে তাঁরা সকলেই হিন্দু ছিলেন।
টাউনে তখন হিন্দু-মুসলিম অনুপাতে খুব একটা ফারাক ছিল না এবং প্রচুর বিত্তশালী মুসলিম পরিবারের বাস ছিল টাউনে।
তাই, বিংশ শতকের গোড়া থেকে টাউনে স্বদেশী চেতনা পাখা মেলতে শুরু করেছিল বললে খুব একটা ভুল হয় না। অবশ্য এর একটা পশ্চাদপটও ছিল। নতুন টাউনে বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ থেকে লেখাপড়া জানা পরিবারগুলির সংখ্যা দ্রুত বাড়তে শুরু করছিল উনবিংশ শতকের শেষ থেকে। অচিরেই তাঁরা টাউনে যুগোপযোগী নতুন উত্তেজনা আমদানি করতে শুরু করেন। ফলে বিংশ শতকের প্রথম দেড় দশকে টাউনের চরিত্রের অন্যতম বিষয় হয়ে ওঠে দেশাত্মবোধক ধারণাজাত কর্মকান্ড।
রাজকুমার দাসের মত আরো অনেককেই স্বদেশীপ্রীতির জন্য টাউনে শাস্তিমূলক পোস্টিং দিয়ে পাঠান হত। তাঁরা নিশ্চয়ই টাউনে এসে স্থানীয় নবীন প্রজন্মকে দেশাত্মবোধে উৎসাহিত করতেন। সব মিলিয়ে ১৯০০ সাল থেকে ১৯১৪, অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু পর্যন্ত সময়কালটা টাউনের রাজনৈতিক চরিত্রের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জলপাইগুড়ির রাজাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও ইংরেজরা জগদীন্দ্রদেব রায়কতকে কব্জা করতে পারেন নি। জগদীন্দ্র নাবালক রাজপুত্রের অভিভাবক হিসেবে রাজা হয়েছিলেন এবং নাবালক রাজপুত্র সাবালক হলে রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসের জেলা সভাপতি হন। সরাসরি রাজবংশের লোক না হওয়ার কারণে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিতে তাঁর সমস্যা যেমন ছিল না, তেমনই অভিভাবক হিসেবে রাজত্ব চালানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিচক্ষণতা এবং সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছিলেন বলে প্রজাদের কাছে ছিলেন শ্রদ্ধা-ভালোবাসার পাত্র।
সুতরাং প্রাক্তন রাজা জগদীন্দ্রদেব রায়কত যখন জেলা কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হলেন তখন সেটা হলো বেশ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নাবালক রাজপুত্রকে না ঠকিয়ে, তাঁকে নিয়মমত রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে জগদীন্দ্রদেব যে ভাবে রাজা থেকে খদ্দর পরিহিত গান্ধী-অনুগামী হয়ে পথে নামলেন এবং সাধারণ জীবন যাপন করলেন, তা অবশ্যই একটা দৃষ্টান্ত।
এইসবের মধ্যেই টাউনে একে একে আত্মপ্রকাশ করছিলেন দেশীয় চা-মালিকেরা। জেলা সদর হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পরই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগ দেন ভগবানচন্দ্র বসু। তিনি স্থানীয় আইনজীবীদের চা-শিল্প স্থাপনে প্রচুর উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু তাঁরই সন্তান। যদিও ইংরেজদের মত মূলধন বাঙালিদের ছিল না এবং ডুয়ার্সে বাগানের উপযুক্ত ভালো জমিগুলি তাঁরাই নিয়ে রেখেছিল, তবুও উদ্যোক্তারা শেয়ার বিলির মাধ্যমে টাউনের স্বচ্ছল লোকজনদের কাছ থেকে মূলধন যোগাড় করে টি-কোম্পানি খোলার কাজে লেগে পড়েছিলেন। বিংশ শতকের শুরুতে যখন টাউনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রসারিত হচ্ছে, ততদিনে টাউনের উদ্যোগী বঙ্গ সন্তানেরা স্থাপন করে ফেলেছিলেন বেশ কয়েকটা চা-বাগান।
অর্থাৎ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সময়ে টাউন কেবল রাজনৈতিক ভাবেই নয়, অর্থনৈতিক ভাবেও সক্রিয়। এহেন টাউনের প্রতি অচিরেই বঙ্গীয় রাজনীতিবিদরা আগ্রহী হলেন। টাউনের বাঙালি চা-মালিকেরা এরপর ক্রমশ জেলায় তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করবেন। টাউনের সাথে বাকি জেলার একটা দূরত্ব থেকেই যাবে।
কিন্তু দেশাত্মবোধের অদম্য প্রবাহ শেষাবধি টাউন ছাড়িয়ে পাখা মেলবে অবশিষ্ট জেলায় এবং সেই সূত্রেই গড়ে উঠবে জেলার সাথে সদরের মানসিক সম্পর্কের প্রথম ধাপ।
এসবের মধ্যেই লম্যান সাহেব গত শতকের এক্কেবারে শুরুতেই টাউনে আসেন পুলিশ আধিকারিক হিসেবে। ফুটবলার হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। অচিরেই দেখা গেল নতুন এক দৃশ্য। টাউনের পাড়াগুলোর ফাঁকে ফাঁকে থাকা বড়-ছোট মাঠগুলোতে ছেলেপুলের দল ফুটবল প্র্যাকটিশ করা শুরু করে দিয়েছে। এক অর্থে সেই সাহেব ছিলেন টাউনের ফুটবলের আদি দ্রোণাচার্য। অশোক প্রসাদ সেন লিখেছেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর কালে টাউনের ফুটবল চর্চা ছিল বেশ উন্নত এবং জনপ্রিয়।
টাউনের কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তেন আরো একটা জায়গার লোকজন। সেটা ছিল বেঙ্গল ডুয়ার্স রেল-এর হেড কোয়ার্টার। তার নাম দোমোহানি। চাকরিসূত্রে সেখানে যারা আসতেন তাঁরাও সামিল হয়ে পড়তেন টাউনের ছন্দে। টাউন আর দোমোহানি তো তিস্তার এপাড়-ওপাড়।
অবশ্য এখনকার দোমোহানী-কে দেখলে তা বোঝার উপায় নেই। পল হোয়েল সাহেবের স্কুল এখনো গভীর রাতে সেইসব সুখস্মৃতি রোমন্থন করে কি না জানি না।
(চলবে)
Have an account?
Login with your personal info to keep reading premium contents
You don't have an account?
Enter your personal details and start your reading journey with us
Design & Developed by: WikiIND
Maintained by: Ekhon Dooars Team