





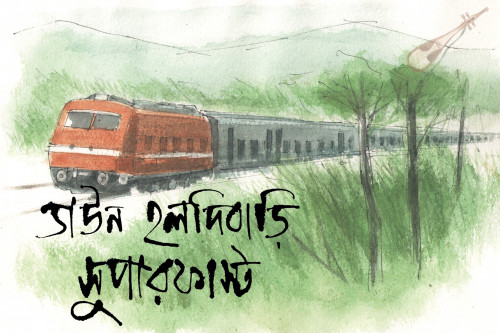
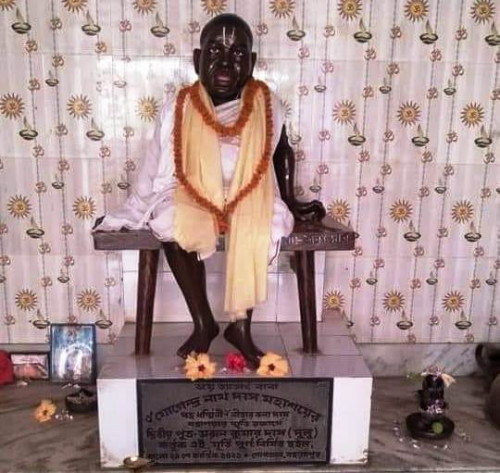






 а¶∞а¶Ња¶Ца¶њ ඙аІБа¶∞а¶Ха¶ЊаІЯа¶ЄаІНඕ
а¶∞а¶Ња¶Ца¶њ ඙аІБа¶∞а¶Ха¶ЊаІЯа¶ЄаІНඕ

а¶ђа¶ња¶Вප පටඌඐаІНබаІАа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓа¶≠а¶Ња¶Ча•§ а¶ЄаІНа¶ђа¶≤аІН඙ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Х а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ ථඌа¶∞аІА ටටබගථаІЗ а¶ЙබаІНа¶≠ගබඐගබаІНа¶ѓа¶Њ, а¶∞ඪඌඃඊථ а¶У а¶ЬаІИа¶ђ-а¶∞ඪඌඃඊථ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ а¶Єа¶Ња¶Ђа¶≤аІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Еа¶ЧаІНа¶∞а¶£аІА а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Уබගа¶ХаІЗ ඙බඌа¶∞аІНඕඐගа¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶Ча¶Ња¶∞аІЗ ටа¶Цථа¶У а¶ХаІЗа¶ђа¶≤ ඙аІБа¶∞аІБඣබаІЗа¶∞а¶З ථගа¶∞а¶ЩаІНа¶ХаІБප а¶Ж඲ග඙ටаІНа¶ѓа•§ ‘඙බඌа¶∞аІНඕඐගа¶ЬаІНа¶ЮඌථаІА’ а¶Жа¶∞ ‘඙аІБа¶∞аІБа¶Ј’ පඐаІНබ බаІБ’а¶Яа¶њ а¶ѓаІЗථ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶∞аІНඕа¶Ха•§ а¶≤а¶ња¶ЩаІНа¶Ча¶ђаІИа¶Ја¶ЃаІНа¶ѓ බаІЛа¶ЈаІЗ බаІБа¶ЈаІНа¶Я а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь ටа¶Цථа¶У а¶≠аІЗа¶ђаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗа¶ЫаІЗ, ඙බඌа¶∞аІНඕඐගа¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶Еа¶ІаІНа¶ѓаІЯථ а¶У а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ ථඌа¶∞аІАබаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ђа¶°аІНа¶° а¶ђаІЗа¶Ѓа¶Ња¶®а¶Ња¶®а•§ ටඐаІБ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶ХаІБа¶Яа¶ња¶≤ а¶≠аІНа¶∞аІВа¶ХаІБа¶Яа¶ња¶ХаІЗ а¶Еа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶єаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЄаІЗа¶З ඙බඌа¶∞аІНඕඐගа¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶З а¶Па¶Х а¶ЕබඁаІНа¶ѓ а¶Жа¶ђаІЗа¶ЧаІЗ а¶ЬаІЬа¶њаІЯаІЗ ඙аІЬа¶≤аІЗථ а¶Па¶Х ටа¶∞аІБа¶£аІА! පаІБа¶ІаІБ ටඌа¶З ථаІЯ, а¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶£а¶ґаІАа¶≤ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь ථගа¶∞аІНඁගට а¶≤а¶ња¶ЩаІНа¶Ч-඙аІНа¶∞ටගඐථаІНа¶Іа¶Хටඌа¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶ХаІЗ а¶Еඃඕඌ а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНа¶ђ බගаІЯаІЗ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶ЃаІВа¶≤аІНඃඐඌථ а¶Єа¶ЃаІЯ ථඣаІНа¶Я а¶Ха¶∞ටаІЗа¶У а¶∞а¶Ња¶Ьа¶њ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ථඌ а¶§а¶ња¶®а¶ња•§ ටඌа¶З ටаІЛ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶∞ а¶Цඌටගа¶∞аІЗ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Еа¶Ха¶ња¶ЮаІНа¶Ъа¶њаІОа¶Ха¶∞ а¶Ча¶≤ගටаІЗ ටගථග ඙аІМа¶Ба¶ЫаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶≠а¶Ња¶Ща¶Ња¶ЪаІЛа¶∞а¶Њ а¶≤аІЛа¶єа¶Ња¶≤а¶ХаІНа¶Ха¶∞ а¶ХаІБаІЬаІЛටаІЗ!
а¶°а¶Ња¶Г ඐග඲ඌථ а¶ЪථаІНබаІНа¶∞ а¶∞а¶ЊаІЯаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ ඙аІЗа¶Ыථ බගа¶Ха¶Ха¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ча¶≤а¶ња•§ а¶ЄаІЗ-а¶Ча¶≤ග඙ඕаІЗа¶∞ а¶Па¶Х а¶Іа¶Ња¶∞аІЗ а¶ЄаІНටаІВ඙аІАа¶ХаІГට а¶єаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ බаІНඐගටаІАаІЯ ඐගපаІНа¶ђа¶ѓаІБබаІНа¶ІаІЗа¶∞ ඐඌටගа¶≤ а¶ЄаІЗථඌ а¶Єа¶∞а¶ЮаІНа¶Ьа¶Ња¶Ѓ - а¶ђа¶ња¶ХаІНа¶∞а¶ња¶∞ а¶Е඙аІЗа¶ХаІНа¶Ја¶ЊаІЯа•§ ටа¶∞аІБа¶£аІАа¶Яа¶њ а¶Еටග බаІНа¶∞аІБට යඌට а¶Ъа¶Ња¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶ЄаІЗа¶З ඙а¶∞ගටаІНа¶ѓа¶ХаІНට а¶≤аІЛа¶єа¶Ња¶≤а¶ХаІНа¶Ха¶∞аІЗа¶∞ ඐග඙аІБа¶≤ а¶ЄаІНටаІВ඙ ඕаІЗа¶ХаІЗ ටаІБа¶≤аІЗ а¶Жථа¶ЫаІЗථ а¶Па¶ХаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶Па¶Х а¶ХаІНа¶ЈаІБබаІНа¶∞ ඃථаІНටаІНа¶∞а¶Ња¶Ва¶ґа•§ а¶Па¶ХаІНа¶Є-а¶∞аІЗ ඃථаІНටаІНа¶∞ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶ЬථаІАаІЯ а¶ЦаІБа¶Ъа¶∞аІЛ ඃථаІНටаІНа¶∞а¶Ња¶ВපаІЗа¶∞ ඪථаІН඲ඌථ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗථ а¶§а¶ња¶®а¶ња•§ а¶°а¶ХаІНа¶Яа¶∞а¶Ња¶≤ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶ѓаІЗ а¶Па¶Ха¶Цඌථඌ а¶Па¶ХаІНа¶Є-а¶∞аІЗ ඃථаІНටаІНа¶∞ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶З а¶єа¶ђаІЗ! а¶Па¶∞ ඙а¶∞ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶ЦаІБа¶ђ а¶ђаІЗපග බගථ а¶Е඙аІЗа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єаІЯථග - а¶Ха¶Ња¶∞а¶£, ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶Єа¶ђ а¶ІаІНඃඌථ඲ඌа¶∞а¶£а¶Ња¶ХаІЗ а¶≠аІЗа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶ЪаІБа¶∞аІЗ аІІаІѓаІЂаІђ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЃаІЗа¶Іа¶Ња¶ђаІА ටа¶∞аІБа¶£аІАа¶Яа¶ња¶З ටаІЛ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶Љ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙බඌа¶∞аІНඕඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ ඙ගа¶Па¶За¶Ъа¶°а¶њ а¶°а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶њ а¶Еа¶∞аІНа¶Ьථа¶Ха¶Ња¶∞аІА ඙аІНа¶∞ඕඁ ථඌа¶∞аІА а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗа¶∞ а¶ЗටගයඌඪаІЗ а¶Еа¶≠аІВට඙аІВа¶∞аІНа¶ђ а¶ХаІГටගටаІНа¶ђаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ХаІНа¶Ја¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ца¶≤аІЗа¶®а•§ පаІБа¶ІаІБ а¶Ха¶њ ටඌа¶З? ඐගපаІНа¶ђа¶ЦаІНඃඌට ඙බඌа¶∞аІНඕඐගа¶ЬаІНа¶ЮඌථаІА а¶Еа¶ІаІНඃඌ඙а¶Х ඪටаІНа¶ѓаІЗථаІНබаІНа¶∞ ථඌඕ а¶ђа¶ЄаІБа¶∞ а¶Па¶З පගඣаІНа¶ѓа¶Ња¶Яа¶њ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗа¶∞ а¶Ьа¶ЧටаІЗ ඐග඙аІБа¶≤ а¶Еඐබඌථ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Ња¶∞ ඙ඌපඌ඙ඌපග, а¶Па¶Ха¶Ьථ පගа¶≤аІН඙аІА, а¶≤аІЗа¶Ца¶Х а¶У а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАටа¶ЬаІНа¶Ю а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶У ටඌа¶Ба¶∞ ඙аІНа¶∞ටගа¶≠а¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ђа¶≤аІНа¶ѓ а¶У а¶ђа¶єаІБа¶ЃаІБа¶ЦаІА а¶ЄаІГа¶ЬථපаІАа¶≤ а¶ХаІНඣඁටඌа¶∞ а¶Єа¶Ња¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ЄаІЗа¶З ටа¶∞аІБа¶£аІАа¶Яа¶њ а¶Жа¶∞ а¶ХаІЗа¶Й ථථ - ටගථග а¶ђа¶ња¶ЦаІНඃඌට ඙බඌа¶∞аІНඕඐගа¶ЬаІНа¶ЮඌථаІА а¶°а¶Г ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Њ а¶Єа¶ња¶Ва¶є!
а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶Яගප а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗа¶∞ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌ පයа¶∞аІЗ аІІаІѓаІ®аІ≠ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ аІІаІ® а¶Еа¶ХаІНа¶ЯаІЛа¶ђа¶∞ ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶Ѓ а¶єа¶ѓа¶Ља•§ а¶ђа¶ња¶Вප පටඌඐаІНබаІАа¶∞ а¶ЪටаІБа¶∞аІНඕ а¶У ඙а¶ЮаІНа¶Ъа¶Ѓ බපа¶ХаІЗ ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Њ а¶ѓа¶Цථ а¶ђаІЗаІЬаІЗ а¶Йආа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗ ටа¶Цථа¶У ථඌа¶∞аІАබаІЗа¶∞ а¶≠аІВа¶Ѓа¶ња¶Ха¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ХආаІЛа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Єа¶Ва¶ЬаІНа¶Юа¶Ња¶ѓа¶Ља¶ња¶§а•§ а¶ЄаІМа¶≠а¶Ња¶ЧаІНඃඐපට ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶Йබඌа¶∞඙ථаІНඕаІА а¶У а¶Жа¶ІаІБථගа¶ХඁථඪаІНа¶Ха•§ ටඌа¶Ба¶∞ ඙ගටඌ а¶°а¶Г ථа¶∞аІЗප а¶ЪථаІНබаІНа¶∞ а¶ЄаІЗථа¶ЧаІБ඙аІНට а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶Єа¶Вඐග඲ඌථ ඐගපаІЗа¶Ја¶ЬаІНа¶Ю а¶Жа¶Зථа¶ЬаІАа¶ђаІАа•§ а¶П а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶У ටගථග а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶Еа¶ІаІНඃඌ඙а¶Х а¶У а¶≤аІЗа¶Ца¶Ха•§ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථ а¶ЪගථаІНටඌ඲ඌа¶∞а¶Ња¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞аІА ථа¶∞аІЗප а¶ЪථаІНබаІНа¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ථඌа¶∞аІА-඙аІБа¶∞аІБа¶ЈаІЗа¶∞ ඪඁඌථඌ඲ගа¶Ха¶Ња¶∞аІЗ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІАа•§ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶Па¶ђа¶В а¶За¶Ва¶∞а¶Ња¶ЬගටаІЗ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ аІђаІЂа¶Яа¶ња¶∞а¶У а¶ђаІЗපග а¶ђа¶За•§ ඙аІНа¶∞ඐථаІНа¶Іа¶У а¶≤а¶ња¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶ЕථаІЗа¶Х, а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ђаІЗප а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඙аІНа¶∞ඐථаІНа¶ІаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶Ја¶ѓа¶Љ а¶Ыа¶ња¶≤ ‘ථඌа¶∞аІА පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ’а•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶Вප а¶Й඙ථаІНа¶ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞а¶У а¶Й඙а¶ЬаІАа¶ђаІНа¶ѓ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯ а¶Ыа¶ња¶≤ ‘ථඌа¶∞аІАа¶ЃаІБа¶ХаІНටග’а•§ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ха¶≤ ඪබඪаІНа¶ѓ, ඐගපаІЗඣට ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ъа¶Ња¶∞ а¶ХථаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶У඙а¶∞, ථа¶∞аІЗප а¶ЪථаІНබаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЬаІАඐථබа¶∞аІНපථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Е඙а¶∞а¶ња¶ЄаІАа¶Ѓа•§ ටඌа¶Ба¶∞а¶З а¶ХථගඣаІНආඌ а¶ХථаІНа¶ѓа¶Њ ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Њ а¶ЄаІЗථа¶ЧаІБ඙аІНට (ඃගථග ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІА а¶ЬаІАඐථаІЗ а¶°а¶Г ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Њ а¶Єа¶ња¶Ва¶є ථඌඁаІЗ а¶Еа¶Іа¶ња¶Х ඙а¶∞а¶ња¶Ъගටග а¶≤а¶Ња¶≠ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ) а¶ѓаІЗ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗа¶∞ а¶Жа¶ХඌපаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЕටаІНа¶ѓаІБа¶ЬаІНа¶ЬаІНа¶ђа¶≤ ථа¶ХаІНඣටаІНа¶∞аІЗ ඙а¶∞а¶ња¶£а¶§ а¶єа¶ђаІЗථ ටඌටаІЗ а¶Жа¶∞ а¶ЖපаІНа¶Ъа¶∞аІНа¶ѓ а¶ХаІА!
඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඌа¶Чට පගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞а¶ЃаІНа¶≠ а¶єа¶ѓа¶Љ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ а¶≤аІЗа¶Х а¶ђа¶Ња¶≤а¶ња¶Ха¶Њ ඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа•§ ඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯа¶Яа¶њ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶ЈаІНආඌ а¶≠а¶ЧаІНථаІА а¶ЄаІБа¶Ја¶Ѓа¶Њ а¶ЄаІЗථа¶ЧаІБ඙аІНа¶§а•§ ටඐаІЗ ඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ ඙ඌආаІНඃ඙аІБа¶ЄаІНටа¶ХаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗа¶У ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Њ а¶У ටඌа¶Ба¶∞ ටගථ බගබග ථඌථඌඐග඲ а¶ђа¶ња¶Ја¶ѓа¶ЉаІЗ ඙аІЬඌපаІЛථඌ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Жа¶ЧаІНа¶∞а¶єаІА а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ђа¶Ња¶°а¶Ља¶ња¶∞ а¶Йබඌа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපаІЗ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ ඙а¶ЫථаІНබඁටаІЛ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ ඙ඌආථ඙ඌආථаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථටඌ ඙аІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ටඌа¶Ба¶∞а¶Ња•§ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ња¶Ха¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶З а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ а¶Пඁථ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗප ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЪගථаІНටඌ඲ඌа¶∞а¶Ња¶ХаІЗ а¶ђа¶ња¶Хපගට а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Єа¶єа¶ЊаІЯа¶Х а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ ටඌа¶З බගබගа¶∞а¶Њ а¶Еа¶∞аІНඕථаІАටග, а¶Еа¶ЩаІНа¶Х, а¶∞а¶Єа¶ЊаІЯථ ථගаІЯаІЗ ඙аІЬඌපаІЛථඌ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶У, ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶Іа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶ХаІГа¶ЈаІНа¶Я а¶єа¶≤аІЗථ ඙බඌа¶∞аІНඕඐගа¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶§а¶ња•§ а¶Жа¶∞ а¶ЄаІЗ-а¶ЄаІНඐ඙аІНථа¶ХаІЗ а¶ђа¶Ња¶ЄаІНටඐඌаІЯගට а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶ЖපаІБටаІЛа¶Ј а¶Ха¶≤аІЗа¶Ь, а¶ЄаІНа¶Ха¶Яගප а¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶Ъ а¶Ха¶≤аІЗа¶Ь а¶єаІЯаІЗ а¶Єа¶∞аІНඐපаІЗа¶ЈаІЗ ටගථග ඙බඌа¶∞аІНඕඐගа¶ЬаІНа¶Юඌථ ථගаІЯаІЗ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъපගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓаІЗ а¶≠а¶∞аІНටග යථ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ а¶Еа¶ІаІАථඪаІНඕ а¶Ѓа¶∞аІНඃඌබඌ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЊаІЯаІЗථаІНа¶Є а¶Ха¶≤аІЗа¶ЬаІЗа•§
а¶Па¶∞а¶З а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ බаІЗа¶ЦටаІЗ-බаІЗа¶ЦටаІЗ аІІаІѓаІ™аІ≠ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ аІІаІЂ а¶Жа¶Ча¶ЄаІНа¶Я а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Па¶≤а•§ බаІЗප а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථ а¶єа¶≤а•§ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථටඌ а¶ЙටаІНටа¶∞ а¶ЪаІВаІЬඌථаІНට а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Х-а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х ඐගපаІГа¶ЩаІНа¶Ца¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶З аІІаІѓаІЂаІІ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶ЄаІНථඌටа¶ХаІЛටаІНටа¶∞ ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶ЊаІЯ а¶ЕඪඌඁඌථаІНа¶ѓ а¶Ђа¶≤ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Ња•§ ඐගපаІНа¶ђа¶ЦаІНඃඌට ඙බඌа¶∞аІНඕඐගа¶ЬаІНа¶ЮඌථаІА ඪටаІНа¶ѓаІЗථаІНබаІНа¶∞ ථඌඕ а¶ђа¶ЄаІБ ටа¶Цථ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ а¶ЦаІЯа¶∞а¶Њ а¶Еа¶ІаІНඃඌ඙а¶Ха•§ а¶Ьа¶єаІБа¶∞а¶ња¶∞ а¶ЪаІЛа¶Ц ටඌа¶Ба¶∞а•§ ඙බඌа¶∞аІНඕඐගа¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටග а¶ЃаІЗа¶Іа¶Ња¶ђаІА ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Еа¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ња¶Х а¶Жа¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶У ථගඣаІНආඌ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЪаІЛа¶Ц а¶ПаІЬа¶Ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ පаІАа¶ШаІНа¶∞а¶З ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ-බа¶≤аІЗа¶∞ ඪබඪаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞аІЗ ථගа¶≤аІЗථ а¶§а¶ња¶®а¶ња•§ а¶Па¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶З а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ а¶ЦаІЯа¶∞а¶Њ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶Ча¶Ња¶∞аІЗ ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶Х а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ ඃඌටаІНа¶∞а¶Ња¶∞а¶ЃаІНа¶≠ а¶єа¶≤а•§
ටඐаІЗ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗа¶∞ а¶Уа¶З ඐගපаІЗа¶Ј පඌа¶Ца¶Ња¶∞ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ-а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ ටа¶Цථ ඙аІБа¶∞аІБඣබаІЗа¶∞а¶З а¶Па¶Ха¶ЪаІНа¶ЫටаІНа¶∞ а¶Ж඲ග඙ටаІНа¶ѓа•§ а¶ђа¶≤а¶Ња¶З а¶ђа¶Ња¶єаІБа¶≤аІНа¶ѓ, ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ ඙බඌа¶∞аІНඕඐගа¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶Єа¶∞аІЗ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶∞а¶З а¶ЪаІЛа¶Ц а¶Х඙ඌа¶≤аІЗ а¶ЙආаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З ටаІБа¶≤а¶≤аІЗථ а¶ЧаІЗа¶≤-а¶ЧаІЗа¶≤ а¶∞а¶ђ! а¶ХаІЗа¶Й-а¶ХаІЗа¶Й а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Еа¶ђа¶ЬаІНа¶Юа¶Њ а¶≠а¶∞аІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ - а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЃаІЗаІЯаІЗ а¶Хගථඌ ඙බඌа¶∞аІНඕඐගа¶ЬаІНа¶Юඌථ ථගаІЯаІЗ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗ, ටඐаІЗа¶З а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ! ටаІОа¶Ха¶Ња¶≤аІАථ а¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶£а¶ґаІАа¶≤ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗ а¶ЄаІНа¶ђа¶≠ඌඐටа¶З ඙аІНа¶∞а¶ђа¶≤ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶≤аІЛа¶Ъථඌа¶∞ а¶ЭаІЬ а¶ЙආаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ХගථаІНටаІБ ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Њ а¶Еට а¶Єа¶єа¶ЬаІЗ а¶єа¶Ња¶∞ а¶ЃаІЗථаІЗ ඙ගа¶Ыа¶њаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඙ඌටаІНа¶∞аІА а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶®а¶Ња•§ ටаІАа¶ђаІНа¶∞ ඁඌථඪගа¶Х පа¶ХаІНටගටаІЗ а¶≠аІЗа¶ЩаІЗ а¶ЧаІБа¶БаІЬа¶њаІЯаІЗ බගඃаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь ථගа¶∞аІНඁගට а¶≤а¶ња¶ЩаІНа¶Ч-඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАа¶∞а•§ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІА а¶єаІЯаІЗ а¶Йආඐඌа¶∞ ඙ඕаІЗ а¶ХаІЛථаІЛ а¶ђа¶Ња¶Іа¶Ња¶З ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶И඙аІНඪගට а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Яа¶≤ඌටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа¶®а¶ња•§ а¶Еа¶ІаІНඃඌ඙а¶Х ඪටаІНа¶ѓаІЗථаІНබаІНа¶∞ථඌඕ а¶ђа¶ЄаІБа¶У ටඌа¶Ба¶∞ а¶Па¶З а¶ЕඪඌඁඌථаІНа¶ѓ а¶ЃаІЗа¶Іа¶Ња¶ђаІА а¶ЫඌටаІНа¶∞аІАа¶Яа¶ња¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶Ча¶≠аІАа¶∞ а¶Жа¶ЄаІНඕඌ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§
඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯ а¶Ыа¶ња¶≤- ‘X-ray crystallography of clay minerals’а•§ а¶Еа¶ІаІНඃඌ඙а¶Х ඪටаІНа¶ѓаІЗථаІНබаІНа¶∞ ථඌඕ а¶ђа¶ЄаІБ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶ЄаІНඕඌථ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶∞ ථඁаІБථඌ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶Ха¶∞аІЗ, ටඌ඙аІАаІЯ а¶У а¶∞а¶Ња¶Єа¶ЊаІЯථගа¶Х ඐගපаІНа¶≤аІЗа¶Ја¶£аІЗа¶∞ ඙ඌපඌ඙ඌපග а¶Па¶ХаІНа¶Є-а¶∞аІЗ а¶ђа¶ња¶ХаІНа¶ЈаІЗ඙ ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶њаІЯа¶Њ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ а¶≤а¶Ња¶Ча¶њаІЯаІЗ, а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ а¶Ха¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ ඙а¶∞а¶Ња¶Ѓа¶∞аІНප බගඃඊаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗа•§ ටඌа¶З а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞ඌඕඁගа¶Х ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶ЊаІЯаІЗ ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Ња¶∞ ඐගපаІЗа¶Ј ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьථ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Па¶Ха¶Цඌථඌ а¶Па¶ХаІНа¶Є-а¶∞аІЗ ඃථаІНටаІНа¶∞аІЗа¶∞а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЄаІЗ-а¶Жа¶Ѓа¶≤аІЗ а¶Па¶ХаІНа¶Є-а¶∞аІЗ ඃථаІНටаІНа¶∞ а¶Єа¶єа¶Ьа¶≤а¶≠аІНа¶ѓ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ ටඌа¶З а¶Еа¶ІаІНඃඌ඙а¶Х ඪටаІНа¶ѓаІЗථаІНබаІНа¶∞ ථඌඕ а¶ђа¶ЄаІБа¶∞ ඙а¶∞а¶Ња¶Ѓа¶∞аІНපаІЗ ඪගබаІН඲ඌථаІНට ථගа¶≤аІЗථ, а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶ЬථаІАаІЯ ඃථаІНටаІНа¶∞඙ඌටග ථගа¶ЬаІЗа¶З ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗа¶®а•§ а¶Ца¶ђа¶∞ ඙аІЗа¶≤аІЗථ, а¶УаІЯаІЗа¶≤а¶ња¶Ва¶Яථ а¶ЄаІНа¶ХаІЛаІЯа¶Ња¶∞аІЗ а¶°а¶Ња¶Г ඐග඲ඌථ а¶ЪථаІНබаІНа¶∞ а¶∞а¶ЊаІЯаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ ඙аІЗа¶ЫථаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌටаІЗ а¶ђа¶ња¶ХаІНа¶∞а¶њ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ බаІНඐගටаІАаІЯ ඐගපаІНа¶ђа¶ѓаІБබаІНа¶ІаІЗа¶∞ ඐඌටගа¶≤ а¶ѓаІБබаІНа¶І а¶Єа¶∞а¶ЮаІНа¶Ьа¶Ња¶Ѓа•§ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ යඌටаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඃථаІНටаІНа¶∞а¶Ња¶Вප а¶ХаІБаІЬа¶њаІЯаІЗ, а¶ХගථаІЗ ථගа¶≤аІЗථ а¶§а¶ња¶®а¶ња•§ а¶ЄаІЗа¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶ЬаІБаІЬаІЗа¶З ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶≤аІЗථ а¶Па¶Х පа¶ХаІНටගපඌа¶≤аІА а¶Па¶ХаІНа¶Є-а¶∞аІЗ ඃථаІНටаІНа¶∞ а¶У а¶ЕථаІНඃඌථаІНа¶ѓ බа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶њ ඃථаІНටаІНа¶∞а¶™а¶Ња¶§а¶ња•§ а¶ЗථаІНа¶°а¶њаІЯඌථ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶Ња¶°аІЗа¶Ѓа¶њ а¶Еа¶ђ а¶Єа¶ЊаІЯаІЗථаІНа¶Є а¶Ха¶∞аІНටаІГа¶Х ඙аІНа¶∞а¶Хඌපගට Lilavati’s Daughters: The Women Scientists of India а¶ђа¶ЗටаІЗ а¶°а¶Г ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Њ а¶Єа¶ња¶Ва¶є а¶ЄаІНа¶ЃаІГටග а¶∞аІЛඁථаІНඕථ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗа¶ЫаІЗථ- ‘а¶ЄаІЗ-а¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶Љ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ѓа¶Љ බපа¶Ьථ а¶Ца¶ѓа¶Ља¶∞а¶Њ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶Ча¶Ња¶∞аІЗ ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶ЃаІВа¶≤а¶Х а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶ѓа¶Љ а¶ђаІНඃඌ඙аІГට а¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶Чට ඙аІНа¶∞а¶ѓа¶ЉаІЛа¶Ьථ а¶ЕථаІБа¶Єа¶Ња¶∞аІЗ ථගа¶Ь ථගа¶Ь ඃථаІНටаІНа¶∞඙ඌටග ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶®а¶ња¶§а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶Ча¶Ња¶∞аІЗ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Ња¶З а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Еа¶≤а¶ња¶Цගට ථගаІЯа¶Ѓа•§… а¶Па¶ХаІНа¶Є-а¶∞аІЗ а¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶ђа¶∞аІЗа¶Яа¶∞ගටаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ථගа¶∞ථаІНටа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶ЊаІЯ පаІЗа¶Ја¶ЃаІЗප ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ѓа¶Љ ඙а¶ЮаІНа¶Ъඌපа¶Яа¶њ а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶∞ ථඁаІБථඌа¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙аІВа¶∞аІНа¶£ පаІНа¶∞аІЗа¶£аІАඐගථаІНа¶ѓа¶Ња¶Є а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ а¶єаІЯ, а¶ѓаІЗඁථ - Kaolinite, Montmorillonite, Illite, Vermiculite, Chlorite а¶ЗටаІНа¶ѓа¶Ња¶¶а¶ња•§’ а¶Еа¶ђа¶Ња¶Х යටаІЗ а¶єаІЯ, а¶Жа¶Ьа¶ХаІЗа¶∞ а¶Жа¶ІаІБථගа¶Х а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗа¶∞ а¶ѓаІБа¶ЧаІЗа¶У ථගа¶ЬаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьථ а¶ЕථаІБа¶Єа¶Ња¶∞аІЗ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶Ча¶Ња¶∞ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞аІЗ ථаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Еа¶Ха¶≤аІН඙ථаІАа¶ѓа¶Љ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а•§ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ЖපаІНа¶Ъа¶∞аІНа¶ѓ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞ а¶єа¶≤, а¶Па¶З а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Жа¶∞аІНඕගа¶Х а¶Єа¶Ња¶єа¶Ња¶ѓаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Жа¶Єа¶Ња¶Ѓ а¶Еа¶ѓа¶ЉаІЗа¶≤ а¶ХаІЛа¶ЃаІНа¶™а¶Ња¶®а¶ња•§ а¶ЄаІЗ-а¶ѓаІБа¶ЧаІЗ а¶ђаІИа¶ЬаІНа¶Юඌථගа¶Х а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ පගа¶≤аІН඙аІЛබаІНа¶ѓаІЛа¶Ч а¶Єа¶Ва¶ЄаІНඕඌа¶∞ а¶Єа¶єа¶ѓаІЛа¶Чගටඌа¶∞ යඌට а¶ђа¶ЊаІЬа¶њаІЯаІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ ඐගපаІЗа¶Ј පаІЛථඌ а¶ѓаІЗට а¶®а¶Ња•§
ථගа¶∞а¶≤а¶Є а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ පаІЗа¶ЈаІЗ аІІаІѓаІЂаІЂ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Њ ‘X-ray & differential thermal analysis of Indian clays’ පаІАа¶∞аІНа¶Ја¶Х а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ ඪථаІНබа¶∞аІНа¶≠а¶Яа¶њ а¶Ьа¶Ѓа¶Њ බаІЗථ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа•§ аІІаІѓаІЂаІђ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ ඙ගа¶Па¶За¶Ъа¶°а¶њ а¶°а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶њ ඙аІНа¶∞බඌථ а¶Ха¶∞аІЗа•§ ටගථගа¶З ඙аІНа¶∞ඕඁ ථඌа¶∞аІА ඃගථග а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙බඌа¶∞аІНඕඐගа¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗ ඙ගа¶Па¶За¶Ъа¶°а¶њ а¶°а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶њ а¶≤а¶Ња¶≠ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ЄаІЗ-а¶ђа¶Ыа¶∞а¶З а¶Еа¶ІаІНඃඌ඙а¶Х ඪටаІНа¶ѓаІЗථаІНබаІНа¶∞ ථඌඕ а¶ђа¶ЄаІБ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶Љ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Еа¶ђа¶Єа¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ХගථаІНටаІБ ටඌටаІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ ඕаІЗа¶ЃаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа¶®а¶ња•§ ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Ња¶¶аІЗа¶∞ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶Х බа¶≤а¶Яа¶њ а¶Еа¶ІаІНඃඌ඙а¶Х а¶Ха¶Ѓа¶≤а¶Ња¶ХаІНа¶Ј බඌපа¶ЧаІБ඙аІНටаІЗа¶∞ а¶Еа¶ІаІАථаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶∞ ථඁаІБථඌа¶∞ а¶ХඌආඌඁаІЛа¶Чට а¶ђаІИපගඣаІНа¶ЯаІНа¶ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶Жа¶∞а¶У а¶ђа¶ња¶ЄаІНටඌа¶∞ගට а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§
඙аІНа¶∞а¶Єа¶ЩаІНа¶Чට а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶ЦаІНа¶ѓ, аІІаІѓаІЂаІ© а¶Єа¶Ња¶≤ ථඌа¶Чඌබ ඙аІГඕගඐаІАа¶∞ а¶Е඙а¶∞ ඙аІНа¶∞ඌථаІНටаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІАа¶∞а¶Њ а¶°а¶ња¶Пථа¶П-а¶Па¶∞ а¶ЧආථටථаІНටаІНа¶∞ а¶ЬඌථටаІЗ а¶Па¶Ха¶З а¶Па¶ХаІНа¶Є-а¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ч ඙බаІН඲ටග а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞ටаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ටඌа¶З а¶Ха¶≤а¶ХඌටඌаІЯ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь පаІЗа¶Ј а¶Ха¶∞аІЗ а¶°а¶Г ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Њ а¶Єа¶ња¶Ва¶є а¶ђа¶ЊаІЯаІЛа¶Ђа¶ња¶Ьа¶ња¶ХаІНа¶ЄаІЗ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъටа¶∞ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඙ඌаІЬа¶њ බගа¶≤аІЗථ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶Хගථ а¶ЃаІБа¶≤аІБа¶ХаІЗа•§ аІІаІѓаІђаІ© ඕаІЗа¶ХаІЗ аІІаІѓаІђаІ™ а¶Єа¶Ња¶≤ а¶Еа¶ђа¶Іа¶њ а¶Єа¶ЃаІЯа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ ටගථග а¶ЄаІНа¶ЯаІНඃඌථ඀а¶∞аІНа¶° ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЯаІЛа¶Ђа¶ња¶Ьа¶ња¶ХаІНа¶Є а¶ђа¶ња¶≠а¶Ња¶ЧаІЗ а¶°а¶Г а¶єа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶° යඌථаІНа¶Я ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶∞ ටටаІНටаІНඐඌඐ඲ඌථаІЗ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶Па¶ђа¶В ‘Origin of life’ ථඌඁа¶Х а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඐගපаІЗа¶Ј ඙аІНа¶∞а¶Ха¶≤аІН඙аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ѓаІБа¶ХаІНට ඕඌа¶ХаІЗа¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЄаІЗ-а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞а¶Яа¶њ а¶Пඁථ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶ЬаІАа¶ђа¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶У ඙බඌа¶∞аІНඕඐගа¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗඁගපаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶∞ а¶Па¶ХаІНа¶Є-а¶∞аІЗ а¶ХඌආඌඁаІЛа¶ХаІЗ а¶°а¶ња¶Пථа¶П-а¶Па¶∞ а¶ЧආථටථаІНටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ටගථග а¶ЬаІНඃඌඁගටගа¶Ха¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ටаІБа¶≤ථඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Па¶ђа¶В ටඌබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ඪඌබаІГපаІНа¶ѓ а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬаІЗ ඙аІЗаІЯаІЗ а¶ђа¶ња¶ЄаІНඁගට а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§
බаІЗපаІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІА බаІБ’බපа¶Х а¶Ьа¶ња¶Уа¶≤а¶Ьа¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ а¶Єа¶Ња¶∞аІНа¶≠аІЗ а¶Еа¶ђ а¶ЗථаІНа¶°а¶њаІЯа¶Њ а¶Па¶ђа¶В а¶ђаІЛа¶Є а¶ЗථඪаІНа¶Яа¶ња¶Яа¶ња¶Йа¶ЯаІЗ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶°а¶Г а¶Єа¶ња¶Ва¶єа•§ ටඌа¶∞ ඙а¶∞аІЗ ටගථග а¶ЄаІЗථаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶Ња¶≤ а¶ЧаІНа¶≤а¶Ња¶Є а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶£аІНа¶° а¶ЄаІЗа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ња¶Х а¶ЗථඪаІНа¶Яа¶ња¶Яа¶ња¶Йа¶ЯаІЗ а¶°аІЗ඙аІБа¶Яа¶њ а¶°а¶ња¶∞аІЗа¶ХаІНа¶Яа¶∞аІЗа¶∞ ඙බ а¶Еа¶≤а¶ЩаІНа¶ХаІГට а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶ЄаІЗа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ња¶Х а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ а¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІЗ ථගඃаІБа¶ХаІНට ඕаІЗа¶ХаІЗа¶ЫаІЗථ а¶§а¶ња¶®а¶ња•§ а¶П а¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶Љ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Еа¶ІаІАට а¶ЬаІНа¶Юඌථа¶ХаІЗ පаІИа¶≤аІН඙ගа¶Х а¶Й඙ඌඃඊаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ХаІНа¶≤аІЗ а¶Ѓа¶°аІЗа¶≤а¶ња¶В පගа¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථа¶ХаІЗ а¶Ьථ඙аІНа¶∞а¶њаІЯ а¶Ха¶∞аІЗ ටаІБа¶≤ටаІЗ а¶У а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶Єа¶ЪаІЗටථටඌ а¶ђаІГබаІНа¶Іа¶ња¶∞ а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓаІЗ ඙බඌа¶∞аІНඕඐගа¶ЬаІНа¶ЮඌථаІА ඪටаІНа¶ѓаІЗථаІНබаІНа¶∞ ථඌඕ а¶ђа¶ЄаІБ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ‘а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІАа¶ѓа¶Љ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ ඙а¶∞ගඣබ’а•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІАаІЯ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ ඙а¶∞ගඣබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶У а¶Єа¶∞аІНඐටаІЛа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ѓаІБа¶ХаІНට ඕаІЗа¶ХаІЗа¶ЫаІЗථ а¶°а¶Г а¶Єа¶ња¶Ва¶єа•§

а¶Ыа¶ђа¶њ - а¶ЃаІЗа¶≤а¶Ња¶ЃаІЗපඌа¶∞ ඙ඌආපඌа¶≤а¶Њ
а¶ђа¶ња¶ЦаІНඃඌට ථаІГටටаІНටаІНඐඐගබ а¶°а¶Г а¶ЄаІБа¶∞а¶Ьа¶њаІО а¶Єа¶ња¶Ва¶єаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ђа¶ња¶ђа¶Ња¶є а¶ЄаІВටаІНа¶∞аІЗ а¶ЖඐබаІНа¶І а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶°а¶Г ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Њ а¶Єа¶ња¶Ва¶єа•§ а¶°а¶Г а¶ЄаІБа¶∞а¶Ьа¶њаІО а¶Єа¶ња¶Ва¶є ඙а¶∞аІЗ ඐගපаІНа¶ђа¶≠а¶Ња¶∞ටаІА ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ а¶Й඙ඌа¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶ѓ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Й඙а¶ЬඌටаІАа¶ѓа¶Љ а¶Ьථа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАа¶∞ а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ьථ ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Њ а¶ЕථаІБ඲ඌඐථаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Еඐබඌථ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶§а¶ња¶®а¶ња•§ а¶ЬаІАඐථඪа¶ЩаІНа¶ЧаІАа¶∞ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ а¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІН඙а¶∞аІНපаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ ථаІГටටаІНටаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞ටගа¶У а¶Жа¶ХаІГа¶ЈаІНа¶Я යථ а¶°а¶Г ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Њ а¶Єа¶ња¶Ва¶єа•§ а¶Й඙а¶ЬඌටаІАаІЯ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ха¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶£аІЗа¶У а¶ђаІНа¶∞ටаІА යථ а¶§а¶ња¶®а¶ња•§ а¶ЄаІЗ-а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓаІЗа¶З а¶Па¶З а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІА බඁаІН඙ටග පඌථаІНටගථගа¶ХаІЗටථ а¶У ටඌа¶∞ а¶ЖපаІЗ඙ඌපаІЗа¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ а¶Еථа¶ЧаІНа¶∞а¶Єа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЖබගඐඌඪаІА а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ЃаІЗаІЯаІЗබаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶Х а¶ЕථаІНа¶ѓа¶Іа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞ ඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯ а¶ЄаІНඕඌ඙ථ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ЄаІЗ-ඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ ථඌඁа¶Цඌථඌ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђаІЬа¶З а¶ЕථථаІНа¶ѓ - ‘а¶ЃаІЗа¶≤а¶Ња¶ЃаІЗපඌа¶∞ ඙ඌආපඌа¶≤а¶Њ’а•§ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Ња¶ІаІБа¶≤аІЛ а¶Жа¶∞ පගа¶≤аІН඙а¶Ъа¶∞аІНа¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓ බගаІЯаІЗа¶З а¶ЫаІЛа¶ЯаІЛබаІЗа¶∞ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ බඌථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶§а•§
а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶У а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ьа¶њ බаІБа¶Яа¶њ а¶≠ඌඣඌටаІЗа¶З а¶ђаІЗප а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ЃаІВа¶≤аІНඃඐඌථ а¶ЧаІНа¶∞ථаІНඕ а¶∞а¶Ъථඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶°а¶Г ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Њ а¶Єа¶ња¶Ва¶єа•§ а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІАаІЯ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ ඙а¶∞ගඣබ а¶Ха¶∞аІНටаІГа¶Х ඙аІНа¶∞а¶Хඌපගට ‘а¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶У а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ’ ථඌඁа¶Х а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ ඙ටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Ња¶ЯගටаІЗ ටගථග ථගаІЯඁගට а¶≤а¶ња¶ЦටаІЗа¶®а•§ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථа¶ХаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶≠а¶Ња¶Ја¶ЊаІЯ а¶Ьථ඙аІНа¶∞а¶њаІЯ а¶Ха¶∞аІЗ ටаІБа¶≤а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ѓаІЗ а¶ЄаІНඐ඙аІНථ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІА ඪටаІНа¶ѓаІЗථаІНබаІНа¶∞ථඌඕ බаІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, а¶ЄаІЗ а¶ЄаІНඐ඙аІНථа¶ХаІЗ а¶ђа¶Ња¶ЄаІНටඐඌаІЯගට а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙аІНа¶∞а¶≠аІВට а¶Еඐබඌථ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ටගථග, а¶Жа¶∞ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЄаІЗ-а¶Ха¶Ња¶Ьа¶ХаІЗ а¶ЄаІНа¶ђаІАа¶ХаІГටග а¶ЬඌථඌටаІЗ а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІАа¶ѓа¶Љ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ ඙а¶∞ගඣබ аІ®аІ¶аІ¶аІІ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ ‘ඪටаІНа¶ѓаІЗථаІНබаІНа¶∞ථඌඕ а¶ђаІЛа¶Є а¶ЃаІЗа¶ЃаІЛа¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶≤ а¶Па¶УаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶°’ බගаІЯаІЗ а¶Єа¶ЃаІНඁඌථගට а¶Ха¶∞аІЗа•§ ටඌа¶Ба¶∞ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Х, ඙ඕ඙аІНа¶∞බа¶∞аІНපа¶Х а¶У පаІБа¶≠а¶Ња¶Ха¶Ња¶ЩаІНа¶ХаІНа¶ЈаІА а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІА ඪටаІНа¶ѓаІЗථаІНබаІНа¶∞ ථඌඕ а¶ђа¶ЄаІБа¶ХаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶Па¶Ха¶Ња¶Іа¶ња¶Х ඙аІНа¶∞ඐථаІНа¶І а¶У а¶ЧаІНа¶∞ථаІНඕ а¶∞а¶Ъථඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗථ а¶°а¶Г а¶Єа¶ња¶Ва¶єа•§ ටඌа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ටගථа¶Яа¶њ ඐගපаІЗа¶Ја¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ца¶ѓаІЛа¶ЧаІНа¶ѓ- аІІ) а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ ඪඌ඲ථඌа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞а¶Ња¶ѓа¶Љ ඪටаІНа¶ѓаІЗථаІНබаІНа¶∞ථඌඕ а¶ђа¶ЄаІБ (඙аІНа¶∞а¶Хඌපа¶Х- ඐගපаІНа¶ђ ඐගබаІНа¶ѓа¶Њ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶є), аІ®) а¶Еа¶Ѓа¶∞ а¶Хඕඌ (аІІаІѓаІ≠аІ© а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ ටඌа¶Ба¶∞ ථаІЗа¶УаІЯа¶Њ ඪටаІНඃථаІНබаІНа¶∞ථඌඕаІЗа¶∞ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Яа¶њ а¶Єа¶Ња¶ХаІНа¶Ја¶ЊаІОа¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶Ха¶≤ථ, ඙аІНа¶∞а¶Хඌපа¶Х- а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІАа¶ѓа¶Љ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ ඙а¶∞ගඣබ), аІ©) ඪටаІНа¶ѓаІЗථ а¶ђа¶ЄаІБа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගටаІНа¶ђ а¶У ඁථථаІЗа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞а¶Њ (බаІЗප ඙ටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Ња¶ѓа¶Љ ඙аІНа¶∞а¶Хඌපගට ඙аІНа¶∞ඐථаІНа¶І)а•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Па¶Ха¶Ња¶Іа¶ња¶Х а¶ЃаІВа¶≤аІНඃඐඌථ ඙аІНа¶∞ඐථаІНа¶І ඙аІНа¶∞а¶Хඌපගට а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶ПපගаІЯа¶Ња¶Яа¶ња¶Х а¶ЄаІЛа¶Єа¶Ња¶За¶Яа¶ња¶∞ а¶Ьа¶Ња¶∞аІНථඌа¶≤аІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶У а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶ђа¶ња¶≠а¶Ња¶ЧаІЗ а¶Па¶ђа¶В а¶За¶ХаІЛථаІЛа¶Ѓа¶ња¶Х а¶ПථаІНа¶° ඙а¶≤а¶ња¶Яа¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ а¶Йа¶За¶Ха¶≤ගටаІЗа•§ ටඌ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ ඙බඌа¶∞аІНඕඐගබ а¶Па¶∞а¶Йа¶Зථ පаІНа¶∞аІЛа¶°а¶ња¶Ва¶Ча¶Ња¶∞аІЗа¶∞ 'Mind and Matter' а¶Па¶ђа¶В а¶ђаІЛа¶ЄаІНа¶Яථ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЯаІЛа¶ЃаІЗа¶°а¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ а¶За¶ЮаІНа¶ЬගථගаІЯа¶Ња¶∞а¶ња¶ВаІЯаІЗа¶∞ а¶Еа¶ІаІНඃඌ඙а¶Х а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІНа¶Єа¶ња¶Ѓ а¶°аІЗа¶≠а¶ња¶°аІЛа¶≠а¶ња¶Ъ а¶ЂаІНа¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶ЩаІНа¶Х-а¶Ха¶Ња¶ЃаІЗථаІЗටඪаІНа¶Ха¶ња¶∞ 'Unravelling DNA: The Most Important Molecule of Life' а¶ђа¶З බаІБ’а¶Яа¶њ ටගථග а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶ЊаІЯ а¶ЕථаІБඐඌබ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§
а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶Ъа¶∞аІНа¶Ъа¶Ња¶∞ ඙ඌපඌ඙ඌපග පගа¶≤аІН඙а¶Ха¶≤а¶Њ а¶У а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАටаІЗа¶У а¶°а¶Г ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Њ а¶Єа¶ња¶Ва¶єаІЗа¶∞ а¶ЕඪඌඁඌථаІНа¶ѓ ඙ඌа¶∞බа¶∞аІНපගටඌ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ඃඌඁගථаІА а¶Ча¶ЩаІНа¶ЧаІЛ඙ඌ඲аІНа¶ѓа¶ЊаІЯаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ටගථග යගථаІНබаІБа¶ЄаІНටඌථаІА а¶ІаІНа¶∞аІБ඙බаІА а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАටаІЗа¶∞ ටඌа¶≤а¶ња¶Ѓ ථаІЗа¶®а•§ аІІаІѓаІ≠аІ¶ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАටаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶ђа¶З а¶≤аІЗа¶ЦаІЗථ - 'An Approach to the Study of Indian Music', ඙аІНа¶∞а¶Хඌපа¶Ха¶Г Indian Publicationsа•§ а¶Пඁථа¶Ха¶њ а¶°а¶Г а¶ЄаІБа¶∞а¶Ьа¶њаІО а¶Єа¶ња¶Ва¶є а¶ѓа¶Цථ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓа¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ ඙аІБа¶∞аІБа¶≤а¶њаІЯа¶Њ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ а¶ЖබගඐඌඪаІА а¶Ьථа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАа¶∞ а¶Й඙а¶∞ ථаІГටඌටаІНටаІНа¶ђа¶ња¶Х а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ а¶Ха¶∞а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, ටа¶Цථ ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Ња¶У ටඌа¶Ба¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЄаІЗ-а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ ථඌථඌඐග඲ а¶≤аІЛа¶Ха¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАට а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАටаІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶≤аІЛа¶Ха¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАටаІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞аІЗ а¶Па¶Ха¶Ња¶Іа¶ња¶Х ඙аІНа¶∞ඐථаІНа¶І а¶∞а¶Ъථඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶°а¶Г ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Њ а¶Єа¶ња¶Ва¶єа•§ аІІаІѓаІЃаІЃ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶Ьа¶Ња¶∞аІЛаІЯඌබаІЗа¶∞ а¶ЧඌථаІЗ а¶ђаІИබගа¶Х ඁථаІНටаІНа¶∞аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђ а¶ЕථаІБඪථаІН඲ඌථ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶ЖථаІНබඌඁඌථ ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶ЫаІБа¶ЯаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ а¶§а¶ња¶®а¶ња•§ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Па¶Х а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶ЃаІВа¶≤а¶Х ඙аІНа¶∞ඐථаІНа¶І - 'Jarawa Songs and Vedic Chant: A Comparison of Melodic Pattern'а•§ аІ®аІ¶аІ¶аІЂ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶ПපගаІЯа¶Ња¶Яа¶ња¶Х а¶ЄаІЛа¶Єа¶Ња¶За¶Яа¶ња¶∞ а¶Ьа¶Ња¶∞аІНථඌа¶≤аІЗ а¶ЄаІЗа¶З ඙аІНа¶∞ඐථаІНа¶І ඙аІНа¶∞а¶Хඌපගට а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЃаІЗаІЯаІЗа¶∞а¶Њ а¶ѓаІЗ ටඐа¶≤а¶Ъа¶њ යටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ, а¶Па¶З а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶Њ а¶ЄаІЗ-а¶Жа¶Ѓа¶≤аІЗ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Ха¶≤аІН඙ථඌа¶∞а¶У а¶ЕටаІАа¶§а•§ а¶ЄаІЗа¶З ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶ІаІНඃඌථ඲ඌа¶∞а¶£а¶Ња¶ХаІЗ а¶≠аІЗа¶ЩаІЗа¶ЪаІБа¶∞аІЗ බගаІЯаІЗ а¶™а¶£аІНධගට а¶ЬаІНа¶Юඌථ ඙аІНа¶∞а¶Хඌප а¶ШаІЛа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ටගථග ටඐа¶≤а¶Ња¶∞ ටඌа¶≤а¶ња¶Ѓ ථගඃඊаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ඙аІНа¶∞а¶ЦаІНඃඌට පගа¶≤аІН඙аІА а¶ЧаІЛ඙ඌа¶≤ а¶ШаІЛа¶Ј а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЪගටаІНа¶∞පගа¶≤аІН඙аІЗа¶∞ а¶ЧаІБа¶∞аІБа•§ а¶≠а¶Ња¶ЄаІНа¶Ха¶∞аІНа¶ѓ-ථගа¶∞аІНа¶Ѓа¶Ња¶£аІЗа¶∞а¶У ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ඪගබаІНа¶Іа¶єа¶ЄаІНа¶§а•§ а¶Еа¶ђа¶Єа¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£аІЗа¶∞ ඙а¶∞аІЗ ටගථග පඌථаІНටගථගа¶ХаІЗටථаІЗ ඙ඌа¶Хඌ඙ඌа¶Ха¶њ а¶ђа¶Єа¶ђа¶Ња¶Є а¶Ха¶∞ටаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ЄаІЗ-а¶Єа¶ЃаІЯ а¶°а¶Г а¶Єа¶ња¶Ва¶є а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАට а¶≠ඐථаІЗ ‘а¶Ђа¶ња¶Ьа¶ња¶ХаІНа¶Є а¶Еа¶ђ а¶Ѓа¶ња¶Йа¶Ьа¶ња¶Х’ а¶ХаІЛа¶∞аІНа¶Є а¶Ъа¶Ња¶≤аІБ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶Па¶ђа¶В а¶ЄаІНඕඌථаІАаІЯ а¶ХаІБа¶ЃаІЛа¶∞බаІЗа¶∞ а¶Єа¶єа¶ѓаІЛа¶ЧගටඌаІЯ а¶ЃаІГаІОපගа¶≤аІН඙аІЗа¶∞ а¶ЙථаІНථаІЯථа¶Ха¶≤аІН඙аІЗ ථගаІЯа¶Ьගට а¶єа¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶њ а¶У а¶ЄаІЗа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ња¶ХаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶ЄаІНа¶Ха¶∞аІНа¶ѓ පаІНа¶∞аІАථගа¶ХаІЗටථаІЗ ඐගපаІНа¶ђа¶≠а¶Ња¶∞ටаІАа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞යපඌа¶≤а¶ЊаІЯ а¶Єа¶ЬаІНа¶Ьගට а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЕථඐබаІНа¶ѓ а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶Па¶Ха¶Цඌථග а¶ЃаІНа¶ѓаІБа¶∞а¶Ња¶≤ ඐගපаІНа¶ђа¶≠а¶Ња¶∞ටаІА ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ а¶Й඙ඌа¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤аІЛа¶∞ බаІЗа¶ѓа¶Ља¶Ња¶≤аІЗа¶∞ පаІЛа¶≠а¶Њ а¶ђа¶∞аІН඲ථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ъа¶≤аІЗа¶ЫаІЗ а¶Жа¶Ьа¶Уа•§
඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Ња¶∞ බаІБа¶З а¶ХථаІНа¶ѓа¶Њ а¶ЄаІБ඙а¶∞аІНа¶£а¶Њ а¶У а¶ЄаІБа¶ХථаІНа¶ѓа¶Њ а¶Ѓа¶ЊаІЯаІЗа¶∞ බаІЗа¶ЦඌථаІЛ ඙ඕаІЗ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ ඪඌ඲ථඌ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Єа¶Ђа¶≤ ඙බඌа¶∞аІНඕඐගබ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶°а¶Г а¶ЄаІБ඙а¶∞аІНа¶£а¶Њ а¶Єа¶ња¶Ва¶є ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ѓа¶ЊаІЯаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ЃаІГටගа¶Ъа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ - ‘ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ පаІЗа¶ЈаІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ, а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඁථаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ѓаІЗ а¶Ыа¶ђа¶ња¶Яа¶њ а¶∞а¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗ ටඌ а¶єа¶≤ - ටගථග а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶°аІЗа¶ЄаІНа¶ХаІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗථ а¶Па¶ђа¶В ඁථаІЗ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£аІЗ (а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІНа¶Єа¶ња¶Ѓ) а¶Ха¶Ња¶ЃаІЗථаІЗටඪаІНа¶Ха¶ња¶∞ а¶ђа¶З ‘Unraveling DNA: The Most Important Molecule of Life’ а¶ЕථаІБඐඌබ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ъа¶≤аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ЄаІЗ-а¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶Љ ටඌа¶∞ බаІГа¶ЈаІНа¶Яගපа¶ХаІНටග а¶ХаІНа¶ЈаІАа¶£ а¶єаІЯаІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗ, ටඌа¶З පඐаІНබа¶ЧаІБа¶≤а¶њ ඙ධඊඐඌа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Жටප а¶Ха¶Ња¶Ба¶Ъ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єа¶§а•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Жа¶ІаІБථගа¶Ха¶Ха¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶°а¶ња¶Пථа¶П-а¶Па¶∞ а¶Ѓа¶≤а¶ња¶ХаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ђа¶ЊаІЯаІЛа¶Ђа¶ња¶Ьа¶ња¶ХаІНа¶Є ථගඃඊаІЗ ටගථග а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ а¶Ха¶∞ටаІЗථ, а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶ЄаІЗ-а¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶Љ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЄаІЗа¶З а¶Єа¶Ва¶ХаІНа¶∞ඌථаІНට а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ටඌටаІНටаІНа¶ђа¶ња¶Х а¶Ха¶Ња¶Ьа¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІЗ ථගаІЯаІЛа¶Ьගට а¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ ඪටаІНа¶ѓа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Еа¶∞аІНඕаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Й඙ඪаІНඕගටග а¶Єа¶Ха¶≤а¶ХаІЗа¶З а¶ЕථаІБ඙аІНа¶∞аІЗа¶∞а¶£а¶Њ а¶ѓаІЛа¶Ча¶Ња¶§а•§ ටගථග а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶У පගа¶≤аІН඙аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГට а¶Єа¶ВඁගපаІНа¶∞а¶£а•§’
аІ®аІ¶аІІаІЂ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ аІІаІІ а¶ЬаІБа¶≤а¶Ња¶З а¶°а¶Г ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Њ а¶Єа¶ња¶Ва¶є ඙а¶∞а¶≤аІЛа¶Х а¶Чඁථ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ටඐаІЗ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ ථඌа¶∞аІА а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІАබаІЗа¶∞ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶£аІЗа¶∞ ඙ඕаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЬаІАඐථ а¶У а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶ХඌථаІНа¶° පа¶ХаІНටගපඌа¶≤аІА а¶ЕථаІБ඙аІНа¶∞аІЗа¶∞а¶£а¶Њ а¶єаІЯаІЗ а¶ђаІЗа¶Ба¶ЪаІЗ ඕඌа¶Ха¶ђаІЗа•§ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗа¶∞ а¶Ьа¶ЧටаІЗ а¶ЄаІБබаІАа¶∞аІНа¶Ша¶Ха¶Ња¶≤ а¶Єа¶Ђа¶≤а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ђа¶ња¶Ъа¶∞а¶£ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶У а¶Єа¶ЃаІНඁඌථ а¶ђа¶Њ а¶ЦаІНඃඌටගа¶∞ ඙аІЗа¶ЫථаІЗ а¶ХаІЛථаІЛа¶Ха¶Ња¶≤аІЗа¶З а¶ЫаІЛа¶ЯаІЗථථග а¶°а¶Г а¶Єа¶ња¶Ва¶єа•§ а¶Пඁථа¶Ха¶њ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶Х а¶ЬаІАඐථаІЗ а¶Па¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶Ъа¶≤а¶Ња¶∞ ඙ඕаІЗ а¶ѓа¶Ња¶Ба¶∞а¶Њ ඙аІНа¶∞ටගඐථаІНа¶Іа¶Хටඌ а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶ЪаІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗа¶У а¶Ха¶Цථа¶Уа¶З а¶ХаІЛථаІЛ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶ЖථаІЗа¶®а¶®а¶ња•§ а¶Жа¶ЬаІАඐථ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ ඁථа¶ХаІЗ а¶Ха¶≤аІБඣටඌ а¶ЃаІБа¶ХаІНට а¶∞а¶Ња¶Ца¶ђа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓ а¶ЄаІНඕගа¶∞ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ а¶ЃаІЗටаІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶ЫаІЗථ а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶∞ а¶ЖථථаІНබаІЗа•§ а¶ЄаІГа¶ЬථපаІАа¶≤ а¶У පаІИа¶≤аІН඙ගа¶Х а¶ХаІНඣඁටඌа¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Па¶ђа¶В ඙බඌа¶∞аІНඕඐගа¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶ХඌපаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ථගа¶∞а¶≤а¶Єа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶З а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ ඙а¶∞ග඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶§а¶Њ а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬаІЗ ඙аІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶§а¶ња¶®а¶ња•§ ටඌа¶Ба¶∞ ඐඌධඊගටаІЗ а¶Ха¶ђа¶њ, ඕගඃඊаІЗа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගටаІНа¶ђ, а¶Ъа¶≤а¶ЪаІНа¶ЪගටаІНа¶∞ ථගа¶∞аІНඁඌටඌ, а¶ЪගටаІНа¶∞පගа¶≤аІН඙аІА, а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАටа¶ЬаІНа¶Ю, а¶Ха¶ња¶Ва¶ђа¶Њ ඙аІНа¶∞ඕගටඃපඌ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІАබаІЗа¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤ ථගටаІНа¶ѓ ඃඌටඌаІЯа¶Ња¶§а•§ ථගа¶Ь а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ЧаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЪаІБа¶∞ බаІБа¶ЈаІН඙аІНа¶∞ඌ඙аІНа¶ѓ а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶У а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶Єа¶Ња¶ЃаІЯа¶ња¶ХаІАа¶∞ а¶Па¶Х а¶ђа¶ња¶∞а¶Ња¶Я а¶ЧаІНа¶∞ථаІНඕඌа¶Ча¶Ња¶∞ а¶ЧаІЬаІЗ ටаІБа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶ђа¶ЊаІЬගටаІЗа•§ ඙බඌа¶∞аІНඕඐගа¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ, а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАට-පගа¶≤аІН඙а¶Ха¶≤а¶Њ а¶Ъа¶∞аІНа¶Ъа¶Њ, а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶≤аІЗа¶Ца¶њ, а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටග а¶Ха¶∞аІНටඐаІНа¶ѓ-- а¶Єа¶ђаІЗටаІЗа¶З ටඌа¶Ба¶∞ ඙аІНа¶∞ටගа¶≠а¶Ња¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ХаІНа¶Ја¶∞ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ а¶Па¶З а¶ЕබаІНඐගටаІАаІЯ ඙аІНа¶∞ටගа¶≠а¶Ња¶ЃаІЯаІАа•§ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯපа¶З а¶ђа¶≤ටаІЗ පаІЛථඌ а¶ѓаІЗට - ‘а¶Єа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ЬаІАඐථ а¶ЄаІГа¶ЬථපаІАа¶≤ ඕඌа¶ХаІБа¶®а•§’ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ ඪඌ඲ථඌа¶∞ ඙ඕаІЗ ටගථග а¶ѓаІЗ а¶ЕඪඌඁඌථаІНа¶ѓ а¶ХаІАа¶∞аІНටග а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ, ටඌ а¶Жа¶Ьа¶У а¶Еа¶Ча¶£а¶ња¶§ ථඌа¶∞аІАа¶ХаІЗ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗа¶∞ ථඌථඌථ а¶Іа¶Ња¶∞а¶ЊаІЯ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶ЕථаІБ඙аІНа¶∞аІЗа¶∞а¶£а¶Њ а¶ѓаІЛа¶Ча¶ЊаІЯа•§ ඙аІБа¶∞аІБඣටඌථаІНටаІНа¶∞а¶ња¶Хටඌа¶∞ පаІГа¶ЩаІНа¶Ца¶≤ а¶≠аІЗа¶ЩаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගа¶Яа¶њ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ ථඌа¶∞аІАබаІЗа¶∞ ථගа¶Ьа¶ЄаІНа¶ђ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථ ඙а¶∞а¶ња¶Єа¶∞ а¶ЧаІЬаІЗ ටаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ а¶≤аІЬа¶Ња¶ЗаІЯаІЗ а¶°а¶Г ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶Ѓа¶Њ а¶Єа¶ња¶Ва¶єаІЗа¶∞ ඁටаІЛ ඪටаІНඃථගඣаІНආ, а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶ђаІАа¶∞ а¶У ඐගබаІВа¶ЈаІА ථඌа¶∞аІАа¶∞ а¶Еඐබඌථ а¶ЕථඪаІНа¶ђаІАа¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ѓа•§
--------------------------------------------------------------------------------------------------
඙а¶∞ගපаІЗа¶ЈаІЗ а¶ђа¶≤ටаІЗа¶З а¶єаІЯ, а¶≤а¶ња¶ЩаІНа¶Ч ථගа¶∞඙аІЗа¶ХаІНа¶Ја¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ а¶≠аІВа¶Ца¶£аІНа¶°аІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗа¶∞ а¶ЗටගයඌඪаІЗа¶∞ ඙аІБථа¶∞аІНථගа¶∞аІНа¶Ѓа¶Ња¶£ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Ьа¶∞аІБа¶∞а¶ња•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£, а¶ђаІБබаІНа¶Іа¶ња¶ђаІГටаІНටගа¶Х а¶ЕථаІНටа¶∞аІНබаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶∞ а¶Еа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ටඌ а¶≤а¶ња¶ЩаІНа¶Ч а¶ђаІИа¶Ја¶ЃаІНа¶ѓ බаІЛа¶ЈаІЗ බаІБа¶ЈаІНа¶Яа•§ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗа¶∞ а¶Еа¶ЧаІНа¶∞а¶ЧටගටаІЗ ථඌа¶∞аІА а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІАа¶∞а¶Њ а¶Єа¶ХаІНа¶∞а¶њаІЯа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Еа¶Вපа¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶У, බаІБа¶∞аІНа¶≠а¶Ња¶ЧаІНඃඐපට ඙аІБа¶∞аІБඣටථаІНටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶ІаІНа¶ђа¶Ьа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞аІА а¶ЗටගයඌඪඐගබබаІЗа¶∞ а¶Еа¶ђа¶ЃаІВа¶≤аІНඃඌඃඊථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗа¶∞ а¶ЗටගයඌඪаІЗ ථඌа¶∞аІАබаІЗа¶∞ а¶Еඐබඌථа¶ХаІЗ а¶За¶ЪаІНа¶Ыа¶Ња¶ХаІГටа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Е඙ථаІЯ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ЄаІНа¶ђа¶≠ඌඐටа¶З а¶Кථඐගа¶Вප පටа¶ХаІЗа¶∞ පаІЗа¶ЈаІЗ а¶У а¶ђа¶ња¶Вප පටа¶ХаІЗа¶∞ а¶ЧаІЛаІЬа¶Ња¶∞ බපа¶Ха¶ЧаІБа¶≤ගටаІЗ а¶Жа¶ІаІБථගа¶Х а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗа¶∞ а¶Еа¶ЧаІНа¶∞а¶Чටගа¶∞ а¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶ѓаІЗ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶Єа¶Ња¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞а¶Њ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ පඌа¶Ца¶Ња¶∞ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ-඙ඕаІЗ а¶Жа¶≤аІЛа¶Ха¶ђа¶∞аІНටගа¶Ха¶Њ යඌටаІЗ а¶Па¶Ха¶Ња¶ХаІА а¶єаІЗа¶Ба¶ЯаІЗ а¶П බаІЗපаІЗа¶∞ а¶≠а¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶ѓаІО а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ ඙аІНа¶∞а¶њаІЯ ථඌа¶∞аІАබаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЄаІЗ-඙ඕ а¶Жа¶≤аІЛа¶ХаІЛа¶ЬаІНа¶ЬаІНа¶ђа¶≤ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ - ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶ХගථаІНටаІБ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ а¶≤аІЛа¶Ха¶Ъа¶ХаІНа¶ЈаІБа¶∞ а¶ЕථаІНටа¶∞а¶Ња¶≤аІЗа¶За•§ а¶ЄаІНа¶∞аІЛටаІЗа¶∞ ඐග඙а¶∞аІАටаІЗ а¶Еථටගа¶ХаІНа¶∞а¶ЃаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞ටගඐථаІНа¶Іа¶Хටඌа¶ХаІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІА а¶Ха¶∞аІЗ а¶Па¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶Ъа¶≤а¶Њ а¶ЄаІЗа¶З ථඌа¶∞аІА а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІАබаІЗа¶∞ а¶ЬаІАඐථ, а¶≤аІЬа¶Ња¶З а¶У а¶Еඐබඌථа¶ХаІЗ а¶Жа¶∞а¶У а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНа¶ђ බගаІЯаІЗ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗа¶∞ а¶ЗටගයඌඪаІЗа¶∞ а¶ЃаІВа¶≤а¶ЄаІНа¶∞аІЛටаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶Жа¶Єа¶Њ а¶ЖපаІБ ඙аІНа¶∞а¶ѓа¶ЉаІЛа¶Ьа¶®а•§ ටඐаІЗа¶З а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗа¶∞ ඙аІБථа¶∞аІНа¶Ьа¶Ња¶Ча¶∞а¶£ а¶У а¶ЬаІЯඃඌටаІНа¶∞а¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГට а¶Зටගයඌඪ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗ а¶Єа¶∞аІНඐටаІЛа¶∞аІВ඙аІЗ а¶ЙථаІНа¶ЃаІЛа¶Ъගට а¶єа¶ђаІЗа•§
------------------------------ x -------------------------------
Have an account?
Login with your personal info to keep reading premium contents
You don't have an account?
Enter your personal details and start your reading journey with us
Design & Developed by: WikiIND
Maintained by: Ekhon Dooars Team