










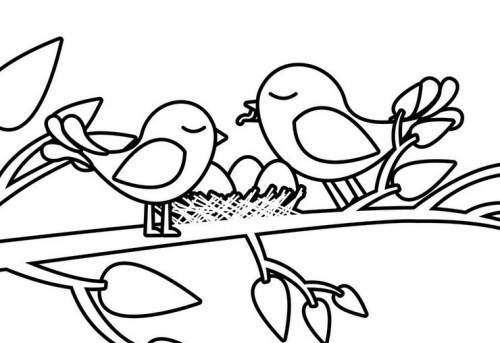


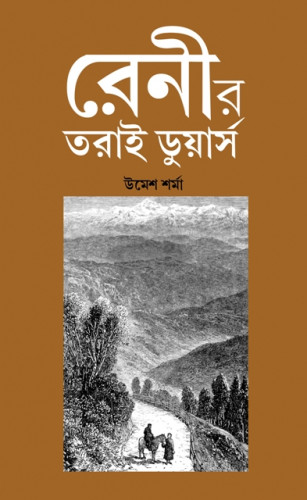



 а¶°. а¶∞а¶Ња¶Ьа¶∞аІНа¶Ја¶њ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є
а¶°. а¶∞а¶Ња¶Ьа¶∞аІНа¶Ја¶њ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є

බаІАа¶∞аІНа¶Ш ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ ඪඌට බපа¶ХаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯа¶єаІАථටඌ, а¶ЕථඪаІНටගටаІНа¶ђ, а¶Еа¶Єа¶єа¶ЊаІЯටඌ, а¶ЄаІНටඐаІН඲ටඌ, බаІАа¶∞аІНа¶ШපаІНа¶ђа¶Ња¶Є, ථගа¶∞ඌ඙ටаІНටඌයаІАථටඌ а¶У ටඕඌа¶Хඕගට а¶Єа¶≠аІНඃටඌа¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙аІВа¶∞аІНа¶£ ඐග඙а¶∞аІАට ඃඌ඙ථаІЗа¶∞ ඙а¶∞ ಮಶಲಀටаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ђа¶Ња¶ЄаІАа¶∞а¶Њ а¶ЖපඌаІЯ а¶ђаІБа¶Х а¶ђаІЗа¶Ба¶ІаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤ ඐගථගඁаІЯ а¶ѓаІЗථ а¶Ыа¶ња¶≤ ‘බаІНඐගටаІАаІЯ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථටඌ බගඐඪ’а•§ аІ©аІІ а¶ЬаІБа¶≤а¶Ња¶З а¶ЄаІВа¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶ЄаІНටаІЗа¶∞ ඙а¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶ЕථаІНа¶Іа¶Ха¶Ња¶∞аІЗ ථගඁа¶ЬаІНа¶Ьගට а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶ЬаІЗථඌа¶∞аІЗа¶Яа¶∞ а¶У ඁපඌа¶≤аІЗа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛаІЯ а¶Жа¶≤аІЛа¶Хගට а¶єаІЯаІЗ а¶ЙආаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ බаІЗපа¶≠а¶Ња¶ЧаІЗа¶∞ ඙а¶∞ аІђаІЃ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ ඐථаІНබаІАබපඌ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЃаІБа¶ХаІНටගа¶∞ а¶ЖථථаІНබаІЗ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶ња¶≤ යථ а¶Ьඌටග඲а¶∞аІНа¶Ѓ ථගа¶∞аІНඐගපаІЗа¶ЈаІЗ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗа¶За•§ а¶ЄаІАඁඌථаІНටаІЗа¶∞ а¶П඙ඌа¶∞аІЗ а¶Єа¶ђ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤ а¶ЬඌටаІАаІЯ ඙ටඌа¶Ха¶ЊаІЯ а¶У а¶Жа¶≤аІЛа¶∞ а¶∞аІЛපථඌа¶ЗаІЯаІЗ а¶≠аІЗа¶ЄаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ аІІа¶≤а¶Њ а¶Жа¶Ча¶ЄаІНа¶Я а¶ЄаІЗа¶З а¶Рටගයඌඪගа¶Х а¶ЃаІБа¶єаІВа¶∞аІНටаІЗ ඙аІЛаІЯඌටаІБа¶∞ а¶ХаІБආග, ඁපඌа¶≤а¶°а¶Ња¶Ща¶Њ, а¶ђа¶Ња¶Ха¶Ња¶≤а¶ња¶∞ а¶ЫаІЬа¶Њ, පගඐ඙аІНа¶∞ඪඌබ а¶ЃаІБа¶ЄаІНට඀ග, ථа¶≤а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ, а¶Ђа¶≤ථඌ඙аІБа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶≠аІГටග а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗපаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Х а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗ а¶Єа¶Ха¶Ња¶≤ аІѓа¶Яа¶ЊаІЯ а¶Ѓа¶єа¶Ња¶Єа¶Ѓа¶Ња¶∞аІЛа¶єаІЗ ටаІНа¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНа¶£ а¶∞а¶ЮаІНа¶Ьගට а¶ЬඌටаІАаІЯ ඙ටඌа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЙටаІНටаІЛа¶≤ථ а¶Ха¶∞аІЗථ ඙аІНа¶∞පඌඪථаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞аІНටඌඐаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶∞а¶Ња•§ а¶Па¶ХаІЗ а¶Е඙а¶∞а¶ХаІЗ а¶Жа¶≤а¶ња¶ЩаІНа¶Чථ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Ѓа¶ЮаІНа¶Ъ а¶ђа¶Ња¶Ба¶Іа¶Њ а¶єаІЯа•§ ථаІЗටඌа¶∞а¶Њ а¶Жа¶ЄаІЗа¶®а•§ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤ ඐගථගඁаІЯаІЗ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Рටගයඌඪගа¶Х а¶ЕඐබඌථаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ බаІГ඙аІНටа¶Ха¶£аІНආаІЗ а¶ШаІЛа¶Ја¶£а¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ බගаІЯаІЗ ඃඌථ а¶Па¶Ха¶Ња¶Іа¶ња¶Х ඙аІНа¶∞ටගපаІНа¶∞аІБටගа¶Уа•§ බපа¶ХаІЗа¶∞ ඙а¶∞ බපа¶Х а¶Іа¶∞аІЗ а¶ђа¶ЮаІНа¶Ъථඌ а¶У а¶Еа¶ђа¶єаІЗа¶≤а¶ЊаІЯ ඕඌа¶Ха¶Њ යටබа¶∞ගබаІНа¶∞ ඁඌථаІБа¶Ја¶ЧаІБа¶≤а¶њ බගථ ඙ඌа¶≤аІНа¶ЯඌථаІЛа¶∞ а¶ЄаІНඐ඙аІНථ බаІЗа¶ЦටаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§
а¶ХගථаІНටаІБ а¶Еа¶Ъа¶ња¶∞аІЗа¶З ඀ඌථаІБа¶ЄаІЗа¶∞ ඁට а¶Йа¶ђаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ЄаІЗ’а¶Єа¶ђ а¶ЄаІНඐ඙аІНа¶®а•§ а¶Па¶З а¶ЄаІНඐ඙аІНථа¶≠а¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶З ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ ඁඌථаІБа¶Ј а¶≠а¶ња¶ЯаІЗа¶Ѓа¶Ња¶Яа¶њ а¶ЫаІЗаІЬаІЗ ඪ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗ а¶ЄаІАඁඌථаІНටаІЗа¶∞ а¶У඙ඌа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ ‘а¶Е඙පථ’ බගаІЯаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Жа¶ЄаІЗථ а¶П඙ඌа¶∞аІЗа•§ ටඌа¶БබаІЗа¶∞а¶У а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ЄаІНඐ඙аІНа¶®а•§ а¶Па¶ЄаІЗ а¶УආаІЗථ ‘а¶Пථа¶ХаІНа¶≤аІЗа¶≠ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙аІЗ’а•§ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶Жа¶ЄаІЗ ඪඌටа¶Ъа¶≤аІНа¶≤ගප а¶У а¶Па¶ХඌටаІНටа¶∞аІЗ පа¶∞а¶£а¶Ња¶∞аІНඕаІАබаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙ ඃඌ඙ථаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ЃаІГа¶§а¶ња•§ ඙ඌа¶∞аІНඕа¶ХаІНа¶ѓ а¶Па¶Ха¶Яа¶Ња¶З а¶Па¶З а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙аІЗа¶∞ а¶ЖපаІНа¶∞ගටа¶∞а¶Њ а¶єа¶≤аІЗථ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯа•§ а¶Па¶Ба¶∞а¶Ња¶У а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ බаІАа¶∞аІНа¶Ш а¶ЕථаІБථаІНථаІЯථаІЗа¶∞ а¶Еа¶ВපаІАබඌа¶∞ а¶Па¶ђа¶В а¶≠а¶Ња¶ЧаІНа¶ѓ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථаІЗа¶∞ а¶ЄаІНඐ඙аІНථ ථගаІЯаІЗа¶З а¶ПබаІЗපаІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ ඪඌට බපа¶ХаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЮаІНа¶Ъථඌ а¶У а¶ЕථаІБථаІНථаІЯථ а¶ХаІЛථ ඃඌබаІБа¶¶а¶£аІНа¶° බගаІЯаІЗ а¶Па¶Х а¶≤а¶єа¶Ѓа¶ЊаІЯ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටගට а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Ха¶Ња¶∞аІНඃට а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Еа¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђа•§ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІНඃඌපඌа¶∞ ඙ඌа¶∞බ а¶Пටа¶З а¶Ка¶∞аІНа¶ІаІНа¶ђа¶ЃаІБа¶ЦаІА а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ѓаІЗ ටඌ а¶Еа¶Ъа¶ња¶∞аІЗа¶З ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථටඌа¶∞ ඁට а¶ЄаІНඐ඙аІНථа¶≠а¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ ඙аІБථа¶∞а¶Ња¶ђаІГටаІНටග а¶Ша¶ЯаІЗа•§
а¶ЙථаІНථаІЯථ
ඪබаІНа¶ѓ а¶≠а¶Ња¶∞ටа¶≠аІБа¶ХаІНට а¶Па¶З а¶Еටග ඙аІНа¶∞ඌථаІНටගа¶Х а¶У а¶ЕථаІБථаІНථට а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Х а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶ХаІЗ ඙ඌа¶∞аІНපаІНа¶ђа¶ђа¶∞аІНටаІА а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ ඪඁ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶ЊаІЯ а¶≠аІБа¶ХаІНට а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьථ а¶Ыа¶ња¶≤ ඙ඌයඌаІЬ ඙аІНа¶∞а¶Ѓа¶Ња¶£ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞а•§ а¶Па¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶У ඐග඙аІБа¶≤ а¶Еа¶∞аІНඕаІЗа¶∞ а¶ѓаІЗ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьථ, а¶ЄаІЗа¶Хඕඌ ඙аІНа¶∞පඌඪථаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞аІНටඌඐаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶∞а¶Њ а¶Єа¶ЃаІНа¶ѓа¶Х а¶ЬඌථටаІЗа¶®а•§ ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Х а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗа¶∞ а¶ЙථаІНථаІЯථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ аІ©аІ¶аІ¶аІЃ а¶ХаІЛа¶Яа¶њ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ а¶ШаІЛа¶Ја¶£а¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Па¶З ඐග඙аІБа¶≤ а¶Еа¶∞аІНඕ а¶ђа¶∞ඌබаІНබаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ පаІБථаІЗ а¶Еа¶Єа¶єа¶ЊаІЯ ඁඌථаІБа¶Ја¶ЧаІБа¶≤а¶њ බගථ ඐබа¶≤аІЗа¶∞ а¶ЄаІНඐ඙аІНථ බаІЗа¶ЦටаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ХගථаІНටаІБ ඙аІНа¶∞ඌඕඁගа¶Х а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Еа¶∞аІНඕ а¶ђа¶∞ඌබаІНබ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ ඁඌටаІНа¶∞ аІЂаІ¶ а¶ХаІЛа¶Яа¶њ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Ња•§ а¶ЄаІАඁගට а¶Еа¶∞аІНඕаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶У ඙аІНа¶∞පඌඪථаІЗа¶∞ ටа¶∞а¶ЂаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶єаІЯ а¶ЙථаІНථаІЯථаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶ѓа¶ЬаІНа¶Юа•§ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌа¶Ша¶Ња¶Я, а¶Ха¶Ња¶≤а¶≠а¶Ња¶∞аІНа¶Я а¶У а¶ЄаІЗටаІБ ථගа¶∞аІНа¶Ѓа¶Ња¶£, ඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯ а¶У а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІНඕаІНа¶ѓ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ а¶ЄаІНඕඌ඙ථ, ඙ඌථаІАаІЯ а¶Ьа¶≤аІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌ, а¶ђаІИබаІНа¶ѓаІБටගа¶Ха¶∞а¶£, а¶Ха¶Ѓа¶ња¶Йථගа¶Яа¶њ а¶єа¶≤ а¶ЄаІНඕඌ඙ථ ඙аІНа¶∞а¶≠аІГටග а¶Еа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ ඙ඌаІЯа•§ а¶Па¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶У ‘а¶Ьа¶ђ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶°’, ‘а¶∞аІЗපථ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶°’, ‘а¶Жа¶Іа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶°’ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶Яа¶ња¶У ඙аІНа¶∞ඌ඲ඌථаІНа¶ѓ ඙аІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§
а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ а¶≠аІВа¶Ца¶£аІНа¶°аІЗа¶∞ а¶ЕථаІНටа¶∞аІНа¶Чට а¶ѓаІЗ аІЂаІІа¶Яа¶њ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗපаІА а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤ а¶ПබаІЗපаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНටа¶∞аІНа¶≠аІБа¶ХаІНට а¶єаІЯ, а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶Вපа¶З а¶ХаІБа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Жа¶∞ බපа¶Яа¶Њ а¶ЄаІАඁඌථаІНටඐа¶∞аІНටаІА а¶Ъа¶ња¶∞ а¶Еа¶ђа¶єаІЗа¶≤ගට а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ ඁටа¶За•§ а¶ХаІЛථа¶У а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ යගථаІНබаІБ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶Еа¶ІаІНа¶ѓаІБඣගට, а¶ХаІЛථа¶Яа¶њ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථ а¶Еа¶ІаІНа¶ѓаІБа¶Ја¶ња¶§а•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ХаІЛථ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ යගථаІНබаІБ-а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථ ඁගපаІНа¶∞а¶ња¶§а•§ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶УආаІЗ, а¶ХаІЛථа¶У а¶ХаІЛථа¶У а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗ а¶ЙථаІНථаІЯථаІЗ а¶Ъа¶∞а¶Ѓ а¶ђаІИа¶Ја¶ЃаІНа¶ѓаІЗа¶∞ පගа¶Ха¶Ња¶∞ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶З ‘а¶ЙථаІНථаІЯථ’ ථගаІЯаІЗ ටа¶∞аІНа¶Х-ඐගටа¶∞аІНа¶Х-඙аІНа¶∞ටа¶∞аІНа¶Х а¶Ъа¶≤ටаІЗа¶З ඕඌа¶ХаІЗа•§ පаІБа¶ІаІБ а¶ЕථаІБථаІНථаІЯථаІЗа¶∞ ටа¶∞а¶Ьа¶Ња¶З ථаІЯ, а¶Па¶З ඙аІНа¶∞ඌථаІНටගа¶Х а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Х а¶Ьа¶Ѓа¶њ බа¶Ца¶≤аІЗа¶∞ а¶≤аІЬа¶Ња¶ЗаІЯаІЗ ථаІЗа¶ЃаІЗ ඙аІЬаІЗ а¶Єа¶ђ බа¶≤а•§ පаІБа¶ІаІБ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Њ а¶ЄаІНටа¶∞аІЗа¶З ථаІЯ, а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ බа¶≤аІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ а¶ЄаІНටа¶∞аІЗа¶∞ ථаІЗටඌ-ථаІЗටаІНа¶∞аІАа¶∞а¶Њ ඪබаІНа¶ѓ а¶≠а¶Ња¶∞ටа¶≠аІБа¶ХаІНට а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ЧаІБа¶≤ගටаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶Єа¶Ва¶Чආථ а¶ЧаІЬаІЗ ටаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ а¶ЬаІЛа¶∞ බаІЗа¶®а•§ а¶Пබගа¶ХаІЗ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ а¶У а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗа¶∞ ඙а¶∞аІНඃඌ඙аІНට а¶Еа¶∞аІНඕ а¶ђа¶∞ඌබаІНබ ථගаІЯаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶єаІЯ а¶Яඌථඌ඙аІЬаІЗа¶®а•§ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌа¶Ша¶Ња¶Я, ඙ඌථаІАаІЯ а¶Ьа¶≤аІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌ, а¶Еа¶ЩаІНа¶Чථа¶УаІЯа¶Ња¶∞а¶њ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞, ඙аІНа¶∞ඌඕඁගа¶Х а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤, а¶Ха¶Ѓа¶ња¶Йථගа¶Яа¶њ а¶єа¶≤ ඙аІНа¶∞а¶≠аІГටගа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь බаІНа¶∞аІБට а¶ЧටගටаІЗ а¶Єа¶ЃаІН඙ථаІНථ а¶єа¶≤аІЗа¶У а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶≤аІЛа¶Ъථඌ ඙ගа¶ЫаІБ а¶Ыа¶ЊаІЬаІЗ а¶®а¶ња•§ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ђа¶Ња¶ЄаІАබаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Ња¶ВපаІЗа¶∞ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶Ыа¶ња¶≤, ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ЙථаІНථаІЯථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ђа¶∞ඌබаІНබ а¶Еа¶∞аІНඕ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ЦඌටаІЗ а¶ђаІНа¶ѓаІЯ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ а¶ХаІБа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ ‘а¶Єа¶Ња¶ђ а¶°а¶ња¶≠ගපථඌа¶≤ යඪ඙ගа¶Яа¶Ња¶≤аІЗ’а¶∞ а¶ЙථаІНථаІЯථ, аІ™аІ®аІ™ а¶ХаІЛа¶Яа¶њ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЃаІЗа¶Ца¶≤а¶ња¶Ча¶ЮаІНа¶Ь-а¶єа¶≤බගඐඌаІЬа¶ња¶∞ а¶Єа¶Ва¶ѓаІЛа¶Ча¶Ха¶Ња¶∞аІА а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶Ь ථගа¶∞аІНа¶Ѓа¶Ња¶£ ඙аІНа¶∞а¶≠аІГටග а¶ЙථаІНථаІЯථඁаІВа¶≤а¶Х а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Х а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ђа¶Ња¶ЄаІАබаІЗа¶∞ ඪථаІНටаІБа¶ЈаІНа¶Я а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа¶®а¶ња•§
а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Х а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ХඌආඌඁаІЛ а¶ЙථаІНථаІЯථаІЗ ඐග඙аІБа¶≤ а¶Еа¶∞аІНඕаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьථ ටඌ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ а¶У а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ а¶Йа¶≠аІЯаІЗа¶З а¶Па¶Ха¶ђа¶Ња¶ХаІНа¶ѓаІЗ а¶ЃаІЗථаІЗ ථගа¶≤аІЗа¶У, а¶Па¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ථගයගට а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђа¶єаІБ а¶Ьа¶Яа¶ња¶≤а¶§а¶Ња•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ а¶ѓаІЗ а¶Еа¶∞аІНඕ а¶Ѓа¶ЮаІНа¶ЬаІБа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗ ටඌа¶∞ а¶Єа¶ња¶Ва¶єа¶≠а¶Ња¶Ч а¶ђа¶∞ඌබаІНබ а¶єаІЯ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶Єа¶Њ ඐඌඪගථаІНබඌබаІЗа¶∞ ඙аІБථа¶∞аІНඐඌඪථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗа•§ а¶Єа¶Вඐඌබ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Хඌප а¶єаІЯ а¶ѓаІЗ аІ©аІ¶аІ¶аІ¶ а¶ХаІЛа¶Яа¶њ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ аІ®аІ™аІ®аІЂ а¶ХаІЛа¶Яа¶њ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Ња¶З а¶ђа¶∞ඌබаІНබ а¶єа¶ђаІЗ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ ඙аІБථа¶∞аІНඐඌඪථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗа•§ а¶Ђа¶≤аІЗ а¶Єа¶Ва¶ѓаІБа¶ХаІНට а¶єа¶УаІЯа¶Њ аІЂаІІ а¶Яа¶њ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ аІІаІђ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Еа¶Єа¶єа¶ЊаІЯ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ЙථаІНථаІЯථаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗප ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶Єа¶Њ ඁඌටаІНа¶∞ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Єа¶ња¶Ва¶єа¶≠а¶Ња¶Ч а¶Еа¶∞аІНඕඐа¶∞ඌබаІНබаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶Яа¶њ а¶ХаІНа¶ЈаІЛа¶≠аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Пබගа¶ХаІЗ ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ ඙а¶∞ බаІАа¶∞аІНа¶Ш а¶Єа¶ЃаІЯ а¶ХаІЗа¶ЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗа¶У,а¶Еа¶∞аІНඕ а¶ђа¶∞ඌබаІНබ ථගаІЯаІЗа¶У а¶Йа¶≠аІЯ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ටа¶∞а¶Ьа¶Њ а¶Ъа¶≤ටаІЗа¶З ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶Зටගඁ඲аІНа¶ѓаІЗ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶ЙආаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗ а¶ѓаІЗ, а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ а¶ђа¶∞ඌබаІНබ а¶Еа¶∞аІНඕ а¶ЕථаІБа¶ЃаІЛබථ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а¶ња•§ аІ®аІ¶аІІаІЂ-аІІаІђ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ аІІаІ¶аІ¶аІЂ.аІѓаІѓ а¶ХаІЛа¶Яа¶њ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЕථаІБа¶ЃаІЛබථ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶У аІ®аІ¶аІІаІЃ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ЂаІЗа¶ђаІНа¶∞аІБаІЯа¶Ња¶∞а¶њ а¶Ѓа¶Ња¶Є ඙а¶∞аІНඃථаІНට аІ™аІ®аІ© а¶ХаІЛа¶Яа¶њ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ а¶ђа¶∞ඌබаІНබ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО а¶Еа¶∞аІНа¶ІаІЗа¶ХаІЗа¶∞а¶У а¶ђаІЗපаІА аІЂаІЃаІ®.аІѓаІѓ а¶ХаІЛа¶Яа¶њ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤ а¶ЙථаІНථаІЯථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ යඌටаІЗ ඙ඌаІЯථග а¶ђа¶≤аІЗ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ පаІЛථඌ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Еа¶∞аІНඕаІЗа¶∞ а¶Е඙аІНа¶∞ටаІБа¶≤ටඌаІЯ а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Х а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗа¶∞ а¶ЙථаІНථаІЯථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶ІаІАа¶∞ а¶Чටග а¶Єа¶ЃаІН඙ථаІНථ а¶єа¶≤аІЗ а¶ХаІНа¶ЈаІЛа¶≠ ඙аІБа¶ЮаІНа¶ЬаІАа¶≠аІВට යටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђаІЗ а¶Па¶З а¶ЄаІНඕඌථа¶ЧаІБа¶≤ගටаІЗ а¶ХаІЛථа¶∞аІВ඙ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶У а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІНඕаІНа¶ѓ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ ථඌ ඕඌа¶Ха¶ЊаІЯ а¶ЄаІНඕඌථаІАаІЯ ඐඌඪගථаІНබඌබаІЗа¶∞ බපа¶ХаІЗа¶∞ ඙а¶∞ බපа¶Х а¶Іа¶∞аІЗ а¶Хආගථ а¶Єа¶Ва¶Ха¶ЯаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ බගථ а¶ЧаІБа¶Ьа¶∞ඌථ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Па¶Хඕඌ а¶ђа¶ња¶ђаІЗа¶Ъථඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶З а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Х а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ЧаІБа¶≤ගටаІЗ ඙аІНа¶∞ඌඕඁගа¶Х а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤, а¶Еа¶ЩаІНа¶Чථа¶УаІЯа¶Ња¶∞а¶њ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞, ඙аІНа¶∞ඌඕඁගа¶Х а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІНඕаІНа¶ѓ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ а¶ЄаІНඕඌ඙ථаІЗ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶Ч ථаІЗаІЯа•§ ටඌ ථගаІЯаІЗа¶У а¶Ьа¶Яа¶ња¶≤ටඌ а¶Ха¶Ѓ а¶єаІЯ а¶®а¶ња•§ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Х а¶У а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІНඕаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІА ථගаІЯаІЛа¶ЧаІЗ а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Х а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ђа¶Ња¶ЄаІАබаІЗа¶∞ а¶Еа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ බගටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ а¶Пඁථ බඌඐаІАа¶У а¶УආаІЗа•§ а¶ХаІНа¶ЈаІЛа¶≠- а¶ђа¶ња¶ХаІНа¶ЈаІЛа¶≠аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶≤ටඌඁඌඁගа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶З а¶ђа¶ЄаІНටаІБа¶Чට а¶ЙථаІНථаІЯථаІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶Іа¶Ња¶∞а¶Њ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђаІЗа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶ЪගටаІНа¶∞а¶ХаІЗ а¶Жа¶Вපගа¶Х а¶єа¶≤аІЗа¶У ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථ а¶Ха¶∞аІЗа•§
а¶ЬаІАඐථ-а¶ЬаІАа¶ђа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ва¶Ха¶Я
аІІа¶≤а¶Њ а¶Жа¶Ча¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛа¶∞ а¶∞аІЛපථඌа¶З බаІНа¶∞аІБට ථගа¶≠аІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ ඪඌඁථаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Жа¶ЄаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ца¶∞ а¶ђа¶Ња¶ЄаІНа¶§а¶ђа•§ ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ а¶ђа¶єаІБ а¶Жа¶ЧаІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З, а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗ а¶ђа¶Єа¶ђа¶Ња¶Єа¶Ха¶Ња¶∞аІАබаІЗа¶∞ а¶ЬаІАඐථ а¶У а¶ЬаІАа¶ђа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට ඙ඕ а¶Еа¶ђа¶∞аІБබаІНа¶І а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Єа¶ња¶Ва¶єа¶≠а¶Ња¶Ч ඐඌඪගථаІНබඌ а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶∞ а¶У඙а¶∞ ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞පаІАа¶≤ а¶єа¶≤аІЗа¶У, а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶Хඌථඌ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Ъඌඣඌඐඌබ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶У, ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶Ђа¶Єа¶≤аІЗа¶∞ ථаІНа¶ѓа¶Ња¶ѓаІНа¶ѓ а¶ЃаІВа¶≤аІНа¶ѓ ඙аІЗටаІЗථ а¶®а¶Ња•§ а¶Ђа¶≤аІЗ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶ѓаІЗඁථ а¶≠ගථа¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶ѓа¶ЊаІЯаІА පаІНа¶∞а¶Ѓа¶ња¶ХаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ а¶ѓаІЛа¶Ч බаІЗаІЯ, ටаІЗඁථа¶З а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶Еа¶ђаІИа¶І а¶Й඙ඌа¶∞аІНа¶ЬථаІЗа¶∞ ඙ඕаІЗ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶ња¶≤ යටаІЗ а¶ђа¶Ња¶ІаІНа¶ѓ а¶єаІЯа•§ ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З ටඌа¶З ථටаІБථ а¶Єа¶Ва¶Ха¶ЯаІЗ ඙аІЬаІЗа¶®а•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђаІЗ а¶Еа¶ђаІИа¶І а¶Ха¶Ња¶∞а¶ђа¶Ња¶∞а¶ња¶∞а¶Њ а¶ђа¶∞аІНа¶°а¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ва¶≤а¶ЧаІНථ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶ХаІЗ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Іа¶∞аІЗ а¶ЪаІЛа¶∞а¶Ња¶Ъа¶Ња¶≤ඌථ а¶Єа¶є а¶Па¶Ха¶Ња¶Іа¶ња¶Х а¶Еа¶ђаІИа¶І а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Жа¶∞ а¶Па¶З а¶Еа¶ђаІИа¶І а¶Й඙ඌа¶∞аІНа¶ЬථаІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶ђа¶Ња¶ІаІНа¶ѓ а¶єаІЯаІЗа¶З ඙аІНа¶∞ඌථаІНට а¶≠аІВа¶Ца¶£аІНа¶°а¶ђа¶Ња¶ЄаІАබаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Ња¶Вප ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞පаІАа¶≤ а¶єаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа•§ а¶ђаІЗප а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗ а¶Ча¶Ња¶Ба¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Ъа¶Ња¶Ј а¶єа¶§а•§ а¶ѓаІЗа¶Цඌථ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඐග඙аІБа¶≤ а¶Еа¶∞аІНඕඌа¶Ча¶Ѓ а¶єа¶≤аІЗа¶У, а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ђа¶Ња¶ЄаІАබаІЗа¶∞ а¶Х඙ඌа¶≤аІЗ а¶ЬаІБа¶Яට ඪඌඁඌථаІНа¶ѓа¶За•§ а¶Пබගа¶ХаІЗ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ ඙аІБа¶≤ගප ඙аІНа¶∞පඌඪථ а¶ЄаІЗа¶Хඕඌ а¶Ьඌථа¶≤аІЗа¶У, ටඌа¶БබаІЗа¶∞ යඌට а¶ЧаІБа¶Яа¶њаІЯаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶ЧටаІНඃඌථаІНටа¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗපඌ඲ගа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ ටඐаІЗ ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶Уа¶З а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ЧаІБа¶≤ගටаІЗ ඙аІНа¶∞පඌඪථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ХаІНа¶∞а¶њаІЯටඌаІЯ а¶Ча¶Ња¶Ба¶Ьа¶Њ а¶Ъа¶Ња¶ЈаІЗа¶∞ а¶™а¶Ња¶£аІНධඌබаІЗа¶∞ а¶Ж඲ග඙ටаІНа¶ѓ а¶єаІНа¶∞а¶Ња¶Є ඙ඌаІЯа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ђа¶≤аІЗ а¶Па¶∞ а¶У඙а¶∞ ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞පаІАа¶≤ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞а¶Њ а¶Ха¶Ња¶∞аІНඃට а¶ЬаІАа¶ђа¶ња¶Ха¶Ња¶єаІАථ а¶єаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа¶®а•§
а¶Па¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶У ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ ඙а¶∞ ථටаІБථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶Єа¶Ва¶Ха¶Я බаІЗа¶Ца¶Њ බаІЗаІЯа•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶ВපаІЗа¶∞а¶З а¶≠аІЛа¶Ч බа¶Ца¶≤ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞аІНඃට а¶ХаІЛථа¶У а¶Ха¶Ња¶Ча¶Ь а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ ටඌа¶З ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ЄаІЗа¶З а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ХаІЛථ а¶ђаІИ඲ටඌа¶У а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Пබගа¶ХаІЗ ථටаІБථ ථගаІЯа¶Ѓ а¶ЕථаІБа¶ѓа¶ЊаІЯаІА а¶Ьථඐඪටග පаІВථаІНа¶ѓ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ а¶Ьа¶Ѓа¶њ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞аІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶єа¶Ња¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶®а•§ а¶ѓаІЗඁථ а¶ЃаІЗа¶Ца¶≤аІАа¶Ча¶ЮаІНа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ьа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶≤බය а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ ඙а¶ЮаІНа¶Ъа¶ЊаІЯаІЗටаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНටа¶∞аІНа¶Чට аІІаІѓаІ© ථа¶В а¶∞ටථ඙аІБа¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ ඪටаІНටа¶∞аІЛа¶∞аІНа¶І බаІЗа¶ђаІЗපаІНа¶ђа¶∞ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶£ а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Х а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗ аІ© а¶ђа¶ња¶Ша¶Њ а¶ЬඁගටаІЗ а¶Ъඌඣඌඐඌබ а¶Ха¶∞аІЗа¶З а¶Єа¶Ва¶Єа¶Ња¶∞ а¶Ъа¶Ња¶≤ඌටаІЗа¶®а•§ ටගථග а¶ЬඌථටаІЗථа¶У ථඌ а¶ѓаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Уа¶З а¶Ьа¶Ѓа¶њ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ХගථаІНටаІБ ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶Уа¶З а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗа¶∞ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶ЊаІЯаІЗа¶Ѓ а¶єа¶≤аІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЄаІЗа¶З а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ца¶∞аІНа¶ђ а¶єаІЯа•§ ටගථග а¶Уа¶З а¶ЬඁගටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶ЈаІЗа¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶єа¶Ња¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶Ха¶Ња¶∞аІНඃට а¶ЬаІАа¶ђа¶ња¶Ха¶Ња¶єаІАථ а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶®а•§
а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ђа¶Ња¶ЄаІАබаІЗа¶∞ а¶ЬаІАඐථ а¶У а¶ЬаІАа¶ђа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНඕඌථ а¶Ха¶∞а¶Њ ඙аІНа¶∞පඌඪථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Па¶Х а¶ђаІЬ ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Ња•§ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђаІЗа¶∞ ටаІБа¶≤ථඌаІЯ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞ඌථаІНටගа¶Х а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ЧаІБа¶≤ගටаІЗ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶І а¶Ха¶Ѓа¶≤аІЗа¶У, ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Й඙ඌа¶∞аІНа¶ЬථаІЗа¶∞ ඙ඕ а¶ЄаІЗа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЙථаІНа¶ЃаІБа¶ХаІНට а¶єаІЯа¶®а¶ња•§ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Ъа¶ња¶∞а¶Ња¶Ъа¶∞ගට а¶ЬаІАඐථ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Ха¶єаІАථ ටඕඌа¶Хඕගට а¶ЙථаІНථаІЯථаІЗа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞а¶ЊаІЯ а¶ХаІНа¶ЈаІЛа¶≠аІЗа¶∞ а¶ђа¶єа¶ња¶Г඙аІНа¶∞а¶Хඌප а¶Ша¶Яа¶Њ ටඌа¶З а¶Еа¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ња¶Х а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶ПඁථගටаІЗа¶З ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ ඙а¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶ђаІИа¶І ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶ХටаІНа¶ђаІЗа¶∞ ඙ටаІНа¶∞, аІІаІ¶аІ¶ බගථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь, ඪ඙аІНටඌයаІЗ аІ≠ а¶≤а¶ња¶Яа¶Ња¶∞ а¶ХаІЗа¶∞аІЛඪගථ ටаІЗа¶≤ а¶У а¶∞аІЗපථ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ බඌඐаІА а¶ЬඌථඌටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ ඙аІНа¶∞පඌඪථаІЗа¶∞ ටа¶∞а¶ЂаІЗ ‘а¶Ьа¶ђ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶°’ ඙аІНа¶∞බඌථаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙ а¶ЦаІЛа¶≤а¶Њ а¶єаІЯа•§ аІЂаІІа¶Яа¶њ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗа¶∞ аІІаІЂ,аІЃаІЂаІђ а¶Ьථа¶ХаІЗ а¶ђаІИа¶І ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶ХටаІНа¶ђаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ѓа¶Ња¶£ බаІНа¶∞аІБට යඌටаІЗ ටаІБа¶≤аІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶У а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЩаІНа¶Х а¶Жа¶Ха¶Ња¶Йа¶£аІНа¶Я а¶ЦаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶Ч බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶єаІЯа•§ ටඐаІЗ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ ‘а¶Ьа¶ђ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶°аІЗ’а¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ ‘а¶Жа¶Іа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶°’ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ බඌඐаІА ටаІЛа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Жа¶Іа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶° ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶ХටаІНа¶ђаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНඃටඁ ඙аІНа¶∞඲ඌථ ඙аІНа¶∞а¶Ѓа¶Ња¶£а¶™а¶§аІНа¶∞ а¶єа¶УаІЯа¶ЊаІЯ а¶≠ගථබаІЗපаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶Єа¶є а¶ЕථаІНඃඌථаІНа¶ѓ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶З ටඌ а¶Еа¶Іа¶ња¶Х а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ‘а¶Ьа¶ђа¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶°аІЗ’а¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ ‘а¶Жа¶Іа¶Ња¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶°’ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ බඌඐаІА බගථයඌа¶Яа¶Њ а¶Ѓа¶єа¶ХаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙аІЛаІЯඌටаІБа¶∞а¶ХаІБආග, ඁපඌа¶≤а¶°а¶Ња¶ЩаІНа¶Ча¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶Йආа¶≤аІЗа¶У, ටඌ а¶ХаІНа¶∞а¶ЃаІЗ а¶ЕථаІНඃඌථаІНа¶ѓ а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Х а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗа¶У බඌඐඌථа¶≤аІЗа¶∞ ඁට а¶ЫаІЬа¶њаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа•§ а¶Па¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ ථаІЗටаІГටаІНа¶ђ බගටаІЗ а¶Па¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗ ‘ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶Х а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Њ ඪඁථаІНа¶ђаІЯ ඪඁගටග’а•§ аІ©аІІ а¶Жа¶Ча¶ЄаІНа¶Я ටඌа¶∞а¶ња¶ЦаІЗ а¶Ца¶≤а¶ња¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶∞а¶ња¶∞ а¶Ђа¶≤ථඌ඙аІБа¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞පඌඪථаІЗа¶∞ ටа¶∞а¶ЂаІЗ ‘а¶Ьа¶ђа¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶°’ ඐගටа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙ а¶ЦаІЛа¶≤а¶Њ а¶єа¶≤аІЗа¶У, ‘а¶Ыа¶ња¶Я а¶ЄаІБа¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Њ ඪඁගටග’а¶∞ ථаІЗටаІГටаІНа¶ђаІЗ а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Х а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ђа¶Ња¶ЄаІАа¶∞а¶Њ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Еа¶≠а¶Ња¶ђ-а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч ටаІБа¶≤аІЗ ‘а¶Ьа¶ђа¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶°’ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£а¶ђаІЯа¶Ха¶Я а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶ђа¶∞а¶В ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶ђаІИа¶І а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ථඕගа¶∞ බඌඐаІА ටаІЛа¶≤аІЗа¶®а•§
а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤ ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ ඙а¶ЮаІНа¶Ъа¶ЊаІЯаІЗටаІЗа¶∞ а¶Жа¶УටඌаІЯ а¶Па¶≤аІЗ а¶ЄаІНඕඌථаІАаІЯ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤ඌබаІЗа¶∞ а¶ЬаІАа¶ђа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ ඙ඕ а¶ЄаІБа¶Ча¶Ѓ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Па¶ђа¶В ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ХаІНඣඁටඌаІЯථаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶Яа¶ња¶У а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНа¶ђ ඙аІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ ඙а¶∞а¶ња¶Ха¶≤аІН඙ථඌ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶У, а¶ЄаІНඕඌථаІАаІЯ а¶ЄаІНටа¶∞аІЗ ටඌ ඪආගа¶Ха¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ѓа¶Ха¶∞аІА а¶ѓаІЗ а¶єаІЯථග, ටඌ ථගаІЯаІЗ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶УආаІЗ а¶Па¶Ха¶Ња¶Іа¶ња¶Ха¶ђа¶Ња¶∞а•§ а¶ѓаІЗඁථ ඐඌටаІНа¶∞а¶ња¶Ча¶Ња¶Ы а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ а¶ѓаІЗ ඙ඌа¶Ба¶Ъа¶Яа¶њ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤ඌබаІЗа¶∞ а¶ЄаІНඐථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞ а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА а¶ЧаІЬаІЗ ටаІЛа¶≤а¶Њ а¶єа¶≤аІЗа¶У, а¶ЄаІЗа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶Жа¶∞аІНඕගа¶Ха¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶≤а¶Ња¶≠ඐඌථ а¶Ха¶∞аІЗ ටаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ а¶ХаІЛථа¶У а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶Ч ථаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶єаІЯථග а¶ђа¶≤аІЗ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶УආаІЗа•§
а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞
а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤ ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ХаІНа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З බаІЛа¶≤а¶Ња¶Ъа¶≤аІЗ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Па¶∞ а¶ЃаІВа¶≤ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Ьа¶Ѓа¶ња•§ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶∞а¶З а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ ඙а¶∞ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Ьа¶Ѓа¶њ а¶єа¶Ња¶∞ඌටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටаІЗ а¶ѓаІЛа¶Ча¶Ња¶ѓаІЛа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ђа¶∞аІНа¶°а¶Ња¶∞аІЗ а¶Ха¶∞а¶ња¶°аІЛа¶∞ а¶ЄаІНඕඌ඙ථаІЗа¶∞ බඌඐаІА ටаІЛа¶≤аІЗа•§ а¶Па¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶У а¶Ьа¶Ѓа¶њ а¶Ѓа¶Ња¶Ђа¶њаІЯඌබаІЗа¶∞ යඌට ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶ХаІЗ а¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗа¶У ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶ЄаІЛа¶ЪаІНа¶Ъа¶Ња¶∞ а¶єа¶®а•§ а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶Хඌථඌа¶∞ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶Яа¶ња¶З а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ђа¶Ња¶ЄаІАබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶У ඙аІНа¶∞඲ඌථ а¶ЪගථаІНටඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗа•§ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗපаІЗа¶∞ аІЂаІІа¶Яа¶њ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶Хඌථඌ ථගаІЯаІЗ а¶Ьа¶Яа¶ња¶≤ටඌа¶У а¶Ха¶Ѓ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶Вප а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ђа¶Ња¶ЄаІА а¶Ьа¶Ѓа¶њ а¶≠аІЛа¶Ч බа¶Ца¶≤ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶У, а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГට а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶Хඌථඌ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЃаІБа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶ЃаІЗаІЯ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ යඌටаІЗа•§ а¶ѓа¶Ња¶БබаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞а¶Ња¶Я а¶Еа¶Вප а¶Зටග඙аІВа¶∞аІНа¶ђаІЗа¶З а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ а¶≠аІВа¶Ца¶£аІНа¶°аІЗ а¶Ьа¶Ѓа¶њ-а¶Ьа¶Ѓа¶Њ а¶ХගථаІЗ а¶ђа¶Єа¶ђа¶Ња¶Є පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗථ а¶У а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶ХටаІНа¶ђ а¶≤а¶Ња¶≠ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶Па¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ а¶Жа¶ЃаІВа¶≤ а¶≠аІВа¶Ѓа¶ња¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶∞ ථඌ а¶єа¶УаІЯа¶ЊаІЯ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶Вප а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶ХаІГа¶Ја¶ХаІЗа¶∞ යඌටаІЗ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶ХаІЛථа¶У ඙ඌа¶ЯаІНа¶Яа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶ђа¶єаІБ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗ а¶ЄаІНа¶ђа¶≤аІН඙ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶∞ යඌටаІЗ ඐග඙аІБа¶≤ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶Хඌථඌ а¶ђа¶єаІБ а¶Жа¶ЧаІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Пඁථ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶ХаІЗа¶∞ ඪථаІН඲ඌථ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ а¶ѓа¶Ња¶Ба¶∞а¶Њ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗ පටඌ඲ගа¶Х а¶ђа¶ња¶Ша¶Њ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶Х а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ЧаІБа¶≤ගටаІЗ а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Х а¶ЬаІЛටබඌа¶∞а¶њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌа¶∞ а¶Йа¶ЪаІНа¶ЫаІЗබ ථඌ а¶єа¶УаІЯඌටаІЗа¶З ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ ඙а¶∞ ථටаІБථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ьа¶Ѓа¶њ а¶Єа¶Ва¶Ха¶Я а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶єаІЯа•§ ඐගපаІЗඣට а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Х а¶ЬаІЛටබඌа¶∞බаІЗа¶∞ යඌටаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ ඐග඙аІБа¶≤ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ ඐථаІНබаІЛа¶ђа¶ЄаІНටа¶У а¶Ьа¶∞аІБа¶∞аІА а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗа•§ а¶ЕථаІНඃබගа¶ХаІЗ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ХඌථඌයаІАථ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶Вප а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ђа¶Ња¶ЄаІАа¶∞а¶Ња¶У а¶Ъа¶∞а¶Ѓ а¶Жපа¶ЩаІНа¶Ха¶ЊаІЯ බගථ а¶ЧаІБа¶Ьа¶∞ඌථ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа¶®а•§ ඁඌඕඌа¶≠а¶Ња¶ЩаІНа¶Ча¶Њ а¶Ѓа¶єа¶ХаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЕථаІНටа¶∞аІНа¶Чට ‘ථа¶≤а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ-а¶Ђа¶≤ථඌ඙аІБа¶∞-а¶ЬаІЛа¶ВаІЬа¶Њ а¶Ыа¶ња¶Я ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶Х а¶ЄаІБа¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶Ха¶Ѓа¶ња¶Яа¶њ’ а¶Еа¶ђа¶ња¶≤а¶ЃаІНа¶ђаІЗ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶≠аІВа¶Єа¶ЃаІН඙ටаІНටගа¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Е඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටගට а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶Хඌථඌ а¶ШаІЛа¶Ја¶£а¶Ња¶∞ බඌඐаІА ටаІЛа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Па¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶У ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІНඁටග а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶З а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Х а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Ња¶ХаІЗ ඙ඌа¶∞аІНපаІНа¶ђа¶ђа¶∞аІНටаІА а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Па¶Х а¶Ха¶∞аІЗ ථටаІБථ а¶ЃаІМа¶Ьа¶Њ ඙аІБථа¶∞аІНа¶Чආගට а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Па¶∞ а¶Ђа¶≤аІЗ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶Хඌථඌ ඙аІНа¶∞ඌ඙аІНටගа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ ඐග඙аІБа¶≤ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ ඙аІЬටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ а¶ђа¶≤аІЗа¶У а¶Ьа¶Ња¶®а¶Ња¶®а•§ а¶Уа¶З а¶Єа¶Ва¶ЧආථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙ඌබа¶Х ඐගථаІНබаІЗපаІНа¶ђа¶∞ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶£ а¶Па¶∞ ඙аІНа¶∞ටගа¶Ха¶Ња¶∞ ථඌ а¶єа¶≤аІЗ а¶ђаІГයටаІНටа¶∞ а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථаІЗа¶∞ а¶єаІБа¶Ѓа¶Ха¶њ බаІЗа¶®а•§ а¶ѓаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ аІІаІђ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ ඐඌඪගථаІНබඌ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗа¶∞ ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶ХටаІНа¶ђ ඙ඌථ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞ඌ඙аІНටගа¶∞ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶Яа¶њ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа¶У а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЪගථаІНටඌа¶∞а•§
а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ЪаІЬа¶Ња¶З а¶ЙаІОа¶∞а¶Ња¶ЗаІЯаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶Ьа¶Ѓа¶њ а¶Єа¶Ва¶ХаІНа¶∞ඌථаІНට а¶ХаІНа¶ЈаІЛа¶≠аІЗа¶∞ а¶ЄаІНඕඌаІЯаІА ථගа¶∞ඪථ а¶єаІЯа•§ аІ®аІ¶аІІаІѓ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ аІ© а¶ЬඌථаІБаІЯа¶Ња¶∞а¶њ ටඌа¶∞а¶ња¶ЦаІЗ ඙аІНа¶∞පඌඪථаІЗа¶∞ ටа¶∞а¶ЂаІЗ а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Х аІЂаІІ а¶Яа¶њ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗа¶∞ аІІаІ©,аІЂаІђаІ¶ а¶Ьථ ඐඌඪගථаІНබඌබаІЗа¶∞ යඌටаІЗ а¶ЃаІЛа¶Я аІ≠аІІаІІаІ¶ а¶Па¶Ха¶∞ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶Ца¶ЄаІЬа¶Њ а¶ЦටගаІЯඌථ ටаІБа¶≤аІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶Уа¶З බගථаІЗ ඙аІНа¶∞ඕඁаІЗ ටаІБ඀ඌථа¶Ча¶ЮаІНа¶ЬаІЗ; ටඌа¶∞඙а¶∞ බගථයඌа¶Яа¶Ња¶∞ පඌа¶≤а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶Њ, ථаІЯа¶Ња¶∞а¶єа¶Ња¶Я а¶У ඐඌටаІНа¶∞а¶ња¶Ча¶Ња¶ЫаІЗ; а¶ЃаІЗа¶Ца¶≤аІАа¶Ча¶ЮаІНа¶Ь, පаІАටа¶≤а¶ХаІБа¶Ъа¶њ ඙аІНа¶∞а¶≠аІГටග а¶ЄаІНඕඌථаІЗ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Уа¶З а¶ЦටගаІЯඌථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ча¶Ь ටаІБа¶≤аІЗ බаІЗථ а¶Ьථ඙аІНа¶∞ටගථග඲ග а¶У ඙аІНа¶∞පඌඪථаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞аІНටඌඐаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶∞а¶Ња•§ а¶Па¶∞ а¶Ђа¶≤аІЗ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶ХаІНа¶∞аІЯа¶ђа¶ња¶ХаІНа¶∞аІЯ, а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶њ а¶Жа¶ђа¶Ња¶Є а¶ѓаІЛа¶Ьථඌ, а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЩаІНа¶Х а¶≤аІЛථ ඙аІНа¶∞а¶≠аІГටග ඙аІНа¶∞ඌ඙аІНටගа¶∞ а¶ѓаІЗ а¶ђа¶Ња¶Іа¶Њ а¶Пටබගථ а¶Ыа¶ња¶≤, ටඌ බаІВа¶∞ а¶єаІЯа•§ ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Х а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ђа¶Ња¶ЄаІАබаІЗа¶∞ යඌටаІЗ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ча¶Ь ටаІБа¶≤аІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ ථගа¶ГඪථаІНබаІЗа¶єаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ђаІИ඙аІНа¶≤а¶ђа¶ња¶Х ඙බа¶ХаІНа¶ЈаІЗ඙ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Ђа¶≤аІЗ а¶ЄаІНа¶ђа¶≤аІН඙ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ යඌටаІЗ а¶ХаІБа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶Чට а¶єаІЯаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶Вප а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶ђа¶£аІНа¶Яථ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶Єа¶ЃаІН඙ථаІНථ а¶єаІЯа•§ а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶Па¶З а¶ЦටගаІЯඌථ ඙аІНа¶∞බඌථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ђа¶Ња¶ЄаІАබаІЗа¶∞ а¶Па¶Х බаІАа¶∞аІНа¶Ш а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ ඪඁඌ඲ඌථ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ බаІНа¶∞аІБට а¶ЧටගටаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶ЫථаІНබ඙ටථ а¶Ша¶ЯаІЗа•§ аІ© а¶ЬඌථаІБаІЯа¶Ња¶∞а¶њ ටඌа¶∞а¶ња¶ЦаІЗ а¶Ца¶ЄаІЬа¶Њ а¶ЦටගаІЯඌථ ටаІБа¶≤аІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶єа¶≤аІЗа¶У, ටඌ а¶≠аІБа¶≤аІЗ а¶≠а¶∞а¶Њ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Х а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ђа¶Ња¶ЄаІАබаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Ња¶Вප а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ථඌඁаІЗа¶∞ а¶≠аІБа¶≤ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶У а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ බඌа¶Ч ථඁаІНа¶ђа¶∞ а¶У ඙а¶∞а¶ња¶Ѓа¶Ња¶£ ථගаІЯаІЗа¶У а¶ђа¶ња¶≠аІНа¶∞ඌථаІНටග ටаІИа¶∞а¶њ а¶єаІЯа•§ аІЂ а¶ЬඌථаІБаІЯа¶Ња¶∞а¶њ ටඌа¶∞а¶ња¶ЦаІЗ ථа¶≤а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ, а¶Ђа¶≤ථඌ඙аІБа¶∞, а¶ЬаІЛа¶Ва¶∞а¶Ња¶∞ ඐඌඪගථаІНබඌа¶∞а¶Њ ‘ථа¶≤а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶Хථа¶Х а¶Жබа¶∞аІНප ඙аІНа¶∞ඌඕඁගа¶Х ඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗ’ а¶Па¶Х ඙аІНа¶∞ටගඐඌබ а¶Єа¶≠а¶Ња¶∞ а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Па¶З а¶Єа¶≠а¶ЊаІЯ а¶∞аІЗа¶ЬаІЯඌථ а¶Ха¶∞а¶ња¶Ѓ, а¶ЧаІМටඁ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶£ ඙аІНа¶∞а¶ЃаІБа¶ЦබаІЗа¶∞ ථаІЗටаІГටаІНа¶ђаІЗ ‘а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Х а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤ а¶≠аІВа¶Ѓа¶њ а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථ а¶Ха¶Ѓа¶ња¶Яа¶њ’ а¶Чආගට а¶єаІЯа•§ а¶Єа¶Ва¶Чආථа¶Яа¶њ ථටаІБථ а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Ьа¶Ѓа¶њ а¶Ьа¶∞ග඙ а¶Ха¶∞аІЗ ථගа¶∞аІНа¶≠аІБа¶≤ а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶ЦටගаІЯඌථ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ බඌඐаІА а¶ЬඌථඌаІЯа•§ ඃබගа¶У ඁඌඕඌа¶≠а¶Ња¶ЩаІНа¶Ча¶Њ а¶Ѓа¶єа¶ХаІБа¶Ѓа¶Њ ඙аІНа¶∞පඌඪථаІЗа¶∞ ටа¶∞а¶ЂаІЗ а¶Па¶З а¶≠аІБа¶≤ а¶Єа¶ВපаІЛ඲ථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ аІѓ ථඁаІНа¶ђа¶∞ а¶Ђа¶∞аІНа¶Ѓ ඙аІВа¶∞а¶£ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ьа¶Ѓа¶Њ බගටаІЗ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО а¶ђа¶ња¶Чට а¶ђа¶Ыа¶∞а¶ЧаІБа¶≤ගටаІЗ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞පаІНථ ථගаІЯаІЗ а¶Па¶Ха¶Ња¶Іа¶ња¶Х а¶Ьа¶Яа¶ња¶≤ටඌ а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶єа¶≤аІЗа¶У, а¶ђа¶∞аІНටඁඌථаІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶ХаІНа¶ЈаІЛа¶≠аІЗа¶∞ ථගа¶∞ඪථ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§
а¶≠ගථа¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗ а¶Еа¶≠ග඙аІНа¶∞аІЯа¶Ња¶£
а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤ ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶ЄаІНඐ඙аІНථ බаІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ЬаІАඐථаІЗ а¶ЄаІБබගථ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶Жа¶Єа¶ђаІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ђа¶Ња¶ЄаІНටඐ а¶ЪගටаІНа¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶≠ගථаІНа¶®а•§ ටගථ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Еටගа¶ХаІНа¶∞ඌථаІНට а¶єа¶≤аІЗа¶У, а¶ЬаІАа¶ђа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶ХаІЛථ а¶ЄаІБа¶∞а¶Ња¶єа¶Њ а¶єаІЯ а¶®а¶ња•§ ථа¶≤а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ, а¶Ђа¶≤ථඌ඙аІБа¶∞аІЗа¶∞ ඁට ඁපඌа¶≤а¶°а¶Ња¶ЩаІНа¶Ча¶Њ, ඙аІЛаІЯඌටаІБа¶∞а¶ХаІБආග, ඐඌටаІНа¶∞а¶ња¶Ча¶Ња¶Ы ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶Єа¶ђ а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Х а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶єаІБ а¶ѓаІБа¶ђа¶Х а¶ЬаІАа¶ђа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ ඪථаІН඲ඌථаІЗ ඙ඌаІЬа¶њ බаІЗථ а¶≠ගථа¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа•§ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථ ඙аІНа¶∞඲ඌථ ඐඌටаІНа¶∞а¶ња¶Ча¶Ња¶Ы ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђаІНඃඌ඙а¶Х а¶єа¶Ња¶∞аІЗ а¶Еа¶≠ග඙аІНа¶∞аІЯа¶Ња¶£ а¶Ша¶ЯаІЗа•§ а¶Па¶З а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ බаІБа¶З а¶ђаІБඕ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶Жපග පටඌа¶Вප а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ а¶ѓаІБа¶ђа¶Х а¶ЃаІВа¶≤ට а¶ХаІЗа¶∞а¶≤, а¶єа¶∞а¶њаІЯඌථඌ, බගа¶≤аІНа¶≤аІА ඙аІНа¶∞а¶≠аІГටග а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗ ඙ඌаІЬа¶њ බගаІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗ බගа¶≤аІНа¶≤аІАа¶∞ а¶За¶Ба¶Яа¶≠а¶Ња¶Яа¶ЊаІЯ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶ѓа¶Ња¶®а•§ а¶≠ගථа¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗ ඙ඌаІЬа¶њ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞а¶Њ පаІБа¶ІаІБ а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Х а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ЧаІБа¶≤аІЛටаІЗа¶З а¶Ыа¶ња¶≤ ථඌ, а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙а¶ЧаІБа¶≤аІЛටаІЗа¶У а¶ђаІНඃඌ඙а¶Х а¶єа¶Ња¶∞аІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ѓаІЗඁථ බගථයඌа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Еа¶ЄаІНඕඌаІЯаІА පගඐගа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶У а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶Ша¶∞аІЗ ටඌа¶≤а¶Њ බගаІЯаІЗ ඙ඌаІЬа¶њ බගаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа•§ аІ®аІ¶аІІаІЃ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ ථа¶≠аІЗа¶ЃаІНа¶ђа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ පаІБа¶∞аІБටаІЗ බගа¶≤аІНа¶≤аІА, а¶ЬаІЯ඙аІБа¶∞, а¶ђаІЗа¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶≤аІБа¶∞аІБටаІЗ а¶Па¶З а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙ඌаІЬа¶њ බаІЗаІЯа•§ а¶Па¶З පගඐගа¶∞аІЗа¶∞ ඐඌඪගථаІНබඌ а¶єа¶∞аІЗа¶ХаІГа¶ЈаІНа¶£ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶£, а¶ХаІГа¶ЈаІНа¶£ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞аІА, а¶Ха¶Ња¶ЫаІБаІЯа¶Њ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶£ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶Ха¶∞аІЗථ а¶Па¶ЦඌථаІЗ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ЬаІАа¶ђа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶ХаІЛථа¶У а¶Й඙ඌаІЯ ථаІЗа¶За•§ а¶Ъа¶Ња¶∞- ඙ඌа¶Ба¶Ъ а¶Ьථ а¶ЯаІЛа¶ЯаІЛ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶Ња¶≤аІЗа¶У, а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶Вපа¶З බගථඁа¶ЬаІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ХගථаІНටаІБ බගථඁа¶ЬаІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь ඙а¶∞аІНඃඌ඙аІНට ථඌ ඕඌа¶Ха¶ЊаІЯ, а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶ѓаІЗඁථ ඪ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗ ඙ඌаІЬа¶њ බගаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ, а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞а¶ХаІЗ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙аІЗ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ а¶ЬаІАа¶ђа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ ඪථаІН඲ඌථаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Па¶З а¶Еа¶≠ග඙аІНа¶∞аІЯа¶Ња¶£ а¶ЃаІЛа¶ЯаІЗа¶У а¶ЄаІБа¶Ца¶Ха¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶≠ගථ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗ ථඌථඌ ඐග඙බаІЗ ඙аІЬටаІЗ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Па¶З а¶Еа¶Єа¶єа¶ЊаІЯ а¶ѓаІБа¶ђа¶ХබаІЗа¶∞а•§ ඙аІЛаІЯඌටаІБа¶∞а¶ХаІБආගа¶∞ а¶∞а¶Ђа¶ња¶ХаІБа¶≤ ථඌඁаІЗ а¶ЬථаІИа¶Х а¶Па¶Х а¶ѓаІБа¶ђа¶Х ඙а¶∞а¶ња¶Ъගටගа¶∞ ථඕග а¶Ьа¶Ѓа¶Њ බගටаІЗ ථඌ ඙ඌа¶∞а¶ЊаІЯ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ ථаІЯа¶°а¶ЊаІЯ а¶ЧаІНа¶∞аІЗ඙аІНටඌа¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ ටඌа¶Ба¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Жа¶∞а¶У а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗ а¶ЧаІНа¶∞аІЗ඙аІНටඌа¶∞ а¶єа¶≤аІЗа¶У, ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶Ьඌඁගථ ඙аІЗаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗа¶У а¶ЄаІЗ ඙ඌаІЯа¶®а¶ња•§ а¶∞а¶Ђа¶ња¶ХаІБа¶≤ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶∞ а¶ХаІЛථаІЛ а¶Ха¶Ња¶Ча¶Ь බаІЗа¶ЦඌටаІЗ ථඌ ඙ඌа¶∞а¶ЊаІЯ ටඌа¶Ба¶∞ ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶ХටаІНа¶ђ ථගаІЯаІЗа¶З ඙аІНа¶∞පаІНථ а¶УආаІЗа•§ а¶Па¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶≠ගථ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗ а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Х а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗа¶∞ а¶≠ගථа¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ පаІНа¶∞а¶Ѓа¶ња¶ХබаІЗа¶∞ බගථаІЗа¶∞ ඙а¶∞ බගථ а¶єаІЗථඪаІНටඌа¶∞ පගа¶Ха¶Ња¶∞ යටаІЗ а¶єаІЯа•§ а¶Па¶З පаІНа¶∞а¶Ѓа¶ња¶ХබаІЗа¶∞ බаІБа¶∞аІНබපඌа¶∞ а¶ХаІЛථа¶У а¶ЄаІБа¶∞а¶Ња¶єа¶Ња¶З а¶єаІЯථග а¶Па¶ђа¶В а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤ ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶У ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ЄаІБබගථ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶Жа¶ЄаІЗа¶®а¶ња•§
а¶Пථа¶ХаІНа¶≤аІЗа¶≠ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙
ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ХаІНа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ ඙аІНа¶∞පඌඪථ а¶ЕථаІБඁඌථ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗපаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНටа¶∞аІНа¶Чට аІІаІІаІІ а¶Яа¶њ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ха¶≤ ඐඌඪගථаІНබඌа¶∞а¶Њ а¶ПබаІЗපаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Жа¶Єа¶ђаІЗа¶®а•§ а¶Па¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ ඙аІНа¶∞පඌඪථ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ХаІБа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶ЄаІНඕඌථаІЗ а¶Па¶Ха¶Ња¶Іа¶ња¶Х ‘а¶Пථа¶ХаІНа¶≤аІЗа¶≠ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙’ а¶ЄаІНඕඌ඙ථаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶Ха¶≤аІН඙ථඌ ථගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ХගථаІНටаІБ аІђ а¶ЬаІБථ ටඌа¶∞а¶ња¶Ц ඕаІЗа¶ХаІЗ ඪ඙аІНටඌයа¶Ха¶Ња¶≤ а¶ђаІНඃඌ඙аІА ‘а¶Е඙පථ’ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£аІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙аІЗ ඁඌටаІНа¶∞ аІѓаІЃаІ¶ а¶Ьථ ථඌඁ ථඕගа¶≠аІБа¶ХаІНට а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Еටа¶Г඙а¶∞ ඙аІНа¶∞පඌඪථ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ ඁඌටаІНа¶∞ ටගථа¶Яа¶њ а¶ЄаІНඕඌථаІЗ а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО බගථයඌа¶Яа¶Њ, а¶ЃаІЗа¶Ца¶≤аІАа¶Ча¶ЮаІНа¶Ь а¶У а¶єа¶≤බගඐඌаІЬගටаІЗ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙ а¶ЄаІНඕඌ඙ථаІЗа¶∞ ඪගබаІН඲ඌථаІНට ථаІЗаІЯа•§ а¶ХගථаІНටаІБ ඙аІНа¶∞ඕඁ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З ථඌථඌ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Ьа¶∞аІНа¶Ьа¶∞ගට а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ђа¶Ња¶ЄаІАа¶∞а¶Ња•§ а¶ѓаІЗ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙аІЗ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶Па¶ЄаІЗ а¶ЙආඐаІЗථ ටඌ ථගаІЯаІЗ ථඌථඌ а¶ЧаІБа¶Ьа¶ђ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ХඌථаІЗ а¶ЖඪටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ ටඌа¶З аІ©аІѓ а¶ЬථаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ බа¶≤ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗප а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЯаІНа¶∞а¶Ња¶≠аІЗа¶≤ ඙ඌඪ ථගаІЯаІЗ а¶ЪаІНа¶ѓа¶Ња¶Ва¶∞ඌඐඌථаІНබඌ а¶ЄаІАඁඌථаІНට а¶ЪаІЗа¶Х඙аІЛа¶ЄаІНа¶Я බගаІЯаІЗ а¶ПබаІЗපаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙аІЗа¶∞ а¶єа¶Ња¶≤а¶єа¶Ха¶ња¶ХаІО а¶Єа¶∞аІЛа¶ЬඁගථаІЗ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶За¶≤аІЗ аІѓ а¶ЄаІЗ඙аІНа¶ЯаІЗа¶ЃаІНа¶ђа¶∞ ටඌа¶∞а¶ња¶ЦаІЗ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Жа¶Яа¶ХаІЗ බаІЗථ а¶ђаІБаІЬа¶ња¶Ѓа¶Ња¶∞а¶њ а¶ЪаІЗа¶Х඙аІЛа¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶∞ а¶Жа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞а¶ња¶Ха¶∞а¶Ња•§ ‘а¶ЯаІНа¶∞а¶Ња¶≠аІЗа¶≤ ඙ඌඪ’ ඐඌඐබ ඁඌඕඌ඙ගа¶ЫаІБ аІЂаІЂаІ¶ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ බගටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Ьа¶Ња¶®а¶Ња¶®а•§ а¶Па¶З ථගаІЯаІЗ а¶Єа¶Ња¶ЃаІЯа¶ња¶Х а¶ЕපඌථаІНටගа¶∞ а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶єа¶≤аІЗа¶У පаІЗа¶Ј ඙а¶∞аІНඃථаІНට ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶ЄаІАඁඌථаІНට ඙ඌа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ХаІБа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙а¶ЧаІБа¶≤а¶њ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ а¶Єа¶ХаІНа¶Ја¶Ѓ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Па¶З ඙а¶∞ගබа¶∞аІНපථа¶Ха¶Ња¶∞аІА බа¶≤ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶Ха¶∞аІЗථ а¶ѓаІЗ, а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗ а¶ЖඪටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶За¶≤аІЗа¶У а¶єаІБа¶Ѓа¶Ха¶ња¶∞ а¶≠аІЯаІЗ ථඌඁ ථඕගа¶≠аІБа¶ХаІНට а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ЫаІЗථ а¶®а¶Ња•§
а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤ ඐගථගඁаІЯ а¶Па¶Х බаІАа¶∞аІНа¶Ш а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ ඪඁඌ඲ඌථ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶У а¶ЕථаІЗа¶Х ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗ а¶≠а¶Ња¶Щථ а¶Іа¶∞аІЗа•§ а¶П’බаІЗපаІЗ а¶ЄаІНඕඌаІЯаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Жа¶Єа¶Њ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶З а¶≠аІЯа¶Ва¶Ха¶∞ බаІБа¶∞аІНа¶ѓаІЛа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ඙аІЬаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ ථа¶≠аІЗа¶ЃаІНа¶ђа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ аІ©аІ¶ ටඌа¶∞а¶ња¶ЦаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶П’බаІЗපаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Жа¶Єа¶Ња¶∞ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІА ථගа¶∞аІНබаІЗපථඌඁඌ а¶Ьа¶Ња¶∞а¶њ а¶єаІЯа•§ а¶Па¶З а¶ЄаІНа¶ђа¶≤аІН඙ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ХаІНа¶∞аІЗටඌа¶∞ а¶Еа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ, а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶Ьа¶Ѓа¶Њ а¶ђа¶ња¶ХаІНа¶∞а¶њ а¶Ха¶Ња¶∞аІНඃට а¶Еа¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ а¶єаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа•§ а¶ПබаІЗපаІЗ а¶Жа¶Єа¶Ња¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІЗ а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ ඁථඪаІНඕගа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඙аІНа¶∞ටගථග඲ග බа¶≤ аІІаІ™ а¶ЄаІЗ඙аІНа¶ЯаІЗа¶ЃаІНа¶ђа¶∞ ටඌа¶∞а¶ња¶ЦаІЗ а¶ХаІБа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗ а¶ЬаІЗа¶≤ඌපඌඪа¶ХаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ХаІГа¶ЈаІНа¶£а¶ХඌථаІНට а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶£, ඁථඁаІЛයථ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶£ ඙аІНа¶∞а¶ЃаІБа¶Ца¶∞а¶Њ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ ටаІБа¶≤аІЗ а¶Іа¶∞аІЗа¶®а•§ බඌපගаІЯа¶ЊаІЬа¶ЫаІЬа¶Њ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗа¶∞ а¶ЃаІЛපඌа¶∞аІЛа¶Ђ а¶єаІЛа¶ЄаІЗථ а¶Ьඌථඌථ, ටඌа¶Ба¶∞ аІІаІ¶ а¶ђа¶ња¶Ша¶Њ а¶Ьа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶ња¶ХаІНа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ЫаІЗථ а¶®а¶Ња•§ а¶ХаІНа¶∞аІЗටඌ ථаІЗа¶За•§ а¶Па¶З а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌаІЯ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶Ьа¶Ѓа¶Њ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ а¶ХаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ටඌа¶∞а¶Њ а¶ПබаІЗපаІЗ а¶Жа¶Єа¶ђаІЗ? а¶Пබගа¶ХаІЗ а¶ПබаІЗපаІЗ а¶Жа¶Єа¶Ња¶∞ බගථ а¶ШථගаІЯаІЗ а¶Па¶≤аІЗ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶Ьа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶ња¶ХаІНа¶∞а¶њ ථඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶З а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Жа¶ЄаІЗа¶®а•§ а¶Па¶ЄаІЗа¶У а¶ЄаІНа¶ђа¶ЄаІНටග ථаІЗа¶За•§ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙аІЗа¶∞ а¶ЫаІЛа¶Я а¶ЫаІЛа¶Я а¶ЯගථаІЗа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶Ша¶∞а¶ЧаІБа¶≤ගටаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗ а¶Чඌබඌа¶Чඌබග а¶Ха¶∞аІЗ ඕඌа¶Ха¶Ња¶Яа¶Њ а¶ХаІНа¶∞а¶ЃаІЗа¶З а¶ЕඪයථаІАаІЯ а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗа•§ ඐගබаІНа¶ѓаІБаІО ථඌ ඕඌа¶Ха¶ЊаІЯ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙ඐඌඪаІАබаІЗа¶∞ а¶ЧаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Ѓа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶≠аІЛа¶ЧඌථаІНටග а¶ѓаІЗඁථ а¶Ъа¶∞а¶ЃаІЗ а¶УආаІЗ, ටаІЗඁථа¶З ඙аІЬаІБаІЯඌබаІЗа¶∞ ඙ආථ-඙ඌආථаІЗа¶У а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Шඌට а¶Ша¶ЯаІЗа•§ ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ а¶Па¶Х а¶ђа¶Ыа¶∞ ඙а¶∞аІЗа¶У а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌ ටඕаІИа¶ђа¶Ъа•§
а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤ ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶ђа¶∞аІНඣ඙аІВа¶∞аІНටගටаІЗ බගථයඌа¶Яа¶Њ, а¶ЃаІЗа¶Ца¶≤аІАа¶Ча¶ЮаІНа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙аІЗ а¶ХаІНа¶ЈаІЛа¶≠аІЗа¶∞ ථගа¶∞ඪථ ථඌ а¶єа¶≤аІЗа¶У, а¶єа¶≤බගඐඌаІЬа¶њ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙аІЗ а¶Па¶З а¶Рටගයඌඪගа¶Х බගථа¶Яа¶њ а¶Йබඃඌ඙ගට а¶єаІЯ а¶Ѓа¶єа¶Ња¶Єа¶Ѓа¶Ња¶∞аІЛа¶єаІЗа¶За•§ аІ®аІ¶аІІаІ≠ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ ථа¶≠аІЗа¶ЃаІНа¶ђа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗ а¶Па¶З а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙а¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ බаІБа¶З а¶ђа¶Ыа¶∞ ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶єа¶≤аІЗа¶У, а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙ඐඌඪаІАබаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ЄаІБа¶∞а¶Ња¶єа¶Њ а¶єаІЯа¶®а¶ња•§ а¶Еඕа¶Ъ බаІБ’а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ ඙аІБථа¶∞аІНඐඌඪථаІЗа¶∞ а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓ а¶ЄаІНඕගа¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙а¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ а¶Еа¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌ ථගаІЯаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯපа¶З ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Єа¶∞а¶ђ යටаІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ЃаІЗа¶Ца¶≤аІАа¶Ча¶ЮаІНа¶ЬаІЗа¶∞ а¶≠аІЛа¶Яа¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙аІЗа¶∞ ඐඌඪගථаІНබඌබаІЗа¶∞ а¶ЄаІНඕඌаІЯаІА ඙аІБථа¶∞аІНඐඌඪථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ѓаІЗ а¶ЄаІНඕඌථаІЗ а¶ЂаІНа¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶Я а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ ථගа¶∞аІНඁගට а¶єа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤, ටඌ ථගаІЯаІЗа¶У ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ХаІНа¶ЈаІЛа¶≠аІЗа¶∞ а¶ЕථаІНට а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶ЪаІНа¶ѓа¶Ња¶Ва¶∞ඌඐඌථаІНබඌටаІЗ аІІаІЂаІ® ථа¶В ඙ඌථගපඌа¶≤а¶Ња¶∞ а¶™а¶Ња¶£аІНа¶°а¶ђ а¶ђа¶∞аІНа¶Ьගට а¶ЄаІНඕඌථаІЗ ථඐථගа¶∞аІНඁගට а¶ЂаІНа¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶Я ථගаІЯаІЗ а¶ЃаІЗа¶Ца¶≤аІАа¶Ча¶ЮаІНа¶Ь а¶Ѓа¶єа¶ХаІБа¶Ѓа¶Њ පඌඪа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Зටග඙аІВа¶∞аІНа¶ђаІЗ а¶Па¶Ха¶Ња¶Іа¶ња¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЕඪථаІНටаІЛа¶Ј а¶Ьඌථඌа¶≤аІЗа¶У а¶ХаІЛථа¶У а¶ЄаІБа¶∞а¶Ња¶єа¶Њ а¶єаІЯа¶®а¶ња•§ а¶ЕඐපаІЗа¶ЈаІЗ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶ЕථපථаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶Еථපථа¶Ха¶Ња¶∞аІАබаІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞ ථගа¶∞аІНа¶Ѓа¶Ѓ ඙аІБа¶≤ගපග ථගа¶ЧаІНа¶∞а¶єаІЗа¶∞ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶УආаІЗа•§ ඙ඌථගපඌа¶≤а¶ЊаІЯ а¶ЄаІНඕඌаІЯаІА а¶Жа¶ђа¶Ња¶Єа¶ЄаІНඕа¶≤ а¶ЧаІЬаІЗ ටаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь පаІБа¶∞аІБ а¶єа¶≤аІЗа¶У, а¶ЄаІЗа¶Цඌථа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ѓаІЛа¶Ча¶Ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌа¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНа¶ђ ථඌ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Хඕඌа¶У а¶ЬඌථගаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙ඐඌඪаІАа¶∞а¶Ња•§ ඙ඌථගපඌа¶≤а¶Њ а¶ЄаІНඕඌථа¶Яа¶њ а¶Пටа¶Яа¶Ња¶З а¶ЕථаІБථаІНථට а¶ѓаІЗ, а¶ѓаІЛа¶Ча¶Ња¶ѓаІЛа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ЄаІБа¶ђа¶ња¶Іа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ а¶Іа¶∞а¶≤а¶Њ ථබаІАа¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶ЬаІЗа¶∞ බඌඐаІА а¶Ьа¶Ња¶®а¶Ња¶®а•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Па¶З а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶Ь а¶єа¶≤аІЗ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ ඙ඌථගපඌа¶≤а¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Єа¶єа¶ЬаІЗа¶З а¶Ъа¶Ња¶Ва¶∞ඌඐඌථаІНබඌ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤, а¶Ха¶≤аІЗа¶Ь, යඌඪ඙ඌටඌа¶≤аІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗа¶®а•§ ථа¶За¶≤аІЗ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ђа¶єаІБ ඙ඕ а¶ШаІБа¶∞аІЗ а¶ЪаІНа¶ѓа¶Ња¶Ва¶∞ඌඐඌථаІНබඌаІЯ а¶ѓаІЗටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§
බаІБ’а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Еටගа¶ХаІНа¶∞ඌථаІНට а¶єа¶≤аІЗ а¶ЄаІНඕඌаІЯаІА ඙аІБථа¶∞аІНඐඌඪථаІЗа¶∞ а¶ХаІЛථа¶У а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඌඐථඌ ටаІЛ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа¶З ථග, а¶Й඙а¶∞ථаІНටаІБ බගථයඌа¶Яа¶Њ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙аІЗа¶∞ ඐඌඪගථаІНබඌа¶∞а¶Њ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶Ха¶∞аІЗථ а¶ѓаІЗ, ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶∞аІЗපථ ඙а¶∞аІНඃථаІНට ඐථаІНа¶І а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙ඐඌඪаІАа¶∞а¶Њ а¶Ьඌථඌථ, පаІБа¶ІаІБ а¶∞аІЗපථ ඐථаІНа¶Іа¶З ථаІЯ аІІаІ¶аІ¶ බගථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞аІЗа¶У ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ а¶™а¶Ња¶®а¶®а¶ња•§ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶Пඁථ ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶ЊаІЯаІЗ ඙аІМа¶Ба¶Ыа¶ЊаІЯ а¶ѓаІЗ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ පඌа¶Х඙ඌටඌ а¶≤ඐථ බගаІЯаІЗ а¶≠ඌට а¶ЬаІБа¶Яа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙ඐඌඪаІАබаІЗа¶∞ බаІБ’а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓа¶З а¶∞аІЗපථ а¶ђа¶∞ඌබаІНබ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ බаІБ’а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Еටගа¶ХаІНа¶∞ඌථаІНට а¶єа¶≤аІЗ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶њ ථගаІЯа¶Ѓ а¶ЕථаІБа¶ѓа¶ЊаІЯаІА ටගථа¶Яа¶њ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙аІЗа¶∞ а¶∞аІЗපථ ඐථаІНа¶І а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ЬаІАа¶ђа¶ња¶Ха¶Ња¶єаІАථ а¶Па¶З а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙ඐඌඪаІАබаІЗа¶∞ а¶∞аІЗපථ ඐථаІНа¶І а¶єа¶≤аІЗ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАථ а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ХаІБа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Њ ඙аІНа¶∞පඌඪථ ඙аІБථа¶∞а¶ЊаІЯ а¶∞аІЗපථ а¶Ъа¶Ња¶≤аІБа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ ටаІО඙а¶∞ а¶єа¶≤аІЗа¶У, а¶Па¶З а¶ђа¶ња¶≤а¶ЃаІНа¶ђ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙ඐඌඪаІАබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ බаІБа¶Га¶Єа¶є а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗа•§
а¶Зටගඁ඲аІНа¶ѓаІЗ аІ®аІѓа¶ЃаІЗ ටඌа¶∞а¶ња¶ЦаІЗ ‘බගථයඌа¶Яа¶Њ а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶ЃаІЗа¶≤а¶Њ а¶ЄаІЗа¶ЯаІЗа¶≤а¶ЃаІЗථаІНа¶Я а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙аІЗ’ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІАаІЯ а¶ЄаІНа¶ђа¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞ ඁථаІНටаІНа¶∞а¶ХаІЗа¶∞ а¶ѓаІБа¶ЧаІНа¶Ѓ а¶Єа¶Ъа¶ња¶ђ а¶ХаІЗ.а¶ђа¶њ.а¶Єа¶ња¶В а¶Па¶∞ ථаІЗටаІГටаІНа¶ђаІЗ ටගථ ඪබඪаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඙аІНа¶∞ටගථග඲ග බа¶≤ ඙а¶∞ගබа¶∞аІНපථаІЗ а¶Па¶≤аІЗ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙ඐඌඪаІАа¶∞а¶Њ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЛа¶≠ а¶Йа¶ЧаІЬаІЗ බаІЗа¶®а•§ а¶ПඁථගටаІЗа¶З а¶∞аІЗපථ ථගаІЯаІЗ а¶ХаІНа¶ЈаІЛа¶≠ ටаІЛ а¶Ыа¶ња¶≤а¶З, а¶Й඙а¶∞ථаІНටаІБ аІІаІ¶аІ¶ බගථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь ආගа¶Хඁට ථඌ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ, а¶Єа¶ЃаІЯඁට ඙ඌа¶∞ගපаІНа¶∞а¶Ѓа¶ња¶Х ථඌ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ, а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗපаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶Ьа¶Ѓа¶Њ а¶ђа¶ња¶ХаІНа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Еа¶ЄаІБа¶ђа¶ња¶Іа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶≠аІГටග а¶Па¶Ха¶Ња¶Іа¶ња¶Х а¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶Уа¶З ඙аІНа¶∞ටගථග඲ග බа¶≤а¶ХаІЗ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶Ьа¶Ња¶®а¶Ња¶®а•§ а¶Па¶Ха¶З а¶ЪගටаІНа¶∞ а¶ЃаІЗа¶Ца¶≤аІАа¶Ча¶ЮаІНа¶Ь а¶ђаІНа¶≤а¶ХаІЗа¶∞ а¶≠аІЛа¶Яа¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙аІЗа¶Уа•§ а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ ටаІБа¶≤ථඌаІЯ а¶ЖපаІНа¶∞ගට ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඪබඪаІНа¶ѓ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ а¶ђаІЗපаІА а¶єа¶УаІЯа¶ЊаІЯ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶ХаІЗа¶З а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ а¶ђа¶Ња¶∞ඌථаІНබඌаІЯ ඕඌа¶ХටаІЗ а¶єаІЯа•§ а¶Па¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶У පаІАට, а¶ЧаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Ѓ, а¶ђа¶∞аІНа¶Ја¶ЊаІЯ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ХаІГටගа¶Х ඙аІНа¶∞ටගа¶ХаІВа¶≤ටඌ а¶Єа¶є ඙ඌථаІАаІЯ а¶Ьа¶≤, පаІМа¶Ъа¶Ња¶Ча¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Еа¶≠а¶Ња¶ђ; а¶∞аІЗපථ а¶У ඐගබаІНа¶ѓаІБටаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Њ ටаІЛ а¶Ыа¶ња¶≤а¶З, ටඐаІЗ а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶Єа¶Ва¶ЄаІНඕඌථаІЗа¶∞ а¶Еа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ ටаІАа¶ђаІНа¶∞ а¶Жа¶∞аІНඕගа¶Х а¶Єа¶Ва¶Ха¶ЯаІЗ а¶≠аІБа¶ЧටаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ඙аІНа¶∞පඌඪථаІЗа¶∞ ටа¶∞а¶ЂаІЗ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙аІЗ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІНඕаІНа¶ѓ පගඐගа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථ, а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНඕඌа¶≤аІАа¶∞ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶ЬථаІАаІЯ а¶Й඙а¶Ха¶∞а¶£ ටаІБа¶≤аІЗ බගа¶≤аІЗа¶У а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙ඐඌඪаІАබаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЛа¶≠аІЗа¶∞ ථගа¶∞ඪථ а¶єаІЯа¶®а¶ња•§ බගථයඌа¶Яа¶Њ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙аІЗ а¶∞аІЗපථ ථගаІЯаІЗ а¶ѓаІЗ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶Ыа¶ња¶≤, ටඌа¶∞ а¶ХаІЛථа¶У а¶ЄаІБа¶∞а¶Ња¶єа¶Њ а¶єаІЯ а¶®а¶ња•§ а¶Е඙а¶∞аІНඃඌ඙аІНට а¶∞аІЗපථ ථගаІЯаІЗ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЛа¶≠ ඙аІБа¶ЮаІНа¶ЬаІАа¶≠аІВට යටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ ඙аІНа¶∞ටаІНඃඌපඌ ඙аІВа¶∞а¶£ а¶єаІЯථග а¶ђа¶≤аІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙ඐඌඪаІА а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Хඕඌа¶У а¶ЬඌථටаІЗ බаІНа¶ђа¶ња¶Іа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а¶®а¶ња•§
ථඌ-ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶Х
ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶Ча¶≠аІАа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ ඙аІЬаІЗථ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ђа¶Ња¶ЄаІАබаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Ња¶Ва¶ґа•§ аІ®аІ¶аІІаІІ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶≠а¶Ња¶∞ට-а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗප а¶ѓаІМඕ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ЧаІЗ බаІБ’බаІЗපаІЗа¶∞ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ЧаІБа¶≤ගටаІЗ а¶Ьථа¶Ча¶£а¶®а¶Њ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗ а¶ђа¶єаІБ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ ථඌඁ ටඌа¶≤а¶ња¶Ха¶Њ а¶≠аІБа¶ХаІНට а¶єаІЯථග а¶ђа¶≤аІЗ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶УආаІЗа•§ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ђа¶Ња¶ЄаІАа¶∞а¶Њ а¶Па¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ ඙аІНа¶∞පඌඪථа¶ХаІЗ බඌаІЯаІА а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶У, а¶Ча¶£а¶®а¶Њ а¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗ а¶Й඙ඪаІНඕගට ථඌ ඕඌа¶Ха¶ЊаІЯ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ ථඌඁ а¶УආаІЗа¶®а¶ња•§ а¶ЃаІЗа¶Ца¶≤аІАа¶Ча¶ЮаІНа¶Ь පයа¶∞ а¶Єа¶Ва¶≤а¶ЧаІНථ ‘а¶Іа¶ђа¶≤а¶ЄаІВටаІА а¶ЃаІГа¶ЧаІА඙аІБа¶∞’ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗа¶∞ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶ЬඌථගаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ а¶ЄаІЗа¶Ха¶•а¶Ња•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Ча¶£а¶®а¶Њ а¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х පаІНа¶∞а¶Ѓа¶ња¶Ха¶∞а¶Њ а¶≠ගථ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤ ඐගථගඁаІЯаІЗ а¶ђа¶єаІБ а¶Жа¶ЧаІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗපаІЗа¶∞ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ЧаІБа¶≤а¶њ ඕаІЗа¶ХаІЗ ‘а¶≤аІЗа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶За¶ЧаІНа¶∞аІЗපථ’ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶≠ගථ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶Па¶З යගථаІНබаІБ а¶У а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථ පаІНа¶∞а¶Ѓа¶ња¶Х а¶ђа¶Њ а¶≤аІЗа¶ђа¶Ња¶∞බаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђаІЬ а¶Еа¶Вපа¶З аІ®аІ¶аІІаІІ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶Ьථа¶Ча¶£а¶®а¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඐඌබ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓа¶Ња¶®а•§ පаІБа¶ІаІБ а¶ПබаІЗපаІЗа¶З ථаІЯ, а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗපаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ЧаІБа¶≤ගටаІЗа¶У а¶ЕථаІБ඙ඪаІНඕගටගа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶Па¶ђа¶В а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ බаІЗපබаІНа¶∞аІЛයගටඌа¶∞ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч ඕඌа¶Ха¶ЊаІЯ ථඌඁ ටඌа¶≤а¶ња¶Ха¶Ња¶≠аІБа¶ХаІНට а¶єаІЯа¶®а¶ња•§ а¶Па¶З а¶ѓаІМඕ а¶Ьථа¶Ча¶£а¶®а¶Њ ථගаІЯаІЗ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ђа¶Ња¶ЄаІАබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНට а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶Па¶З а¶≠аІБа¶≤аІЗ а¶≠а¶∞а¶Њ а¶Ьථа¶Ча¶£а¶®а¶Њ а¶Єа¶ВපаІЛ඲ථаІЗа¶∞ බඌඐаІАටаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯපа¶З а¶ЄаІЛа¶ЪаІНа¶Ъа¶Ња¶∞ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§
඙аІНа¶∞ඌඕඁගа¶Ха¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Па¶З а¶Ьථа¶Ча¶£а¶®а¶Њ ථගаІЯаІЗ а¶ХаІЛථа¶У а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Њ ටаІИа¶∞а¶њ ථඌ а¶єа¶≤аІЗа¶У, ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАටаІЗ ඐග඙аІБа¶≤ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІНа¶ЃаІБа¶ЦаІАථ යටаІЗ а¶єаІЯа•§ аІ®аІ¶аІІаІЂ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ аІђа¶З а¶ЬаІБථ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඪ඙аІНටඌයа¶Ха¶Ња¶≤ а¶ђаІНඃඌ඙аІА а¶ѓаІЗ а¶Ьථа¶Ча¶£а¶®а¶Њ а¶У ‘а¶Е඙පථ’ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь පаІБа¶∞аІБ а¶єаІЯ, ටа¶Цථ аІ®аІ¶аІІаІІ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගඐаІЗබථа¶Яа¶ња¶ХаІЗа¶З а¶≠ගටаІНටග а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђаІЗ а¶Іа¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶Уа¶З ටඌа¶≤а¶ња¶Ха¶Њ а¶ђа¶єа¶ња¶∞аІНа¶≠аІВටබаІЗа¶∞ ථඌඁ а¶ЕථаІНටа¶∞аІНа¶≠аІБа¶ХаІНට ටඌටаІЗ а¶єаІЯ а¶®а¶ња•§ а¶Па¶З а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ ථаІЗයඌටа¶З а¶Ха¶Ѓ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶ЙආаІЗа¶Ыа¶ња¶≤, ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ аІ©аІ¶ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ђа¶Ња¶ЄаІАа¶∞ ථඌඁ ථඕගа¶≠аІБа¶ХаІНට а¶єаІЯ а¶®а¶ња•§ а¶Пඁථ а¶ХаІА ඃඌබаІЗа¶∞ ථඌඁ ථඕගа¶≠аІБа¶ХаІНට а¶єаІЯ ථග, ටඌබаІЗа¶∞ ථටаІБථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶∞ а¶ЕථаІНටа¶∞аІНа¶≠аІБа¶ХаІНට а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶ђаІЗ ථඌ а¶ђа¶≤аІЗа¶У බаІБ’ බаІЗපаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞පඌඪථаІЗа¶∞ ටа¶∞а¶ЂаІЗ а¶ЬඌථගаІЯаІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶єаІЯа•§ බаІБ’බаІЗපаІЗа¶∞ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Па¶З ථඕගа¶≠аІБа¶ХаІНට ථඌ а¶єа¶УаІЯа¶Њ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ђа¶Ња¶ЄаІАබаІЗа¶∞ а¶ХаІЛථ а¶Еа¶ЄаІНටගටаІНа¶ђ ථඌ ඕඌа¶Ха¶ЊаІЯ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶Ха¶Ња¶∞аІНඃට ථඌ-ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶ХаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶£а¶§ а¶єа¶®а•§ ඐගථගඁаІЯаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ ඐගපаІЗඣට а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ЧаІБа¶≤а¶њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶ѓаІЗඁථ а¶ПබаІЗපаІЗ а¶Жа¶Єа¶Ња¶∞ ‘а¶Е඙පථ’ බගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤, ටаІЗඁථа¶З а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶За¶ЪаІНа¶ЫаІБа¶Х ඕඌа¶Ха¶≤аІЗа¶У, ටඌа¶≤а¶ња¶Ха¶ЊаІЯ ථඌඁ ථඌ ඕඌа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶Ч ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶ЮаІНа¶Ъගට а¶єа¶®а•§ а¶Пඁථа¶У а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Па¶Ха¶З ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З ‘а¶Е඙පථ’ බගа¶≤аІЗа¶У, а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ а¶Ха¶∞аІНටඌа¶З а¶ПබаІЗපаІЗ а¶Жа¶Єа¶Ња¶∞ а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶Ч ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶ЮаІНа¶Ъගට а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ѓаІЗඁථ а¶ђа¶Ња¶Бපа¶Ха¶Ња¶Яа¶Њ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗа¶∞ а¶ђа¶≤а¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶£ а¶У ටඌа¶Ба¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞ а¶Па¶З а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ ඙аІЬаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ђа¶≤а¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶£ ථගа¶ЬаІЗ ‘а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤ а¶За¶Йථඌа¶За¶ЯаІЗа¶° а¶Ха¶Ња¶ЙථаІНа¶Єа¶ња¶≤аІЗ’а¶∞ а¶Єа¶≠ඌ඙ටග а¶єа¶≤аІЗа¶У, аІ®аІ¶аІІаІІ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶Ьථа¶Ча¶£а¶®а¶ЊаІЯ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ථඌඁ а¶Йආа¶≤аІЗа¶У ටඌа¶Ба¶∞ ථඌඁ ථඕගа¶≠аІБа¶ХаІНට а¶єаІЯа¶®а¶ња•§ а¶Ђа¶≤аІЗ аІ®аІ¶аІІаІЂ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶За¶ЪаІНа¶ЫаІЗ ඕඌа¶Ха¶≤аІЗа¶У, ‘а¶Е඙පථ’ බගටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа¶®а¶®а¶ња•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЄаІНටаІНа¶∞аІА а¶ЄаІНඐ඙аІНථඌ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶£ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞ а¶Єа¶є а¶ПබаІЗපаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Па¶≤аІЗа¶У, а¶ЄаІЗа¶З а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶Ч ඕаІЗа¶ХаІЗ ටගථග а¶ђа¶ЮаІНа¶Ъගට а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞ ඁට а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶Жа¶ЫаІЗථ, а¶ѓа¶Ња¶БබаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞ а¶ПබаІЗපаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Па¶≤аІЗа¶У, ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶Па¶Цථа¶У а¶ПබаІЗපаІЗа¶∞ ‘ථඌ-ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶Х’а•§
පаІБа¶ІаІБ а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Х а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗа¶З ථаІЯ, а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗපаІЗа¶∞ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗа¶∞ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶Па¶З а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ ඙аІЬаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ѓаІЗඁථ аІ®аІ¶аІІаІ≠ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ЬаІБа¶≤а¶Ња¶З а¶Ѓа¶Ња¶Є ඙а¶∞аІНඃථаІНට ඁපඌа¶≤а¶°а¶Ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞ аІІаІ¶а¶Яа¶њ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ аІ™аІ≠ а¶Ьථ а¶ХаІЛථа¶Уа¶∞аІВ඙ ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶ХටаІНа¶ђаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ඙ටаІНа¶∞ ඙ඌаІЯ а¶®а¶ња•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ аІ®аІ¶аІІаІІ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ѓаІМඕ а¶Ьථа¶Ча¶£а¶®а¶ЊаІЯ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ ථඌඁ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Ђа¶≤аІЗ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට а¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶њ а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶Ч а¶ЄаІБа¶ђа¶ња¶Іа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶ЮаІНа¶Ъගට а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤ ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ ඙а¶∞аІЗа¶У а¶Па¶∞පඌබ а¶Жа¶≤а¶њ, а¶За¶Ѓа¶Ња¶Ѓа¶Жа¶≤ගබаІЗа¶∞ ඁට ඁපඌа¶≤а¶°а¶Ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞ а¶Па¶З ඙а¶∞а¶ња¶ЪගටගයаІАථ ථඌ-ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶ХබаІЗа¶∞ ඁට а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶∞а¶З ථа¶∞а¶Х ඃථаІНටаІНа¶∞а¶£а¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Па¶Х а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Еа¶ІаІНа¶ѓа¶ЊаІЯа•§
а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤аІЗа¶∞ ඐගථගඁаІЯ а¶єа¶≤аІЗа¶У, බаІАа¶∞аІНа¶Ш ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ ඪඌට බපа¶ХаІЗа¶∞ а¶ХаІНඣටаІЗ ඙аІНа¶∞а¶≤аІЗ඙ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ බаІНа¶∞аІБට а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ ථаІЯа•§ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЙථаІНථаІЯථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ а¶Єа¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Я а¶єа¶≤аІЗа¶У, ටඌ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІНඃඌපඌ ඙аІВа¶∞а¶£ а¶єаІЯට а¶Ха¶∞аІЗа¶®а¶ња•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶Еа¶ЃаІЛа¶ЪථаІАаІЯ а¶ХаІНඣට ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ХаІНа¶ЈаІЛа¶≠аІЗа¶∞ а¶ЙබаІНа¶Ча¶ња¶∞а¶£ а¶Ша¶ЯаІЗа¶ЫаІЗ ආගа¶Ха¶З, а¶ХගථаІНටаІБ ඐගථගඁаІЯаІЗа¶∞ а¶ЄаІБа¶Ђа¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶ђа¶ЮаІНа¶Ъගට а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ а¶Пඁථа¶Яа¶Ња¶У ථаІЯа•§ а¶ђа¶ња¶Чට බපа¶ХаІЗ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶У ටඌа¶БබаІЗа¶∞ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђа¶ЄаІВа¶∞а¶ња¶∞а¶Њ ටඕඌа¶Хඕගට ‘а¶≠а¶Ња¶ЧаІНа¶ѓаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ЪаІБа¶ХаІНටග’а¶∞ а¶Ђа¶≤පаІНа¶∞аІБටගටаІЗ а¶ѓаІЗ а¶ђа¶ња¶Ха¶≤а¶Ња¶ЩаІНа¶Ч а¶ЬаІАඐථ ඃථаІНටаІНа¶∞а¶£а¶Њ а¶≠аІЛа¶Ч а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗථ, ටඌа¶∞ ඙аІБථа¶∞а¶Ња¶ђаІГටаІНටග а¶Жа¶∞ а¶Ха¶ЦථаІЛа¶З а¶Ъඌථ а¶®а¶Ња•§
ටඕаІНа¶ѓа¶ЄаІВටаІНа¶∞а¶Г ‘а¶ЖථථаІНබඐඌа¶Ьа¶Ња¶∞ ඙ටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Њ’, ‘а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶Ч а¶Єа¶Вඐඌබ’, ‘а¶ЙටаІНටа¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶∞ඌබගථ’, ‘а¶Па¶З а¶Єа¶ЃаІЯ’, ‘а¶ђа¶∞аІНටඁඌථ’඙ටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Ња¶∞ ථගа¶∞аІНа¶ђа¶Ња¶Ъගට а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Ња•§ а¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶Х а¶Ыа¶ња¶Яа¶Ѓа¶єа¶≤а¶ђа¶Ња¶ЄаІАබаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶ХаІНа¶Ја¶ЊаІОа¶Ха¶Ња¶∞ а¶У а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞а¶Єа¶ЃаІАа¶ХаІНа¶Ја¶Ња•§
Have an account?
Login with your personal info to keep reading premium contents
You don't have an account?
Enter your personal details and start your reading journey with us
Design & Developed by: WikiIND
Maintained by: Ekhon Dooars Team