









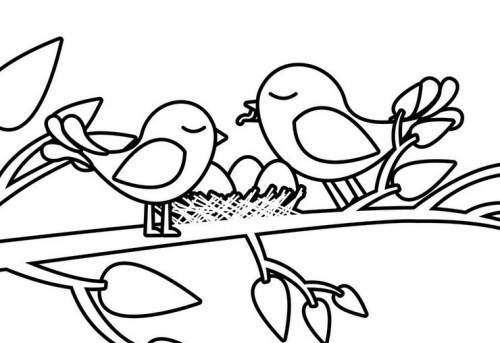


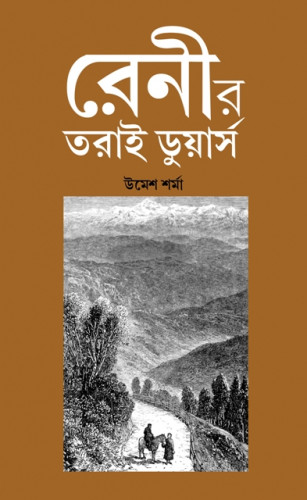



 তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস
তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত লোকসংগীত ভাওয়াইয়া। আর ভাওয়াইয়া গানের মূল সঙ্গত হল দোতারা। এই বাদ্যযন্ত্রটিতে দুইটি মাত্র তার থাকে। সে কারণেই এই নাম। কাঁঠাল কাঠের তৈরি এই দোতারা হাতেই টগর অধিকারী জয় করেছিলেন মানুষের মন। তাঁর দোতারা শুধু সঙ্গত করতো না, কথা বলতো। হরবোলার মত। সেই দোতারায় যেমন বাজতো উলুধ্বনি, তেমনি তা থেকে বের হতো মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় মায়ের করুণ কান্নার সুর। যারা খুব কাছ থেকে টগর অধিকারীকে দেখেছেন, সেইসব মানুষের কাছেই এসব কথা শোনা। এই দোতারায় প্রথম স্টিলের তার ব্যবহার করার কৃতিত্বও তাঁরই। যন্ত্র ও কন্ঠ সংগীত দুটোতেই তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। টগর অধিকারী সে যুগের এক বিস্ময়। শেষ জীবনে যার সম্বল ছিল ভিক্ষাবৃত্তি। তাঁর জীবন সিনেমার স্ক্রিপ্টকেও হার মানায়।
সেটা ১৯৪৩ সাল। সারা ভারত কন্ঠ ও যন্ত্রসংগীত সন্মেলন। দোতারার ডাং-এ মন্ত্রমুগ্ধ গোটা বোম্বাই (অধুনা মুম্বাই) শহর। তাবড় তাবড় সংগীতপ্রেমী থেকে শুরু করে যন্ত্র ও সংগীত শিল্পীরাও দোতারার সুরের মুর্ছনায় আচ্ছন্ন। পন্ডিত রবিশঙ্কর, শচীন দেব বর্মন, সলিল চৌধুরী, ভাল্লাসোল, অনন্ত পট্টনায়েক-- কে নেই সেই মুগ্ধতার তালিকায়। স্বাভাবিক ভাবেই সেই অনুষ্ঠানে যন্ত্রসংগীতে জয়ের মুকুটও উঠলো দোতারা শিল্পীর মাথায়। এ যেন এক্কেবারে এলাম দেখলাম জয় করলাম অবস্থা। অবশ্য এই শিল্পীর ক্ষেত্রে সেটা হয়েছিল, এলাম বাজালাম জয় করলাম। কারন, যার জয়ের কথা এখানে বলা হচ্ছে, তাঁর পক্ষে চোখ দিয়ে দেখা সম্ভব ছিল না। তিনি ছিলেন একপ্রকার জন্মান্ধ। জীবনকে দেখা বোঝা সবটাই ছিল অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। তিনি টগর, টগর অধিকারী। দোতারা সম্রাট। কানা টগর নামেই বেশি পরিচিত।
টগর অধিকারীর বাবা শ্রীকান্ত অধিকারী ছিলেন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষ। মা কলামতী দেবী। সাধারণ গরীব পরিবারে ১৯১২ (মতান্তরে ১৯১৪) সালে টগরের জন্ম। তিন ভাই। টগর, পূর্ণহরি, বৃন্দাবন ও এক বোন গন্ধেশ্বরী। প্রথম জীবনে টগরের পরিবার কোচবিহারে থাকলেও পরবর্তীতে তারা পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসমে চলে যায়। তাই টগর অধিকারীর জন্মস্থান নিয়ে একটা মতভেদ আছে। তবে ছোটোভাই বৃন্দাবন অধিকারীর কথা অনুযায়ী, 'মা নিজে কইছে টগরের জন্মস্থান দেবগ্রাম। টগরের বিয়াও হইছে কিন্তু কোনো সন্তান নাই, টগরের পত্নীর নাম পদ্মেশ্বরী অধিকারী তার একটা চকু অন্ধ আছিল ' (তথ্যসূত্র : নিখিল কুমার চন্দ)।
এই দেবগ্রাম কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির বারোকোদালি অঞ্চলের মধ্যে পরে। দেবগ্রামের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে খরস্রোতা রায়ডাক। পাহাড়ী নদী হওয়ার কারণে বর্ষাকালে যখন তখন তার গতিপথ পরিবর্তন করে। ফলে মাঝমধ্যেই চাষের জমি, বাস্তুভিটে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। অনুমান করা হয়, তেমনি কোনো একটি ঘটনায় টগরের পরিবার দেবগ্রাম থেকে চলে যান অসম রাজ্যের অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জেলার খেরবাড়ি গ্রামে। রাজনৈতিক ভাবে টগরের দুটো জায়গা আলাদা হলেও ভৌগলিকগত ভাবে এরা এক। তেমনি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দিক থেকেও এদের মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই। বাড়িতে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল ছিল। পালাগানের আসর, বিভিন্ন লোকসংগীত, লৌকিক দেবদেবীর পূজার পালাগান, দোতারার রেওয়াজ, সংগীতের আসর ছোটো থেকেই এসবের মধ্যে বেড়ে উঠছিল টগর। জানা যায়, জন্মের সাত দশদিন পরই তাঁর দৃষ্টিশক্তি চলে যায়। ফলে প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয়নি। প্রকৃতির মধ্যেই শুরু হয় তাঁর জীবনের শিক্ষা। সাংগীতিক পরিমন্ডলে বেড়ে ওঠার কারনে সংগীতের প্রতি একটা টান ছিলোই। তাই দোতরা হাতে শুরু হল সংগীত শিক্ষা। প্রথম গুরু আসামের গিদাল চ্যামারু চড়কিয়া। দোতরা বাজানোর তালিমের পাশাপাশি তিনি টগরকে শিখিয়েছিলেন ব্যানা (বেহালার মত দেখতে, ঘোড়ার চুল দিয়ে তৈরি), বাঁশী, সারিন্দা বাজাতেও। বিভিন্ন পালাগান, কীর্তনের আসরে সব সময় সঙ্গে রাখতেন প্রিয় শিষ্য কিশোর টগরকে। এই সময় থেকেই টগর নিম্ন অসম ও কুচবিহারের মানুষের মনে জায়গা করতে শুরু করে। সংগীত শিক্ষার পাশাপাশি চলে অর্থ উপার্জন। টগরের জীবনে দ্বিতীয় গুরু তুফানগঞ্জের রাজারকুঠি গ্রামের প্রিয়নাথ রায়। তিনি ছিলেন বিখ্যাত 'শ্রীদেওয়ানি' যাত্রাদলের মাস্টার। এখানেও বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র যেমন, হারমোনিয়াম, তবলা, খোল, বেহালা এসব বাজাতে শেখেন তিনি। তবে প্রথাগত সংগীত শিক্ষা শুরু হয় সুরেন্দ্রনাথ রায় বসুনীয়ার সংস্পর্শে আসার পর। তিনি ছিলেন উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত ভাওয়াইয়া গানের পথিকৃৎ। প্রসঙ্গত ইনি ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাসউদ্দিনেরও গানের গুরু। এই সুরেন বসুনিয়ার হাত ধরেই প্রথম কলকাতা যাত্রা টগরের। সেটা ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাস। ভাওয়াইয়া দুখানি গানের রেকর্ড প্রকাশ হয় এইচএমভি থেকে। এটাই ভাওয়াইয়া গানের ইতিহাসে সর্বপ্রথম রেকর্ড। সেখানে দোতারায় সঙ্গত করেছিলেন টগর অধিকারী।
কলকাতায় এই সময়ই টগর কাজী নজরুল ইসলামের সংস্পর্শে আসেন। পরিচয়ের সূত্র সুরেন বসুনীয়া। ওনার সাথে খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল নজরুলের। সুরেন বসুনীয়া কলকাতায় গেলেই হোটেলে কাজী সাহেব চলে আসতেন আড্ডা দিতে। সেখানেই টগর অধিকারীর সাথে পরিচয় ও ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হয় নজরুল ইসলামের। সেসব আড্ডার মূল আলোচ্যই ছিল সংগীত। এছাড়াও মাঝেমধ্যেই কোচবিহারের ম্যাগাজিন রোডে সুরেন বসুনীয়ার বাড়িতে টগর অধিকারী এসে থাকতেন। চলত গান আর দোতারার তর্জা, সাথে ভাওয়াইয়া আর শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা। এখানে একটা কথা এখনও বলা হয়নি, তা হল, টগর অধিকারীর কিন্তু গায়ক হিসেবেও যথেষ্ট সুনাম ছিল। দোতারার পাশাপাশি তিনি রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি, ভাওয়াইয়া, শাস্ত্রীয় সংগীত সহ লোক সংগীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তাঁর গলা অসাধারণ ছিল। পরবর্তীতে স্বর নষ্ট হয়ে যায়। কারণ হিসেবে জানা যায়, ভোন্দা গীদাল তার সংগীত প্রতিভায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কিছু একটা খাইয়ে তার গলার স্বর নষ্ট করে দিয়েছিল। যদিও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত টগর অধিকারী গান গেয়ে গিয়েছেন।
গ্রামের সাধারণ সংগীত শিল্পী হয়ে জীবন শুরু করলেও ১৯৪০-৪১ নাগাদ তাঁর যোগাযোগ হয় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। এখান থেকেই শুরু হলো টগরের জীবনের একটা নতুন অধ্যয়। তিনি শুরু করলেন এবার মানুষের জন্য গান গাওয়া। গণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেন গণনাট্য সংঘের সদস্য হিসেবে। সেসব সময় কলকাতার পার্টি অফিসেই থাকতেন তিনি। ১৯৪৩ সাল, সেবার টগর গিয়েছে সুরেন বসুনীয়ার সাথে কলকাতায়। দুজন যথারীতি হোটেলেই ওঠেন। পরের দিন তিনখানা গান রেকর্ড করেন এইচএমভি থেকে। দোতারায় সঙ্গতকারী টগর। তার পরদিন আরও গান রেকর্ড হওয়ার কথা। সেদিন সকালে কোনো একটা কাজে সুরেন বসুনীয়া হোটেলের বাইরে যান। সেই সময় কয়েকজন লোক এসে টগরকে চা খাওয়ানোর কথা বলে তাকে নিয়ে সোজা বোম্বাই পাড়ি দেয়। প্রসঙ্গত, চা বস্তুটির প্রতি টগর অধিকারীর অসম্ভব আসক্তি ছিল। পরবর্তীতে দেখা গেছে চা খাওয়ানোর বিনিময়ে লোককে গান অথবা দোতারা শোনাতে। যাই হোক, সুরেন বসুনীয়া হোটেলে ফিরে দেখে টগর নেই। পরে সব ঘটনা জানতে পেরে আর গান রেকর্ডিং না করে কুচবিহারে ফিরে আসেন। আর টগরকে নিয়ে ওরা তোলে কমিউনিস্ট পার্টির মুম্বাইয়ের কেন্দ্রীয় পার্টি অফিসের বাড়িতে।
সে সময় মুম্বাইতে সারা ভারত যন্ত্র ও কন্ঠসংগীত প্রতিযোগিতা চলছিল। গণনাট্য সংস্থার উদ্যোগে টগর অধিকারীকে সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করানো হয়। যন্ত্রসংগীত বিভাগে দোতারা বাজিয়েছিলেন তিনি। সংগীত সম্রাট আলাউদ্দিন খাঁ থেকে শুরু করে কেরলের মহাকবি ভাল্লাথোল, পন্ডিত রবিশঙ্কর সকলেই জন্মান্ধ বিরল প্রতিভার এই মানুষটার দোতারা শুনে মুগ্ধ। সেবার যন্ত্রসংগীতে বিজয়ী হয়েছিলেন টগর অধিকারী। কিছুদিন ছিলেন শচীন দেব বর্মনের বাড়িতে। পরে আবার পার্টি অফিসে আশ্রয় পান। মুম্বাইতে তিনি যেমন বিরল ব্যক্তিত্বদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তেমনি তাদের কাছে পেয়েছিলেন সংগীতের নানান পাঠ। এসময় হঠাৎই পতিতা পল্লীতে তার নিয়মিত যাতায়াত শুরু হয়। কীভাবে তিনি এই কুসঙ্গে পড়েছিলেন তা জানা যায়নি। ফলস্বরূপ অচিরেই তিনি যৌনরোগে আক্রান্ত হন। সেখানে তার চিকিৎসা চলে। সুস্থ হলে তাকে কলকাতা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অভিশপ্ত এই সময়টুকুর জন্য পরবর্তীতে তিনি বহু অনুশোচনা করেছেন। অবশ্য তাঁর প্রতিভার ছটা মানুষের মন থেকে এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাটিকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।
এরপর গণনাট্য সংঘের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য কলকাতা যাওয়া আসা চলতেই থাকে। এসময় তাঁর ঠিকানা ছিল ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটের পার্টি অফিস। এখানে নিয়মিত এসে টগরের সাথে দেখা করে যেতেন তাঁর আরেক গুণমুগ্ধ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য সবার সাথে ঘনিষ্ঠতা এই গণ আন্দোলনের সূত্রেই। ১৯৪৮ সালে 'অহল্যা' নৃত্যনাট্যে কাজের সূত্রে ঘনিষ্ঠতা হয় সলিল চৌধুরীর সঙ্গে। ১৯৫২ সালে পার্ক সার্কাস ময়দানে শান্তি সন্মেলনে তাঁর দোতারা বাদন মুগ্ধ করে সারা কলকাতাবাসীকে। সেখানে মঞ্চস্থ হয় তুলসী লাহিড়ীর রচিত 'ছেঁড়াতার' নাটকটি। নাটকের আবহ সংগীতে টগরের বেহালার করুণ সুরের মুর্ছনা অভিভূত করে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা প্রতিনিধিদের।
১৯৫৫ সালে গণনাট্যের প্রথম রাজ্য সন্মেলন হয়েছিল। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী সেখানে টগরের দোতারা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান। সে বছরই রংপুরে গণনাট্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন টগর অধিকারী। কতশত শিল্পী সাহিত্যিকের সাথে যে তাঁর সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল তার তালিকা বড়ই দীর্ঘ। এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়।
এসব ছাড়াও টগরের রচিত ও সুরারোপিত গানের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। তাঁর রচিত গান "দিনের শোভা সুরজরে / রাতের শোভা চাঁদ" সেসময় শত শত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তেভাগা আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর, মানুষের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে দোতারাকে সম্বল করে পথে পথে গান গেয়ে বেড়িয়েছেন। বিজন ভট্টাচার্য তাঁর 'মরণচাঁদ' নাটকটি উৎসর্গ করেছিলেন টগরকে। নাটকে পবন চরিত্র আসলে টগর অধিকারী। খাদ্য আন্দোলনের সময় কোচবিহারে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে, তার প্রতিবাদেও গর্জে উঠেছিলেন তিনি। অথচ এত কিছুর পরেও জীবনের শেষ দিনগুলি কেটেছে ভয়ানক দুঃখ ও দারিদ্র্যতায়। মুম্বাই তথা ভারতজয়ী শিল্পী শেষ জীবনে একপ্রকার ভিক্ষাবৃত্তিকে সম্বল করে বেঁচে ছিলেন। সরকারি কোনো সাহায্য পাননি তিনি। হাঁপানির জন্য সুর টানতে কষ্ট হতো, গলাও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। প্রতি সোমবারের হাটে তুফানগঞ্জে আসতেন গান গেয়ে ভিক্ষে করার জন্য। কাচারির সামনে বসে গান গাইতেন। লোকে শুনে পয়সা দিত। চা সিঙ্গারাও দিত গান ও দোতারা বাজানোর বিনিময়ে। ঈশ্বরপ্রদত্ত শিল্পীর কী মর্মান্তিক পরিণতি হয় আমাদের দেশে!
তাঁর যাদুকরী বাজনা যারা শুনেছে তারা এই জীবনে ভুলতে পারেনি সেই সুর। ছোটোখাটো চেহারার মানুষটি সারা জীবন হাফ সার্ট আর হাঁটুর ওপরে ধুতি পরেই কাটিয়ে দিয়েছেন তাঁর জীবন। সাংস্কৃতিক জগতের যে পরিমন্ডলে একসময় তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল, সেটা অসম্ভব প্রতিভাধর না হলে কখনও সম্ভব হতো না। অথচ অসামান্য প্রতিভাধর এই শিল্পীর সঠিক মূল্যায়ন হল না আজও। আজও তিনি রয়ে গিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেই। প্রিয় রাগ বেহাগের মতই তাঁর নিজের জীবনটাও ছিল করুণ সুরে বাঁধা। ১৯৭২ সালের জুন মাসে খেরবাড়িতে তাঁর দেহাবসান হয়। আর বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যান টগর অধিকারী।
ভাওয়াইয়া সম্রাট যদি আব্বাসউদ্দিন হন, তবে নিঃসন্দেহে দোতারা সম্রাট হলেন টগর অধিকারী। তাঁর সমসাময়িক আব্বাসউদ্দিন, নায়েব আলী টেপু এদের সবার জন্য কত কিছুই না করা হচ্ছে। অথচ আজ পর্যন্ত টগর অধিকারীর স্মৃতি রক্ষার জন্য তেমন কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করা হলো না। না সরকারি তরফে, না বেসরকারি। তাঁর জন্মভিটারও সংরক্ষনের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি আজও। তবে একটাই যা সান্ত্বনা, মরা রায়ডাক (বুড়া রায়ডাক) নদীর ওপর বাংলা আসাম সংযোগকারী সেতুর নাম টগর অধিকারীর নামে রাখা হয়েছে। ব্যস শ্রদ্ধাঞ্জলি বলতে এইটুকুই। তবে এটুকুও হতো না, যদি না তৎকালীন কোচবিহার মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক চন্ডী পাল ব্যক্তিগতভাবে এই উদ্যোগটা না নিতেন। সেসময় তাঁরই উৎসাহে তৈরি হয়েছিল 'টগর স্মৃতিরক্ষা কমিটি'। ওই সময়টুকুতে টগর অধিকারীকে নিয়ে কিছুটা নাড়াচাড়া হলেও পরবর্তীতে আবার সব শান্ত হয়ে যায়।
উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত। এই আক্ষেপ আমাদের বরাবর। কিন্তু আমরা নিজেদের সম্পদের কতটুকু মূল্য দিতে পেরেছি যে অন্যদের থেকে আশা করবো? তবুও মুম্বাই সহ অন্যান্য রাজ্যের মানুষ বা কলকাতা তাঁকে যে সম্মান দিয়েছে আমরা ঘরের ছেলেকে সেই আসন দিতে পারলাম কোথায়? উল্টে মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের আগেই মুছে ফেললাম স্মৃতি থেকে। অদ্ভুত আত্মবিস্মৃত জাতি আমরা। যাঁর গান, বাজনা, বহুমুখী প্রতিভা হতে পারতো রীতিমতো গবেষণার বিষয়, তাঁকে নিয়ে কোথাও একটাও শব্দ খরচ করা হয় না। তবে দেরিতে হলেও টগর অধিকারীর মূল্যায়নের সময় এসেছে। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গান যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন দোতারাও থাকবে। তা সে আধুনিকতার ঢেউয়ে যতই অন্যান্য যন্ত্র আসুক দোতারার ডোলডং ডোলডং ছাড়া ভাওয়াইয়া গান প্রাণ পাবে না। আর যতদিন দোতারা থাকবে ততদিন তার ডাং(সুর) এ বেঁচে থাকবে রায়ডাকের পারের অন্ধ ছেলেটা। তাঁকে মানুষের মনে বাঁচিয়ে রাখার দায় দায়িত্ব আমার আপনার কোচবিহারের সবার।
কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ডঃ ধর্মনারায়ণ বর্মা, নির্মলেন্দু চক্রবর্ত্তী
Have an account?
Login with your personal info to keep reading premium contents
You don't have an account?
Enter your personal details and start your reading journey with us
Design & Developed by: WikiIND
Maintained by: Ekhon Dooars Team