







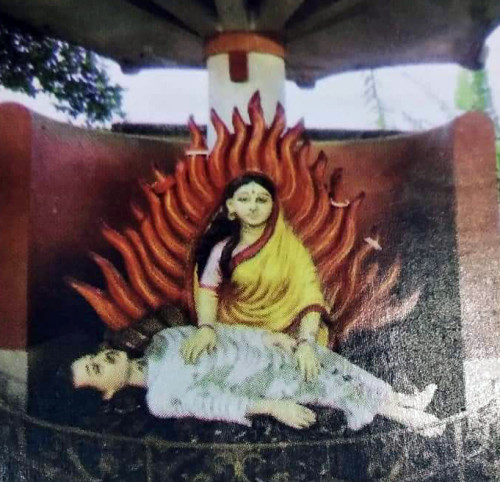









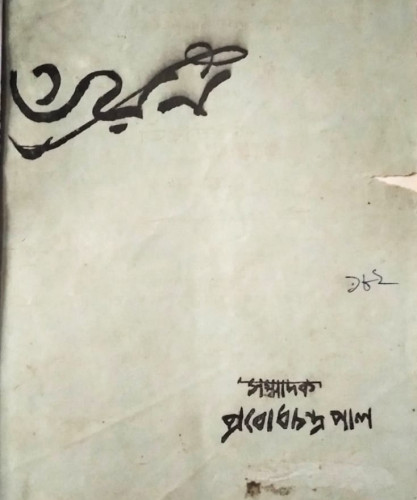




 а¶Єа¶ђаІНа¶ѓа¶Єа¶Ња¶ЪаІА බටаІНට
а¶Єа¶ђаІНа¶ѓа¶Єа¶Ња¶ЪаІА බටаІНට

а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ, а¶ђа¶Њ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶Њ а¶ђа¶Њ а¶ХඌථаІА а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЖථаІБа¶ЈаІНආඌථගа¶Х а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓа•§ а¶ђаІНа¶∞ට а¶У а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІА а¶Па¶З ථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶Іа¶Ња¶∞а¶Њ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа•§ а¶П ථගаІЯаІЗ а¶ђа¶ња¶ЄаІНටඌа¶∞ගට а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ а¶Ха¶∞а¶ђаІЛ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶њ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗ а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯа•§ а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶Єа¶Ва¶ХаІНа¶ЈаІЗ඙аІЗ බаІБ’а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Хඕඌ а¶ЬаІЗථаІЗ ථаІЗа¶ђа•§
а¶ђа¶ња¶ђа¶Ња¶є, а¶ЕථаІНථ඙аІНа¶∞ඌපථ, а¶ЧаІГය඙аІНа¶∞а¶ђаІЗපаІЗа¶∞ ඁට පаІБа¶≠ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗа¶∞ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђаІЗ а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНඕаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ а¶ХඌඁථඌаІЯ а¶Па¶З ඙ඌа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶Єа¶ЃаІН඙аІВа¶∞аІНа¶£ පаІНа¶∞а¶Ња¶ђа¶£ а¶Ѓа¶Ња¶Є а¶ЬаІБаІЬаІЗа¶З а¶Па¶З ඙ඌа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶Па¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶У а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЛථа¶У а¶Єа¶ЃаІЯ а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНඕ ටඌа¶Ба¶∞ ඁඌථඪගа¶Х а¶ЕථаІБа¶Єа¶Ња¶∞аІЗ а¶Па¶З ඙ඌа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ЧаІАට඙аІНа¶∞඲ඌථ а¶Па¶З ථඌа¶ЯаІНа¶ѓаІЗ а¶Еа¶≠ගථаІЯаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶≠аІВа¶Ѓа¶ња¶Ха¶Њ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ ඐථаІНබථඌ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථ බගаІЯаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶єаІЯаІЗ а¶Ѓа¶∞аІНටаІЗ බаІЗа¶ђаІАа¶∞ ඙аІВа¶Ьа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ථаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶≠а¶Ња¶Єа¶Ња¶®а•§ а¶Па¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶З ඙ඌа¶≤а¶Њ а¶Ъа¶≤аІЗ ටගථබගථ, ඙ඌа¶Ба¶Ъබගථ, ඪඌටබගථ, ථаІЯබගථ а¶Еඕඐඌ а¶Па¶Ча¶Ња¶∞аІЛ а¶¶а¶ња¶®а•§ а¶Па¶ХаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶Па¶Х а¶Ша¶Яථඌа¶ХаІНа¶∞а¶Ѓ а¶ЕථаІБа¶Єа¶Ња¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞ටගබගථ а¶Ъа¶≤аІЗ ඙ඌа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Еа¶≠ගථаІЯа•§ а¶Ха¶Цථа¶У а¶ђа¶Њ а¶Па¶ХබගථаІЗа¶З ඙ඌа¶≤а¶Ња¶Яа¶ња¶∞ а¶Єа¶Ва¶ХаІНඣග඙аІНට а¶∞аІВ඙ а¶Еа¶≠ගථаІАට а¶єаІЯа•§ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶ЃаІВа¶≤ а¶Ча¶ЊаІЯаІЗථ, а¶Па¶Ха¶Ьථ බаІЛаІЯа¶Ња¶∞аІА, а¶Ъа¶Ња¶∞а¶Ьථ а¶ЫаІЛа¶Ха¶∞а¶Њ, а¶ЕථаІНඃඌථаІНа¶ѓ а¶Ъа¶∞ගටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Еа¶≠ගථаІЗටඌ, ඐඌබаІНඃඃථаІНටаІНа¶∞аІА— а¶Па¶Х а¶Па¶Ха¶Яа¶њ බа¶≤аІЗ а¶Єа¶ђ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶ЪаІЛබаІНබ-඙ථаІЗа¶∞ а¶Ьථ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Њ а¶У ඙аІБа¶∞аІБа¶Ј පගа¶≤аІН඙аІА ඕඌа¶ХаІЗа¶®а•§ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ ඙ඌа¶≤а¶Њ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗ බаІАа¶∞аІНа¶Ш а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ а¶Ха¶∞а¶ђаІЛ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶ња¶∞ а¶≤аІЛа¶Х а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶Х а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯа•§
а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ ඙ඌа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶ЃаІВа¶≤ а¶Ча¶ЊаІЯаІЗථ а¶ЬаІАටаІЗථ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶£а•§ а¶Ьа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶≤බයаІЗа¶∞ а¶Йа¶ЫаІБа¶≤඙аІБа¶ЦаІБа¶∞а¶њ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ ඙а¶ЮаІНа¶Ъа¶ЊаІЯаІЗට а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ а¶ђа¶Ња¶Є а¶Ха¶∞аІЗථ а¶ђа¶ња¶∞а¶≤ ඙аІНа¶∞ටගа¶≠а¶Ња¶Іа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓа¶ђаІЯа¶ЄаІА а¶Па¶З පගа¶≤аІН඙аІАа•§ а¶Па¶Хඁඌඕඌ а¶Шථа¶Ха¶Ња¶≤аІЛ а¶ЪаІБа¶≤, а¶Йа¶ЬаІНа¶ЬаІНа¶ђа¶≤ а¶ЪаІЛа¶Ц, а¶ЄаІБ-а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІНඕаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞аІА а¶Па¶З ඁඌථаІБа¶Ја¶Яа¶њ පගа¶≤аІН඙аІЗа¶∞ а¶Ьа¶ЧටаІЗ а¶ЬаІЬа¶њаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗථ ඪටаІЗа¶∞-а¶Жආඌа¶∞аІЛ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶ђаІЯа¶ЄаІЗа¶За•§ а¶Йа¶Ыа¶≤඙аІБа¶ЦаІБа¶∞а¶њ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ а¶ЄаІЗ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶ђа¶ња¶ЦаІНඃඌට පගа¶≤аІН඙аІА а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ඥаІНа¶ѓа¶Ња¶Ѓ а¶ЧаІАබඌа¶≤а•§ ටඌа¶Ба¶∞ බа¶≤аІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗථ а¶ЬаІАටаІЗа¶®а•§ а¶ЫаІЛа¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗа•§ බගථ а¶Ѓа¶ЬаІБа¶∞ ඙ගටඌа¶∞ а¶Па¶З а¶ЫаІЛа¶Я а¶ЫаІЗа¶≤аІЗ ඥаІНа¶ѓа¶Ња¶Ѓ а¶ЧаІАබඌа¶≤аІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬаІАටаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶Ха•§ බаІАа¶∞аІНа¶Шබගථ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАටаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපаІЗ ඕඌа¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓа¶З а¶єаІЯටаІЛ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЬаІАඐථаІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАට-ථаІГටаІНа¶ѓ-а¶Еа¶≠ගථаІЯ ඥаІБа¶ХаІЗ ඙аІЬаІЗа•§ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ ඙ඌа¶≤а¶Њ බගаІЯаІЗа¶З ටඌа¶Ба¶∞ පගа¶≤аІН඙аІА а¶ЬаІАඐථ පаІБа¶∞аІБа•§ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАටаІЗ а¶ХаІБපඌථ, ඪටаІНඃ඙аІАа¶∞, බаІЛටඌа¶∞а¶Ња¶°а¶Ња¶Ща¶Њ ඙ඌа¶≤ඌටаІЗа¶У ටගථග ඪගබаІНа¶І а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗа¶®а•§ බа¶≤аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඕඌа¶ХටаІЗ ඕඌа¶ХටаІЗа¶З පගа¶ЦаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗථ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ ඐඌබаІНඃඃථаІНටаІНа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ЬඌථаІЛа¶∞ а¶ХаІМපа¶≤а•§ ඥඌа¶Х, ඥаІЛа¶≤, ටඌඪඌ, а¶ЦаІЛа¶≤, ටඐа¶≤а¶Њ, а¶Ца¶Ѓа¶Х, а¶Па¶Хටඌа¶∞а¶Њ, а¶Єа¶Ња¶∞а¶ња¶ЮаІНа¶Ьа¶Њ, බаІЛටඌа¶∞а¶Њ, а¶ЖаІЬа¶ђа¶Ња¶БපаІА, а¶ЃаІЛа¶Ца¶Ња¶ђа¶Ња¶БපаІА, а¶єа¶Ња¶∞а¶ЃаІЛථගаІЯа¶Ња¶Ѓ а¶ђа¶Ња¶ЬඌටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗථ ඪඁඌථ බа¶ХаІНඣටඌаІЯа•§

ඥаІНа¶ѓа¶Ња¶Ѓ а¶ЧаІАබඌа¶≤аІЗа¶∞ а¶ђаІЯа¶Є а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ බа¶≤аІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶∞ ඙аІЬа¶≤аІЛ а¶ЬගටаІЗථаІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞а•§ а¶ЫаІЛа¶ЯаІНа¶Я а¶ЬගටаІЗථ ටටබගථаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х ඙а¶∞а¶ња¶£а¶§а•§ а¶ЧඌථаІЗа¶∞ බа¶≤аІЗа¶∞ ථаІЗටඌ а¶єа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ђа¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶ЧаІБа¶£ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ЙබаІНа¶≠а¶Ња¶Єа¶ња¶§а•§ බа¶≤ ථගаІЯаІЗ а¶ШаІБа¶∞аІЗа¶ЫаІЗථ а¶Хට а¶Хට а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯа•§ а¶Еа¶ХаІНа¶Ја¶∞а¶ЬаІНа¶ЮඌථයаІАථ а¶Па¶З ඁඌථаІБа¶Ја¶Яа¶њ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ а¶∞а¶Ъථඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗථ а¶Ча¶Ња¶®а•§ ටඌටаІЗ а¶ЄаІБа¶∞ බගаІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ ඙ඌа¶≤а¶Њ ථගаІЯаІЗ ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Њ ථගа¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Еа¶≠ගථаІЯаІЗа¶∞ ඁඌථ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ђаІЗපаІА а¶Жа¶Ха¶∞аІНа¶Ја¶£аІАаІЯ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗථ ඙ඌа¶≤а¶Ња¶ХаІЗ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђаІЗа¶∞ ටаІБа¶≤ථඌаІЯа•§ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ බа¶ХаІНඣටඌ а¶Пඁථ а¶ЙථаІНථаІАට а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗථ— а¶Єа¶ЃаІН඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ ඙ඌа¶≤а¶Њ а¶Па¶Ха¶Ња¶З а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАට, а¶Еа¶≠ගථаІЯ а¶Єа¶єа¶ѓаІЛа¶ЧаІЗ ඙аІНа¶∞බа¶∞аІНපථ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа¶®а•§
аІІаІѓаІЃаІѓ а¶Єа¶Ња¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђаІЗටඌа¶∞ පගа¶≤аІН඙аІАа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђаІАа¶ХаІГටග ඙аІЗа¶≤аІЗа¶®а•§ аІ®аІ¶аІ¶аІ© а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ аІІаІ™аІІаІ¶ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ පаІНа¶∞ඌඐථ а¶Ѓа¶Ња¶Є ඐටаІНа¶∞ගප බගථаІЗа¶∞а•§ а¶ЄаІЗа¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගබගථа¶З ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Жа¶Ха¶Ња¶ґа¶ђа¶Ња¶£аІА පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБаІЬа¶њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Єа¶ЃаІН඙аІНа¶∞а¶Ъа¶Ња¶∞ගට а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ ඙ඌа¶≤а¶Ња•§ а¶Жа¶∞ ටඌ පаІБථගаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ а¶ЬаІАටаІЗථ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶®а•§ аІ®аІ¶аІ¶аІ™ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶Жа¶ђаІНа¶ђа¶Ња¶Єа¶ЙබаІНබаІАථ а¶ЃаІЗа¶≤а¶ЊаІЯ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ ඙ඌа¶≤а¶Њ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපථ а¶Х’а¶∞аІЗ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ ඙ඌපඌ඙ඌපග ඐගබа¶ЧаІНа¶І а¶ЬථаІЗа¶∞а¶У බаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶Жа¶Ха¶∞аІНа¶Ја¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ЄаІЗ а¶ђа¶Ыа¶∞а¶З а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗථ а¶Жа¶єа¶ЃаІЗබඌඐඌබаІЗа•§ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗථ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗප а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЖඁථаІНටаІНа¶∞а¶£аІЗ а¶ЄаІЗ බаІЗපаІЗ а¶Па¶З ඙ඌа¶≤а¶Њ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓа•§ а¶ШаІБа¶∞аІЗ а¶ђаІЗаІЬа¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Њ බаІЗа¶ґа•§ а¶Зටඌа¶≤а¶њ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶У а¶ЖඁථаІНටаІНа¶∞а¶£ а¶ЬඌථගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ХගථаІНටаІБ ඙ඌа¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞а¶ња¶Х а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа¶®а¶®а¶ња•§
ථаІЗа¶З ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЬаІАඐථаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶За•§ ථаІЗа¶З а¶≠බаІНа¶∞а¶ЄаІНඕ а¶Ша¶∞-а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња•§ а¶Ъа¶Ња¶ЈаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ථගа¶Ьа¶ЄаІНа¶ђ а¶Ьа¶Ѓа¶њ ථаІЗа¶За•§ ථගаІЯඁගට а¶ЕථаІНථ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНඕඌථаІЗа¶∞ ථගපаІНа¶ЪаІЯටඌ ථаІЗа¶За•§ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ђаІБа¶ХаІЗа¶∞ а¶≠аІЗටа¶∞аІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶≠а¶Ња¶≤аІЛа¶ђа¶Ња¶Єа¶Ња•§ පගа¶≤аІН඙аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓа•§ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓа•§ ඪඌ඲ථඌаІЯ а¶°аІБа¶ђаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ ඁථ а¶ЪаІЗථаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶За•§ а¶ЬඌථаІЗ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ЧаІБаІЭ ටටаІНа¶ђа•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ха¶Ња¶Ча¶ЬаІЗа¶∞ ඙аІБа¶∞аІЛථаІЛ а¶Ха¶≠а¶Ња¶∞ а¶Ђа¶Ња¶За¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ча¶Ьа¶ЧаІБа¶≤аІЛ බаІЗа¶Ца¶Ња¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Жа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛ а¶єаІЯаІЗ а¶Йආа¶Ыа¶ња¶≤ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЃаІБа¶Ца•§ а¶Па¶Єа¶ђа¶З а¶Ъගආග඙ටаІНа¶∞, а¶Ца¶ђа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ча¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Яа¶ња¶В, а¶Ыа¶ђа¶њ а¶ЗටаІНа¶ѓа¶Ња¶¶а¶ња•§ а¶ЄаІНа¶ђаІАа¶ХаІГටගа¶∞ බගථ, а¶Єа¶ЃаІНඁඌථаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶Ја¶£а¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶Жа¶∞а¶У а¶Па¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ а¶ѓаІЗථ а¶ЙබаІНа¶≠ඌඪගට а¶єаІЯаІЗ а¶Йආа¶Ыа¶ња¶≤ ටඌа¶Ба¶∞ ඁථаІЗа•§ ඙ඌа¶≤а¶Ња¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶З ටаІЛ а¶Ха¶Ња¶Яа¶≤аІЛ а¶Еа¶∞аІНа¶ІаІЗа¶Х а¶ЬаІАа¶ђа¶®а•§ а¶ђа¶Ња¶ХаІАа¶Яа¶Ња¶У а¶Ъа¶≤а¶ђаІЛ ටඌа¶∞ ඪඌඕаІЗа•§ а¶П а¶Па¶Х а¶Е඙ඌа¶∞ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Єа•§ ථගපаІНа¶ЪගථаІНට ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞а¶§а¶Ња•§
а¶ШаІБа¶∞аІЗ а¶ђаІЗаІЬа¶Ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶Пබගа¶Х а¶Уබගа¶Х ටඌа¶Ба¶∞ ඪඌඕаІЗа•§ а¶Ча¶≤аІН඙а¶Ча¶Ња¶Ыа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ха¶Ња¶Яа¶≤аІЛ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Ња¶¶а¶ња¶®а•§ පаІБථа¶≤а¶Ња¶Ѓ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Й඙а¶≤а¶ђаІНа¶Іа¶ња¶∞ а¶Ха¶•а¶Ња•§ а¶ЬаІАඐථа¶ХаІЗ а¶Ча¶≠аІАа¶∞ а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Еа¶ІаІНа¶ѓаІЯථ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗ බаІБа¶Га¶Єа¶є ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපаІЗа¶У а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶∞ а¶ЄаІБа¶ЦаІЗ බගථ а¶Ха¶Ња¶ЯඌටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ ඁඌථаІБа¶Ја•§ а¶Па¶Х а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ЕථаІБа¶≠аІВа¶§а¶ња•§ а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶Хආගථ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶У а¶ЬаІАඐථа¶ХаІЗ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛа¶ђа¶Ња¶Єа¶Ња¶∞ а¶ЕබඁаІНа¶ѓ පа¶ХаІНа¶§а¶ња•§ а¶Жа¶∞ а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶∞ а¶ЖථථаІНබ а¶≠а¶Ња¶Ч а¶Ха¶∞аІЗ ථаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶У а¶ѓаІЗ а¶Па¶Х පගа¶≤аІНа¶™а•§ а¶Па¶Х ඁඌඕඌ а¶Шථ а¶Ха¶Ња¶≤аІЛ а¶ЪаІБа¶≤ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶ђа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ බаІБа¶≤аІЗ а¶УආаІЗ, බаІБ’а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗа¶∞ ටඌа¶∞а¶Њ а¶Йа¶ЬаІНа¶ЬаІНа¶ђа¶≤ а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗа•§ ඙ඌඕа¶∞ а¶ХаІЛа¶Бබඌ පа¶∞аІАа¶∞аІЗ а¶ѓаІЗ බаІЛа¶≤а¶Њ ඙аІЗපගа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ, යඌටаІЗа¶∞ а¶Ъа¶≤ථ, а¶Жа¶ЩаІБа¶≤аІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶ЄаІЗа¶У ටаІЛ පගа¶≤аІН඙ а¶єаІЯаІЗ а¶ЙආටаІЗ බаІЗа¶Ца¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ පගа¶≤аІН඙ а¶Ха¶∞а¶ђаІЛ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗа¶З ටаІЛ а¶Жа¶∞ а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ ඁථ බаІЗаІЯ ථඌ ඁඌථаІБа¶Ја•§ а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ පගа¶≤аІН඙ а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗа•§ а¶Па¶З а¶єаІЯаІЗ а¶Уආඌ а¶ЬаІАටаІЗථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ а¶Еථඌඐගа¶≤а•§ а¶ѓаІЗ а¶ЖථථаІНබаІЗа¶∞ а¶ЦаІЛа¶Ба¶ЬаІЗ ඁඌථаІБа¶Ј а¶ШаІЛа¶∞аІЗ ඙ඌа¶Ча¶≤аІЗа¶∞ ඁට, а¶ЄаІЗ ඙а¶∞ප ඙ඌඕа¶∞ а¶Па¶З ඁඌථаІБа¶Ја¶Яа¶ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ а¶ѓаІЗථ а¶Єа¶∞аІНа¶ђа¶¶а¶Ња•§ а¶ЫаІЛа¶БаІЯа¶Њ а¶≤а¶Ња¶Ча¶≤аІЗа¶З а¶ЄаІЛථඌа¶∞ ඙а¶∞ප а¶Єа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶За•§ а¶П а¶Па¶Х а¶ЕථථаІНа¶ѓ а¶ЕථаІБа¶≠аІВа¶§а¶ња•§ а¶ЬаІАඐථ а¶ѓаІЗ а¶Еа¶ЃаІБа¶≤аІНа¶ѓа•§
а¶ЄаІВа¶∞аІНа¶ѓ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶ЃаІЗ ඥа¶≤аІЗ ඙аІЬа¶≤аІЛа•§ а¶ЕථаІНа¶Іа¶Ха¶Ња¶∞ ටඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶≤аІЛ а¶Ъඌබа¶∞ ථගаІЯаІЗ а¶єа¶Ња¶Ьа¶ња¶∞а•§ а¶Па¶ђа¶Ња¶∞ ටаІЛ а¶Ђа¶ња¶∞ටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ ථගа¶Ь ථගа¶ХаІЗටථаІЗа•§ а¶ЙආаІЗ ඙аІЬа¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ђа¶Ња¶ЄаІЗа•§ ටගථගа¶У а¶Йආа¶≤аІЗа¶®а•§ බаІЗа¶ЦаІЗ ථගа¶≤аІЗථ ආගа¶Хඁට ඐඪටаІЗ ඙аІЗа¶∞аІЗа¶Ыа¶њ а¶Ха¶ња¶®а¶Ња•§ а¶ђа¶Ња¶Є а¶Ыа¶ЊаІЬа¶≤аІЛ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ша¶∞аІЗ а¶ЂаІЗа¶∞а¶Ња¶∞а•§ ටගථගа¶У а¶Ъа¶≤а¶≤аІЗථ а¶Йа¶≤аІНа¶ЯаІЛබගа¶ХаІЗа•§ ථටаІБථ а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶∞ а¶ЦаІЛа¶Ба¶ЬаІЗа•§ а¶ЖථථаІНබ ඪඌඕаІЗ а¶Х’а¶∞аІЗа•§
а¶Ъа¶£аІНа¶°а¶њ ථඌа¶Ъ
а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶РටගයаІНа¶ѓаІЗ а¶ЃаІБа¶ЦаІЛපаІЗа¶∞ а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶≠аІВа¶Ѓа¶ња¶Ха¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶ЃаІБа¶ЦаІЛප ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ЃаІВа¶≤ а¶Жබа¶≤а¶ХаІЗ ඥаІЗа¶ХаІЗ බගаІЯаІЗ ඐබа¶≤аІЗ බаІЗаІЯа•§ ඙аІНа¶∞а¶≠ඌඐගට а¶Ха¶∞аІЗ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපа¶ХаІЗа•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗ බаІЗඐටඌ а¶Е඙බаІЗඐටඌ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶≠а¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа•§ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ පа¶∞аІАа¶∞аІЗа¶∞ බа¶Ца¶≤ ථаІЗаІЯа•§ а¶ЄаІЗа¶Єа¶ЃаІЯ а¶ЄаІЗ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ ඁථа¶У ඐබа¶≤аІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Жа¶∞ ඐග඙а¶∞аІАටаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶ЕථаІНඃඌථаІНа¶ѓ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗ ටඌа¶ХаІЗ බаІЗඐටඌ а¶ђа¶Њ а¶Е඙බаІЗඐටඌа¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓа¶ХаІНа¶Ј а¶∞аІВ඙ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІЗ а¶≠аІЯ ඙ඌаІЯ, а¶≠а¶ХаІНටගටаІЗ а¶Жථට а¶єаІЯа•§ а¶Еඕඐඌ බаІВа¶∞аІЗ а¶Єа¶∞аІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§
а¶ЃаІБа¶ЦаІЛපаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ а¶ЬඌබаІБඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є а¶ЬаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ ඁඌථаІБа¶Ј а¶ЕථаІЗа¶Хබගථ а¶Жа¶ЧаІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЃаІБа¶ЦаІЛප ඙а¶∞а¶≤аІЗ ඁඌථаІБа¶Ј ඐබа¶≤аІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ЕථаІБඁඌථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ а¶Ха¶Ња¶≤аІЗ පගа¶Ха¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶Еа¶≠ගථаІЯ а¶Ха¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶ЃаІГට ඙පаІБа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶ЃаІЬа¶Њ а¶Ча¶ЊаІЯаІЗ а¶ЬаІЬа¶њаІЯаІЗ ථගට а¶Еа¶≠ගථаІЗටඌа¶∞а¶Ња•§ ඁඌඕඌаІЯ а¶ђаІЗа¶Ба¶ІаІЗ ථගට а¶ЃаІГට ඙පаІБа¶∞ පගа¶Ва•§ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ а¶ЧаІБа¶єа¶Ња¶ЪගටаІНа¶∞аІЗ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЛප ඙а¶∞ගයගට а¶Ыа¶ђа¶њ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Ъа¶≤ටаІЗ а¶Ъа¶≤ටаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඙а¶∞аІЗ ඙ඌඕа¶∞аІЗа¶∞ ටаІИа¶∞а¶њ а¶ЃаІБа¶ЦаІЛප බගаІЯаІЗ ඥаІЗа¶ХаІЗ බගට а¶ЃаІБа¶Ца•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ බаІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶њ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶ЃаІБа¶ЦаІЛප ටаІИа¶∞ගටаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єаІГට а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Ъа¶Ња¶ЃаІЬа¶Њ, ඙ඌඕа¶∞, а¶Хඌආ, а¶ђа¶Њ а¶ХаІЛථа¶У ඲ඌටаІБа•§ а¶ЃаІБа¶ЦаІЛප ඙а¶∞аІЗ ථඌа¶Ъ, а¶Еа¶≠ගථаІЯ а¶Е඙ඌа¶∞аІНඕගඐ а¶ХаІЛථа¶У පа¶ХаІНටගа¶∞ а¶Жа¶∞а¶Ња¶Іа¶®а¶Ња•§
а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶Жа¶ЫаІЗ ‘а¶Ъа¶£аІНа¶°а¶њ ථඌа¶Ъ’а•§ ‘а¶Ъа¶£аІНа¶°а¶њ ථඌа¶Ъ’ ථඌඁаІЗ ටඌа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ а¶єа¶≤аІЗа¶У а¶П а¶ЖබටаІЗ ථаІГටаІНа¶ѓа¶Ња¶≠ගථаІЯа•§ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶ЪаІИටаІНа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ පаІЗа¶ЈаІЗ а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО а¶П඙аІНа¶∞а¶ња¶≤ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Эа¶њ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ බගථයඌа¶Яа¶Њ а¶Ѓа¶єа¶ХаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙аІБа¶Ба¶Яа¶ња¶Ѓа¶Ња¶∞аІА а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶∞а¶Њ පаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ ටаІИа¶∞а¶њ а¶ЃаІБа¶ЦаІЛප а¶ђаІЗа¶Ба¶ІаІЗ а¶Ча¶Ња¶БаІЯаІЗа¶∞ а¶Ша¶∞аІЗ а¶Ша¶∞аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Чථ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђаІЗаІЬа¶ЊаІЯа•§ පаІЛа¶≤а¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ьа¶≤а¶Ь а¶ЙබаІНа¶≠а¶ња¶¶а•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЙබаІНа¶≠ගබ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶Ња¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞а¶Њ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶Ха¶∞аІЗථ а¶Па¶ђа¶В а¶ЃаІБа¶ЦаІЛප, а¶ЂаІБа¶≤, ඙аІНа¶∞ටගඁඌа¶∞ а¶ЧаІЯථඌ, а¶ђа¶њаІЯаІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶ХаІБа¶Я а¶ЗටаІНඃඌබග а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶ЧаІНа¶∞аІА ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§
а¶Ъа¶£аІНа¶°а¶њ ථඌа¶ЪаІЗа¶∞ а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶Па¶Ха¶Ьථ ‘а¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶Юа¶Њ’ (඙аІНа¶∞඲ඌථ а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьа¶Х, а¶Єа¶≠ඌ඙ටග, බа¶≤඙ටග, ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞඲ඌථ ‘а¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶Юа¶Њ’ а¶Й඙ඌ඲ගටаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගට යථ)а•§ ටගථගа¶З а¶Жа¶∞аІНඕගа¶Х බඌаІЯගටаІНа¶ђ ඐයථ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ බа¶≤аІЗа¶∞ а¶Ца¶∞а¶Ъа¶У ටඌа¶Ба¶∞а•§ а¶ХаІЛථа¶У а¶ХаІЛථа¶У а¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶Юа¶Њ ඙аІНа¶∞ටගඐа¶Ыа¶∞ ථගаІЯඁගට а¶Па¶З а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Ха¶Ња¶∞аІБа¶∞ ඁඌථඪගа¶Х ඕඌа¶Ха¶≤аІЗ а¶Ъа¶£аІНа¶°а¶њ ථඌа¶ЪаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§
а¶ЪаІИටаІНа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ පаІЗа¶Ј ඪඌටබගථ а¶ђа¶Њ බපබගථ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶ЃаІБа¶ЦаІЛප а¶ђаІЗа¶Ба¶ІаІЗ ඙аІЛපඌа¶Х ඙а¶∞аІЗ а¶Ъа¶£аІНа¶°а¶ња¶∞ а¶∞аІВ඙ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶Х’а¶∞аІЗ ඥඌа¶ХаІЗа¶∞ ඐඌබаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ථаІЗа¶ЪаІЗ ථаІЗа¶ЪаІЗ а¶ШаІБа¶∞аІЗ а¶ђаІЗаІЬඌථ а¶Ча¶Ња¶БаІЯаІЗа¶∞ ඙ඕаІЗ ඙ඕаІЗа•§ ඙аІНа¶∞ටගа¶Яа¶њ а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНඕаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ඃඌථ ථаІГටаІНа¶ѓ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපථ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶У а¶Ѓа¶Ња¶Чථ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ථඌа¶ЪаІЗа¶∞ බа¶≤аІЗ ටගථ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ъа¶Ња¶∞а¶Ьථ ඕඌа¶ХаІЗа¶®а•§ а¶Ъа¶£аІНа¶°а¶њ, ඥඌа¶Ха¶њ, а¶≠а¶Ња¶∞аІА, а¶ґа¶ња¶ђа•§ ඥඌа¶ХаІЗа¶∞ а¶ђаІЛа¶≤аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ පගඐ а¶У а¶Ъа¶£аІНа¶°а¶њ ථаІГටаІНа¶ѓа¶Ња¶≠ගථаІЯ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНඕ а¶≠а¶ХаІНටගа¶≠а¶∞аІЗ බඌථ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ටඌ а¶≠а¶Ња¶∞аІАа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶ЭаІЛа¶≤а¶ЊаІЯ а¶Ьа¶Ѓа¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶Ѓа¶Ња¶Чථ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶є පаІЗа¶Ј а¶Х’а¶∞аІЗ а¶ЪаІИටаІНа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗ පаІЗа¶Ј බගථ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶ХаІЛථа¶У а¶Ха¶Ња¶≤аІА ඁථаІНබගа¶∞аІЗ а¶ђа¶Њ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶Юа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬගටаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ ටටаІНටаІНඐඌඐ඲ඌථаІЗа¶З а¶ІаІВа¶Ѓа¶Іа¶Ња¶Ѓ а¶Х’а¶∞аІЗ ඙аІБа¶ЬаІЛ а¶єаІЯа•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට а¶Еа¶Іа¶ња¶ђа¶Ња¶ЄаІА ටඌටаІЗ а¶Еа¶Вපа¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Ца¶ња¶ЪаІБа¶∞аІА ඙аІНа¶∞ඪඌබ ටаІИа¶∞а¶њ а¶єаІЯ, ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓаІЗа¶ХаІЗа¶З ටඌ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Ъа¶£аІНа¶°а¶њ ථඌа¶ЪаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЬаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ а¶ЬඌබаІБ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є а¶У ටඌථаІНටаІНа¶∞а¶ња¶Х ඙බаІНа¶Іа¶§а¶ња•§
а¶Ъа¶£аІНа¶°а¶њ ථඌа¶Ъ а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІА а¶ЕථаІБа¶ЈаІНа¶†а¶Ња¶®а•§ а¶Па¶З а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗ а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞а¶ња¶Х а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථа¶ЯаІБа¶ХаІБа¶З а¶єаІЯа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ъа¶£аІНа¶°а¶њ ථඌа¶ЪаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ЮаІНа¶Ъ а¶Й඙ඪаІНඕඌ඙ථඌ ඃඕаІЗа¶ЈаІНа¶Я а¶Жа¶Ха¶∞аІНа¶Ја¶£аІАаІЯ а¶У ථඌа¶ЯаІНа¶ѓ а¶Й඙а¶Ха¶∞а¶£ а¶Єа¶ЃаІГබаІНа¶Іа•§ а¶Ъа¶£аІНа¶°а¶њ ථඌа¶ЪаІЗа¶∞ а¶Ъа¶∞ගටаІНа¶∞ а¶ЪථаІНа¶°а¶њ, පගඐ, а¶°а¶Ња¶Хගථග, а¶ѓаІЛа¶Чගථග, පаІГа¶Ча¶Ња¶≤ а¶У а¶Еа¶ЄаІБа¶∞а•§ а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶Й඙ඪаІНඕඌ඙ගට а¶єаІЯ а¶ЪථаІНа¶°а¶њ а¶∞аІВ඙аІЗ බаІЗඐපටаІНа¶∞аІБ බаІИටаІНа¶ѓ ඐගථඌපаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶єа¶ња¶®а¶ња•§ а¶ХаІЗа¶ђа¶≤ ඁඌටаІНа¶∞ ඥඌа¶ХаІЗа¶∞ ඐඌබаІНа¶ѓ а¶Жа¶ђа¶є а¶∞аІВ඙аІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶ХаІЛථа¶У а¶Єа¶Ва¶≤ඌ඙ а¶ђа¶Њ а¶ЧаІАට ඕඌа¶ХаІЗ а¶®а¶Ња•§
බаІЗа¶ђаІА а¶Ъа¶£аІНа¶°а¶ња¶∞ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ц ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶ХаІЗථаІНа¶°аІЯ ඙аІБа¶∞а¶Ња¶£аІЗа•§ ටගථග а¶≤аІЛа¶ХබаІЗа¶ђаІАа•§ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓа¶ђа¶ЩаІНа¶Ч, а¶Жа¶Єа¶Ња¶Ѓ, а¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞, а¶УаІЬа¶ња¶Ја¶Њ а¶У а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗපаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ බаІЗа¶ђаІА а¶Ъа¶£аІНа¶°а¶ња¶∞ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථ а¶У ඙аІБа¶ЬаІЛ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ථ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓа•§ а¶Ъа¶£аІНа¶°а¶њ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓ බаІЗа¶ђаІАа¶∞ ඁඌයඌටаІНа¶ЃаІНа¶ѓ а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶®а¶Њ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Ха¶ђа¶ња¶Ха¶ЩаІНа¶Хථ а¶ЃаІБа¶ХаІБථаІНබ а¶ђа¶ња¶∞а¶Ъගට ‘а¶Ъа¶£аІНа¶°аІАа¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤’ а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶Ьථ඙аІНа¶∞а¶њаІЯ а¶У а¶ђа¶єаІБа¶≤ ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶ња¶§а•§ а¶Ъа¶£аІНа¶°а¶њ ථඌа¶ЪаІЗ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶§ ඙аІБа¶∞аІБа¶Ј පගа¶≤аІН඙аІАа¶∞а¶Ња¶З а¶Еа¶Вප а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§
(а¶Па¶∞඙а¶∞ а¶Жа¶Ча¶Ња¶ЃаІА а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ)
Have an account?
Login with your personal info to keep reading premium contents
You don't have an account?
Enter your personal details and start your reading journey with us
Design & Developed by: WikiIND
Maintained by: Ekhon Dooars Team