






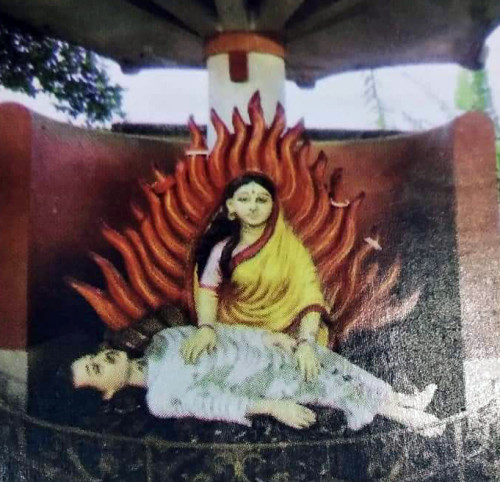









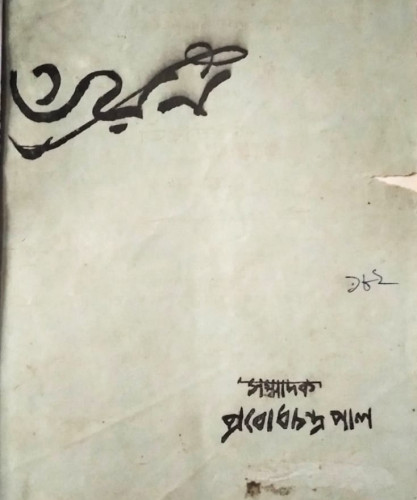




 শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

দেবেশবাবু বলেছিলেন, জলপাইগুড়ি শহরের তিনদিক দিয়ে সূর্য ওঠে চারদিক দিয়ে বানা আসে --- সেটা খাঁটি সত্যি। তিনদিক দিয়ে সূর্য ওঠার বিষয়টা যারা নিয়মিত ভোর বেলায় অন্তত সাত-আট মাস গেছেন তাঁরা চাক্ষুষ করেছেন। এর পেছনে ইংরেজদের অবদানই বেশি কারণ তাঁরা তিস্তার বিস্তীর্ণ পশ্চিমঘাটের ঠিক পাশেই, মানে যতটা পাশে করা যায় ততটা পাশেই স্থাপন করেছিল শহর। বৈকুণ্ঠপুর-কোচবিহারের ইতিহাস নিয়ে যারা সামান্য অবহিত তাঁরাই জানেন যে এদিককার ইতিহাসের বিচারে জলপাইগুড়ি ‘টৌন’ (এমনটা বলত চা-বাগানের শ্রমিকরা) অর্বাচীন। শহর ইংরেজরা বানিয়েছিলেন নিজেদের তাগিদে।
নিশ্চিত জানি না তবে ১৮০০ সালের অল্প আগে-পরে বৈকুন্ঠপুরের রাজধানী শিকারপুর থেকে স্থাপিত হলো এই টাউনে। তবে তখন নাকি তার নাম ছিল ‘ফকিরগঞ্জ’। তাই বলা যায় রাজধানী স্থাপিত হলো ফকিরগঞ্জের এমন এক ভূখন্ডে যার একদিকে তিস্তা, আরেক দিকে করলা। স্থান হিসেবে যেমন সুরক্ষিত তেমনই তিস্তার বন্যায় তুলনামূলক কম ডোবে। রাজবাড়িকে ঘিরে জনবসতিও গড়ে উঠল টপাটপ। তখন টাউনের চেহারা ছড়িয়ে থাকা বৃক্ষছত্রছায়ায় ঢাকা একটা গ্রাম। তারপর তো ইংরেজরা শহর বানাতে শুরু করল। সে কাজ যখন শুরু হচ্ছে তখন ওদিকে জন্মেছেন রবীন্দ্রনাথ।
টাউন বানাবার কাজ শুরু হওয়ার প্রায় চার দশক পরে স্থাপিত হলো টাউনের নাট্যমঞ্চ আর টাউন ক্লাব। খেলাধূলার জন্য। নাট্যমঞ্চ অর্থাৎ আর্যনাট্য সমাজ স্থাপনের পেছনের কাহিনী থেকে জানা যায় যে উঠতি বয়সের ছেলেপুলেরা সংস্কৃতি চর্চার অভাবে বখে যাচ্ছে। ভালো কিছু একটা হওয়া দরকার। এইভাবে নাটকের দল হলো। বখে যাওয়া ছেলেপুলেরা ছিলেন মূলত ছাত্র যুবর দল। বাড়িতে কমবেশি লেখাপড়ার চল ছিল।
টাউন বানাতে গিয়ে ইংরেজদের অনেক কিছুর দরকার হয়েছিল। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সরকারী কর্মচারী। গোড়ায় এরা প্রায় সকলেই দক্ষিণবঙ্গ, বলা ভালো কলকাতা ও তার কাছাকাছি জায়গা থেকে এসেছিলেন। এরা বাড়িতে মা-বাবাকে রেখে টাউনে রীতিমত স্বাধীন জীবন যাপন করা সুযোগ পান। বর্তমান বাংলাদেশ থেকে তখন এই রকম স্বাধীন হয়ে টাউনে ভাগ্য ফেরাতে যে সব লেখাপড়া শেখা নবীনরা আসতেন তাঁদের লক্ষ্য ছিল আইনজীবী হওয়া। এরাই মূলত টাউনে সামাজিক উন্নতি গড়ে তোলার কাজে মেতেছিলেন। সরকারী বিধিনিষেধ বাঁচিয়ে সরকারী কর্মচারীরাও যোগাতেন উৎসাহ। এঁদের কেউ কেউ তো এই শহরেই থেকে গেছেন।
আর্যনাট্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই মোটামুটি হিট হয়ে যায়। নামের সাথে ‘সমাজ’ কথাটা যুক্ত হয়েছিল তবে সেটা ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে না তৎকালীন যুগের হাওয়ার, সেটা গবেষকরা বলতে পারেন। গোটা ব্যাপারটাই দান-ধ্যানের মাধ্যমে হয়েছিল। বখে যাওয়ার কিশোর-যুবকের নিজেরাই শ্রমিককের ভূমিকা পালন করেন। অচিরেই আর্যনাট্য সমাজ টাউনে একটি সামাজিক প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি হয়ে ওঠে।
কিন্তু এমন একটি নাট্যসমাজ একটি তৈরি হওয়ার পর যখন সাফল্য পেল তখনই বোঝা গেছিল যে দ্বিতীয় আরো একটি আসা কেবল সময়ের অপেক্ষা। এই দ্বিতীয় সমাজটি ছিল বান্ধবনাট্য সমাজ। কিন্তু এর সূত্রপাত সেবা সমিতির সরঞ্জাম কেনাকে কেন্দ্র করে। এই বিষয়ে চারুচন্দ্র সান্যাল লিখে গেছেন। ১৯২২ নাগাদ টাউনে এই সেবা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চিকিৎসায় সহযোগিতা করার জন্য। ওই সময় টাউনের হাসপাতাল ছিল ছোট্ট। ম্যালেরিয়া-কালাজ্বরের প্রচন্ড দাপট। জ্বর মাপার জন্য থার্মমিটার ছিল পাড়ায় হয় তো একটা বাড়িতে। এই অবস্থায় কিছু সরঞ্জাম কিনে চিকিৎসায় সাহায্য করার জন্যই সেবা সমিতিটি গড়ে ওঠে। সরঞ্জাম কেনার টাকা যোগারের জন্য টিকিট বিক্রি করে নাটক করার কথা ভাবা হয়।
নাটক হাউজফুল হয়েছিল এবং আর্যনাট্য ভাড়া করেই হয়েছিল। এরপর আবার শো করতে চাইলে আর্যনাট্য হল দিতে অস্বীকার করে। এটা ছিল প্রত্যক্ষ কারণ। পরিণতিতে টাউনে প্রথম নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠার প্রায় দু-দশক পর বান্ধব নাট্যসমাজের আবির্ভাব যেটা আসলে তখন কালের গর্ভে একটু একটু করে বেড়ে উঠছিল। তবে স্থাপিত হওয়ার পর জমি যোগার করে মঞ্চ বানাতে বান্ধবনাট্যের বছর দুয়েক লেগেছিল। সময়টা ছিল টাউনের অর্থনৈতিক ইতিহাসের উজ্জ্বল কাল। জমি, টাকা এবং মঞ্চ নির্মাণের কাঠ পেতে কোনও সমস্যা হয় নি। কাঠের খুঁটি দিয়েছিলেন বাতাবাড়ির এক জোতদার। টাউনের এলেমদার ব্যক্তিরা কেউ টিন, কেউ কাঠের তক্তা ইত্যাদি দিয়েছিল। চা-বাগানের মালিকরা ভালো টাকা দিয়েছিলেন।
বান্ধবনাট্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে টাউনে একটা সাংস্কৃতিক ভারসাম্য এলো। টাউনে তখন লোক বেশি নেই। দুটো মঞ্চই যথেষ্ট। ফলে টাউনে অভিনয় চর্চার গতি দ্বিগুণ হয়ে গেল। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে স্বাধীনতা পর্যন্ত টাউনে দুটো বিষয় ছিল তুমুল জনপ্রিয়। অভিনয়-গান এবং ফুটবল খেলা। তুলনায় সাহিত্য পত্রিকা প্রায় নেই। তেমন কোনও লেখকের নামও নেই। কিন্তু সংবাদপত্র বেরিয়েছে। দুটো সাপ্তাহিক অনেকদিন চলেছিল। সাপ্তাহিক জনমত এবং ত্রিস্রোতা --- এই দুটো কাগজে সেকালের টাউনের সমাজ জীবনের অনেক তথ্যই ধরা ছিল।
কিন্তু এটাই ছিল স্বাভাবিক। আধুনিক সাহিত্য, পত্রিকা এসব জাতির কাছে ছিল নতুন। কিন্তু গান আর অভিনয় তাঁর রক্তে। তাছাড়া তখন সাহিত্য-পত্রিকা বিষয়টি রীতিমত কলকাতা কেন্দ্রিক। তার প্রভাব টাউনে ছিল মূলত বই পড়ায়।
টাউনে যেটা অনেকদিন পর্যন্ত ছিল না তা হলো হোটেল। বাইরে থেকে আসা লোক মানেই কারো না কারো বাড়িতে থাকবে। সে অনাত্মীয় হলেও ক্ষতি নেই। তাই হোটেলের দরকার হত না। কামাখ্যা প্রসাদ চক্রবর্তী লিখেছিলেন, সকালে টাউন স্টেশনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন এমন কিছু লোকও ছিল। ট্রেন থেকে অচেনা কাউকে নামতে দেখলেই আলাপ জমিয়ে নিজের বাড়িতে অতিথি করে রাখতেন। সম্পর্কের একটা ছুতো পেলেই হলো। ‘আরে আমার মামাশ্বশুর আর আপনি তো একই জেলার লোক। চলুন চলুন!’ এই রকম ছিল ব্যাপারটা।
টাউনে এখনো তারকা হোটেল নেই। সেটা এই কারণেই নাকি?
(চলবে)
Have an account?
Login with your personal info to keep reading premium contents
You don't have an account?
Enter your personal details and start your reading journey with us
Design & Developed by: WikiIND
Maintained by: Ekhon Dooars Team